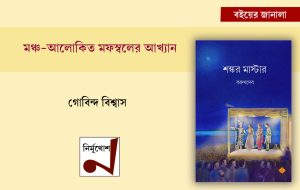পুনর্ভবাপুত্র। ধারাবাহিক উপন্যাস। চতুর্থ পর্ব। লিখছেন আহমেদ খান হীরক।

দূর থেকে সোনা সোনা
কাছ থেকেও সোনা সোনা…
আমাদের স্কুল নিয়ে আমার প্রথম যে মন্তব্য ছিল তা হলো– দূর থেকেও সোনা সোনা, কাছ থেকেও সোনা সোনা!
এরকম বলার কারণ ছিল স্কুল নিয়ে আমাদের মধ্যে ছিল কোমল রেষারেষি।
পাড়ার সমবয়সীরা সবাই পড়ত উত্তরা প্রাইমারি স্কুলে। আম বাগানের মধ্যে, ছায়াঢাকা চমৎকার স্কুল। কিন্তু আমাকে সেই স্কুলে ভর্তি করা হলো না। আমাকে দেওয়া হলো কিন্ডার গার্ডেনে।
তা কিন্ডার গার্ডেন রহনপুরে কেবলই হয়েছে। নিজস্ব ভবনও নেই তাদের। গার্লস হাইস্কুলের ভবনে তারা নিজেদের ক্লাস বসায়। ক্লাস শেষ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়েও আসতে হতো। কারণ কিন্ডার গার্ডেন বেরোলে ক্লাসগুলোতে গার্লস হাইস্কুল শুরু হবে।
প্রাইমারি স্তরে ভালো শিক্ষার কথা ভেবে আব্বা-আম্মা আমাকে এই স্কুলে ভর্তি করে দিলো। স্কুলের নাম- শিশু শিক্ষা কিন্ডার গার্টেন। ওরফে কেজি স্কুল। আমার বয়স তখন চার। স্কুল যাওয়া মানে এক বিরাট বন্দিকাল। ফলে প্রতিদিন সকালেই আমার হাপুস নয়নে ক্রন্দন এবং ইতি আপার আমাকে প্রায় পাঁজকোলা করে স্কুলের দিকে নিয়ে যাওয়া।
পেঁয়াজ পট্টি থেকে বড় বাজারের ইঁদারা, কাছারি থেকে সওদা বাবার মাজার… সকাল সকাল আমার কান্নাকাটিতে একদম জেগে উঠত। আর ওই সওদা বাবার মাজারের কাছে গিয়ে আমার ক্রন্দনের সাথে যুক্ত হতো আরেকটি ক্রন্দন। মনোজের ক্রন্দন।
পুরো নাম শ্রীমনোজকুমার দাস। বয়স আমার সমানই। দেখতে আমারই মতো চিকন-চাকন। স্কুলের প্রতি আমারই মতো অভক্তি। আমার বোনের মতো তার পিসি তাকে টেনেহেঁচড়ে স্কুলে নিয়ে যেত। আমার মতোই সারা রাস্তা ভেভাত। ফলে আমাদের বন্ধু না হয়ে কোনো উপায় ছিল না। আমরা যেতে যেতে কাঁদতাম, তারপর আমাদের স্কুলে রেখে যখন আপা-পিসিরা ফিরে আসতো, তখনও কাঁদতাম। স্কুলের প্রথম বছরটা ছিল আমাদের শাবানা-কাল!
কিন্তু একটা বছর পরই স্কুলের প্রতি এই অভক্তি একেবারে পাল্টে গেল। আমরা দ্রুতই স্কুলপাগলা হয়ে উঠলাম। আর তা শুরু হয়েছিল স্কুলের নিজের ভবনটা হওয়ার পরেই।
বড় বাজার থেকে স্টেশনের দিকে যেতে, পুনর্ভবার সাথে একটা একটা ভাঙা ব্রিজ। ব্রিজ ভাঙা, কিন্তু তার ওপর দিয়েই মানুষের চলাচল ছিল। সাইকেল চলত, ভ্যান-রিকশাও তখন চলত। তো সেই ব্রিজ পার হলেই রাস্তার বাম পাশে টেলিফোন অফিস। আর তার পেছনেই আমাদের স্কুলের নতুন ভবন। কী যে সুন্দর!
চারটা আম গাছ… ইয়া বড় বড়… গুঁড়ির এপাড়-ওপাড় একসাথে দেখা যায় না–তাদের ঘিরে আমাদের স্কুলের বিল্ডিং। “এল” আকৃত্তির। একপাশে অফিসরুম। তারপর বাথরুম। তারপর সারি ধরে চারটা ঘর। সেখানে আমাদের পড়ানো। স্কুলের পেছনেই উপজেলা অফিস। আরেকটু পেছনে পুকুর। তার বাঁপাশজুড়ে অফিসার্স কোয়ার্টার। ফলে স্কুলটাকে আমার দূর থেকেও সোনা সোনা লাগে, আবার কাছ থেকেও লাগে!
কাছ থেকে বোধহয় একটু বেশিই সোনা সোনা লাগে। কারণ এখানেই তো আমার গড়ে ওঠা প্রথম বন্ধুত্ব। মনোজ যেমন ছিল ক্রন্দনবন্ধু, তেমনি ছিল একই দিনে ভর্তি হওয়া বন্ধু স্বপন। সাথে শফিকুল, হিমেল, শিপলু… কত কেউ! এক সাথে ক্লাস করা, টিফিন করা, একই সাথে পাশের দোকানে গিয়ে ডালপুরি খাওয়া… আর সুযোগ পেলেই চোর-পুলিশ খেলা। আমার ওই হাফপ্যান্ট বয়সে পুরো রহনপুর, রহনপুরের আনাচে-কানাচে জায়গায়, পদচিহ্ন পড়েছিল এই চোর-পুলিশের কল্যাণে। আমরা যারা একটু সেয়ানা ছিলাম, চোর হয়ে, পুরো সময়টা কাটিয়ে দিতাম বিভিন্ন জায়গা-বেজায়গায় গিয়ে। তারপর এসেম্বলিতে ঠিক হাজির। গলায় ঘাম, চুলে ঘাম… সেগুলোকে কোনোমতে ঠেকিয়ে বুকটান করে দাঁড়িয়ে…আমি ওয়াদা করিতেছি যে… লাল-সবুজ পতাকাকে স্যালুট দেয়া… জাতীয় সঙ্গীত…আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি… “মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি” লাইনটা এলেই আমার আম্মার মুখটা ভেসে উঠত। নাকফুলটা ঝিলিক দিতো তখন। তাতেই মনে হতো আম্মা হাসছেন!
পিটি-প্যারেডের শিক্ষক ছিলেন গৌতম স্যার।
ছোটো-খাটো মানুষ। হুইসেলের সাথে একটা কালো কড লাগানো ছিল তার। সেটা তিনি নিয়ে বেড়াতেন সবসময়। গলার টাই, বুকের ব্যাজ, শার্টের কলার এইসব ঠিক না থাকলে চিপ ধরে টান দিতেন। আর পিটির সময় তালে তাল না মেলাতে পারলে পায়ের ওপর কডের বাড়ি। চামড়া জ্বলে যেত একেবারে। শুনে গৌতম স্যারকে বেশ কড়া শিক্ষক মনে হলেও আমরা আসলে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতাম রফিক স্যারকে। তিনি হাসতে হাসতে ঢুকতেন আর আমাদের নাচাতে নাচাতে বেরোতেন।
ছাত্র পেটানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশেষ ক্রিয়েটিভ মানুষ।
টেবিলের নিচে মাথা ঢুকিয়ে, হাতে টিপ করে পায়ের ওপর আচমকা মেরে তিনি আমাদের কলিজা খালি করে দিতেন। কিন্তু তার সবচেয়ে ক্রিয়েটিভ পিটানি ছিল ব্ল্যাকবোর্ডে তিনটা শূন্য এঁকে তাতে দুই হাত আর কপাল ঠেকিয়ে রাখানো। ওই অবস্থায়, যখন চোখের সামনে কেবলই বোর্ডের অন্ধকার…সপাৎ সপাৎ করে পেছনে তখন বেত পড়ত… এ কারণে আমার চোখের সামনে দুই জন পড়ালেখা ছেড়ে দিয়েছিল… একজন নুরতাজুল, অন্যজনের নামটা এখন মনে নেই।
অনেক দিন পর, একদিন, স্যারের সাথে দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করেছিল এত যে পিটিয়েছিলেন স্যার আপনি, প্রায় সারা জীবন ধরে, কখনো অনুশোচনা হয়নি?
আমাদের শিক্ষকদের অনুশোচনা ছিল না। তারা হুংকার দিয়ে পেটাতেন। যে শিক্ষক যত বেশি পেটাতে পারে তখন সেই শিক্ষকই তত ভালো শিক্ষক। অভিভাবকরা তখন বলত—ছাত্র দিয়া গেলাম সার, আমাদের শুধু হাড্ডি ফেরত দিলেই হবে!
মার খেয়ে খেয়ে আমরা হাড্ডি হয়ে যেতাম। গোপনে কাঁদতামও। কাঁদত না শুধু শুভ।
শুভ আমাদের অদ্ভুত বন্ধু।
বড় বড় চোখ। শক্ত চুল-ভ্রু। পেটা কপাল ওই বয়সেই। আমাদের মতো পড়ালেখা পারত না সে। ফলে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো শিক্ষকের কাছে মার খেতে হতো তাকে। কোনো কোনো দিন তো পরপর দুই ক্লাশেও। কিন্তু সে কাঁদত না। চোখ-মুখ-নাক-গলা সব লাল হয়ে যেত। কিন্তু কাঁদত না।
শিক্ষকদের মনেও কখনো কখনো জেদ চেপে যেত নিশ্চয়। শুভকে কাঁদিয়ে ছাড়বে। সপাং সপাং করে বেতের বাড়ি পড়ত। কেউ কেউ কলমি ডালেও দ্যুতি ছড়াতেন; কিন্তু কান্না দূরের কথা, শুভ হাসত। শিক্ষকদের মেজাজ আরও চড়ত। শুভ আরও হাসত!
সেই শুভকে নিয়ে আমি বেরিয়েছি। উদ্দেশ্য রুবেল ভাইয়ের দোকান।
স্কুল শেষ। রুটিনমাফিক শুভ আজও মার খেয়েছে। তবে মারটা খেয়েছে রেহানা ম্যাডামের কাছে। অপেক্ষাকৃত সহজ মার। হাতের ওপর স্কেলের তিনটা বাড়ি। শুভ একবার হাত সরিয়ে নিয়েছিল বলে একটা বোনাস খেতে হয়েছে।
রুবেল ভাইয়ের দোকান শুভদের বাড়ির পাশেই।
দোকানটা আসলে রুবেল ভাইয়ের না। তার চাচার। ঘড়ি-চশমা বিক্রি হয়। রুবেল ভাই দোকানে গলায় পাউডার দিয়ে বসে থাকে। চুলে শ্যাম্পু। মাথার ওপরে ঘোরা চার পাখার বাতাসে চুলগুলো উড়তেই থাকে। রুবেল ভাইয়ের চুল দেখলে নিজের চুলে হাত চলে যায়। একটু উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে।
দোকানেই ছিল রুবেল ভাই। সাথে এক কাস্টমার থাকায় আমরা পাশের বেঞ্চিতে বসি। শুভ বলে, ঘড়ি কিনবি?
আমি মাথা নাড়ায়। সময় কাটে না। কাস্টমার টিপে টিপে চশমা দেখছে। শুভ তার হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও লাল। আমি বলি, তোর ব্যথা লাগে না?
শুভ হাসে।
‘তুই কান্দিস না ক্যান?’
‘কান্না আসে না তো। না আসলে ক্যামনে কান্দবো?’
শুভ আবারও হাসে। আমার মনে হয় হাসিটাই বোধহয় শুভর কান্না। এমন কি হতে পারে, কোনো কারণে একজন কান্না আর হাসির বিষয়টা গুলিয়ে ফেলেছে। মগজে কান্নার এলার্ম গেলে, মগজটা তাকে হাসিয়ে দিচ্ছে!
কাস্টমার গেছে। রুবেল ভাই এগিয়ে এসে বলে, কী নিবা হীরক?
আমি আশ-পাশ দেখে নিই। তার পকেট থেকে ছবি আপার বুকের ওম বের করি। রুবেল ভাইকে দিয়ে বলি, ছবি আপা দিয়েছে…
রুবেল ভাই ভ্রু কুঁচকে চিঠিটা খোলে। একটু পড়ে। তারপর হঠাৎ করেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে। তারপর টুকরোগুলো আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, তোমার ছবি আপাকে বলবা, এইটাই আমার উত্তর!
আমি চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো নিয়ে থম মেরে বসে থাকি। ক্লাস ফাইভে পড়ি, জীবন বেশি দেখিনি সত্যি, কিন্তু এও সত্যি যে বিস্ময়ে এত বিমূঢ় আমি এর আগে আর কখনো হইনি। এর মধ্যেই শুভ হেসে ওঠে। আমার মনে হয়, কে জানে, শুভ হয়তো এখন কাঁদছে!
(ক্রমশ)