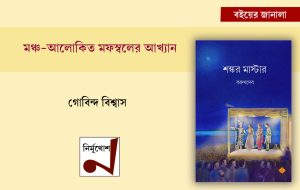উড়নচণ্ডীর পাঁচালি। পর্ব ২৪। লিখছেন সমরেন্দ্র মণ্ডল

অন্য আরেক মেরু
লেখরাজদার দোকান ঘিরে এই যে কর্মকাণ্ড, তাতে অনেকেই সামিল হলেও, এই আড্ডার শরিক সবাই হননি। যেমন দেবদাস আচার্য একটা আলাদা বৃত্তে থাকতে ভালবাসতেন। রথীন ভৌমিক মাঝে মধ্যে আসতেন, বসতেন। তার কাছ থেকেই কলকাতার সাম্প্রতিকতম লেখালেখির ঝাঁঝ পেতাম। শ্রুতি সহ নানা আন্দোলনের খবর পেতাম। তিনিই পড়িয়েছিলেন অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রানা চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল বসু চৌধুরী, রত্নেশ্বর হাজরা, পরেশ মন্ডলের কবিতা। কিন্তু তিনি পরিযায়ী পাখির মতো। আর ছিল শিবাজী রায়। ‘অনিকেত’ নামে একটি পত্রিকা করত। নেতার নিজের মতো থাকত। তারপর হারিয়ে যায়।
আরেকদল ছিল। এরা বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। যাদের কোনও একটি অঞ্চলে কারো বাড়িতে ওদের সন্ধ্যাবাসর ছিল। ওই দলে ছিল শ্যামা বিশ্বাস (রামানন্দ সেন), শান্তি নাথ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, শতঞ্জীব রাহা আর এক বয়স্ক ভদ্রলোক ছিলেন। নাম ঠিক মনে পড়ছে না। তিনি বোধহয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করতেন। আর একজন ছিল পার্থ ভট্টাচার্য। শ্যামা, শান্তি, বিশ্ব, শতঞ্জীব এরা পাঁচজন মিলে একটা কবিতার বই বের করেছিল। আমার কাছে তার একটি ছিল, কোথায় সে গেছে, আর খুঁজে পাচ্ছি না। বারবার বাসা বদল করার ফলে সেটিও বোধহয় হাতবদল হয়ে গিয়েছে। পরের দিকে শতঞ্জীব আলাদা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে সে ওই আড্ডায় যেতো। আমাকেও দু-একবার নিয়ে গিয়েছে। শান্তি-শ্যামারা বের করল ‘কৃকলাশ’। বেশ কয়েকটা সংখ্যা বেরিয়েছিল। কিছুদিন পর ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শান্তি কাঁচড়াপারায় রেলের কারখানায় কাজ পেয়ে যায়। শ্যামা গ্রামে চলে যায় কৃষি উন্নয়ন আর জৈব সার দিয়ে কাজ করতে। শহরের ঐতিহ্যশালী ‘হোমশিখা’ পত্রিকাটি সে নিয়ে নেয়। সাহিত্য পত্রিকাটিকে সে কৃষিপত্রিকা করে দেয়। সঙ্গে ‘শিগক’ নামে একটা সাহিত্য পত্রিকাও বের করতে শুরু করে। শ্যাম-শান্তি বিশ্ব তিনজন সম্পাদক। বিশ্ব কিছুদিন আগে অনন্তলোকে চলে গেছে, তবুও সে এখনও শ্যাম-শান্তির সঙ্গে সম্পাদক রয়ে গেছে।
এই সময়ে মহানগর থেকে প্রকাশিত হল ‘কলকাতা’ পত্রিকা। সম্পাদক জ্যোর্তিময় দত্ত। পূর্বপরিচিতির সূত্রে শ্যামা আর শান্তি সেই পত্রিকায় লিখতে শুরু করল। এই সময়েই বাদল সরকারের সঙ্গে কারো যোগাযোগ হয়। ওর সঙ্গে ছিল রানাঘাটের গৌতম চট্টোপাধ্যায়। বাদল বাবু তখন থার্ড থিয়েটার করছেন। শ্যামা, গৌতম, শান্তি বাদলবাবু এখন শতাব্দী দলকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে এলো। পরিচয় ঘটালো থার্ড থিয়েটারের। ওরা ‘কেভ’ নামে একটা নাট্যদল গড়ে বাদলবাবুকে নিয়ে এসে ক্লাস করাতে শুরু করল। এরই মধ্যে শান্তি একটি নাটক লিখে ফেলেছে। তার মহড়া শুরু হল। শান্তিই নির্দেশক। কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে সে নাটক মঞ্চস্থ হল। না, থার্ড থিয়েটার নয়। প্রসেনিয়াম থিয়েটার। তো সেই প্রথম, সেই তো শেষ, তারপর, যে যার নিজের মতো।
সাদা চামড়ার সাহিত্যচর্চা
এবার একটু ঘুরে অন্যপাড়ায়। মূল শহরের এক পাশে, কৃষ্ণনগরে মহাবিদ্যালয়ের উল্টো দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথলিক চার্চ। গ্রিক ও ইতালীয় ভাস্কর্যের মিলনে তৈরি এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। শহরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এই চার্চ বা গির্জা চত্বরেই বাসভবন ছিল বিকাশ মরোর। মোস্ট রেভারেন্ড বিশপ লুইস এল আর মরো। ইনি ছিলেন মার্কিন নাগরিক। ১৯৪০ সালে তিনি বিশপ পদে মনোনীত হয়ে কৃষ্ণনগর এলেন। তার আগে ছিলেন ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যাথিলাতে। তাঁর বাড়ি ছিল মেক্সিকোতে। ইংরেজিভাষায় তাঁর কিছু বই ছিল, সবই অবশ্য ধর্মীয়। শহরের বুকে তিনি সমাজসেবী হিসাবে খ্যাত হন। কৃষ্ণনগর পুরসভায় দুবার পুরকমিশনার নির্বাচিত হন নির্দল প্রার্থী হিসাবে। একজন ক্যাথলিক পুরোহিত পুরনির্বাচনে প্রার্থী হবেন, সেটা ভারতের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই শুধু নয়, এখনও অকল্পনীয়। শোনা যায়, তাঁর জনহিতকর কাজের জন্যই শহরের বিশিষ্টজনদের অনুরোধে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় অবশ্য তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।
শোনা যায়, স্বাধীনতা লাভের সময় কৃষ্ণনগর পূর্বপাকিস্তানের অংশ হয়ে গেলে, তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃত্বের সঙ্গে তিনিও ব্রিটিশ সরকারের কাছে চিঠি লেখেন। তবে, কৃষ্ণনগর টাউন হল মাঠে প্রথম স্বাধীনতা উৎসব পালনের মঞ্চে তিনি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং কৃষ্ণনগর সহ নদীয়া জেলার উন্নয়নে সামিল হওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করেন। তাঁর এই প্রতিশ্রুতি কেবলমাত্র হাততালি কুড়ানোর ছল যে ছিল না, তা শহরবাসী পরে বুঝতে পারেন। পুর কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর শহরে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহবৃদ্ধি, বিদ্যুতায়নের উন্নতি, সদর হাসপাতালে এক্সরে কমিশনে ব্যবস্থা, রাস্তা সম্প্রসারণ এগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে করেন। এজন্য আমেরিকার বন্ধু ও স্বজনদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন। এছাড়া কৃষ্ণনগর কদমতলা ঘাটের কাছে যে শিশু উদ্যানটি আছে, সেটিও তিনি তৈরি করে দেন। নদীয়া জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণের সময়েও তিনি অর্থ সংগ্রহ করে দেন। শ্রী অরবিন্দ ভবনের যে স্টুডেন্টস হেল্থ হোম আছে, সেখানে প্রতি মাসে অর্থদান করতেন। এইসব অর্থ তিনি বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতেন। ১৯৬৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪ সালে প্রয়াত হন।
এই সমাজহিতৈষী ক্যাথলিক সন্ন্যাসী কৃষ্ণনগর আসার পর ১৯৪১ সালে চারজন তরুণ ক্যাথলিক সন্ন্যাসীকে শহরে দিয়ে এলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন ইতালিয়ান। এঁদেরই অন্যতম ফাদার অগাস্টিন গুয়ারনেরি। তিনি বাংলাভূমিতে এসে বাংলাভাষা আয়ত্ব করেন। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা হয়ে ওঠে। বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে ছিল সম্যকজ্ঞান। ইংরেজি ও ইতালিভাষা থেকে সহজ বাংলায় অনুবাদ করতেন। হাতের লেখাটিও ছিল চমৎকার। প্রথম দিকে মিশন ও স্কুল সভার কাজে ব্যাপৃত থাকলেও, অচিরেই বিশপ মরো তাঁকে গির্জা সংলগ্ন বিশপ হাউসে ডেকে নেন। বিশপ তাঁকে পণ্ডিত নামে ডাকতেন। তাঁর প্রধান কাজ হল বিশপ রচিত ইংরাজি বইগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করে সুলভ মূল্যে সাধারণ ভক্তদের হাতে তুলে দেওয়া। সাতের দশকে এই উড়নচণ্ডী কিছুদিন তার সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। সেই সময় কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, প্রথম অনুবাদের কাজ শুরু সময়, শহরের দু-একজন বিদগ্ধ মানুষের সাহায্য নেন। এ প্রসঙ্গে ‘হোমশিখা’ পত্রিকা ও হোমশিখা প্রেসের মাসিক কালিকাপ্রসাদ বসুর কথা তিনি স্মরণ করেন। কালিকাবাবু পরে পি টি আইয়ের সংবাদদাতা হন। সাতের দশকেই এই উড়নচন্ডীর সঙ্গে কালিকাবাবুর আলাপ হয়। মাঝে মধ্যে হোমশিখা প্রেস ও দপ্তরে পা পড়ত। সেই সময় পুরনো বইয়ের স্তূপের মধ্যে কৃষ্ণনগর চার্চ থেকে প্রকাশিত দু-একটি বই দেখেছিলাম। তখনই জেনেছিলাম হোমশিখা প্রেস থেকে ফাদার অগাস্টিন অনূদিত বই ছাপা হত। অনুবাদের কাজে কালিকাবাবুর ফাদারকে সাহায্য করতেন। তাঁর অনূদিত ধর্মসংগীত সম্বলিত প্রার্থনাপুস্তক ‘আমার সহচর’ ও সম্ভবত পঞ্চাশের দশকেই প্রথম মুদ্রিত হয়। বইটি বিশপ মরো রচিত ‘মাই কম্প্যানিয়ন’ বইয়ের অনুবাদ। তিনি বেশ কিছু বই অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু অনুবাদক হিসাবে নিজের নাম ব্যবহার করতেন না। মৌলিক লেখার দিকে তিনি পা বাড়াননি, তবে কিছু খ্রিস্টীয় গান রচনা করেছিলেন। যেহেতু তিনি আড়ালেই থেকে যেতেন, ফলে দু-একটি ছাড়া তার আর কোনও গানের হদিশ পাওয়া যায়নি। ভারতকে ভালোবেসে তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। আমৃত্যু তিনি বাংলাভাষার সেবা করে গেছেন।
এমনই আরেকজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ফাদার লুচানো কলুসিস। ইনিও ইতালীয়। ফাদার লুচানোর দাদা ও ছোট ভাইও ছিলেন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী। তারা নদীয়ার বিভিন্ন গ্রামে ছিলেন। ছোটো ভাই ফাদার মিলো খ্রিস্টান অর্থনৈতিক অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের অর্থাগমের জন্য বিবিধ প্রকল্প গড়ে তুলে তাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছিলেন। পরে তিনি নদীয়া ছেড়ে চলে যান ভিন রাজ্যে। সম্ভবত কলকাতায় তাঁর দেহান্তর ঘটে। ফাদার লুচানো ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। পুরোহিত-ব্রত নেওয়া পর তিনি গ্রামে গ্রামেই মিশনারি দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন কলকাতায়। বাংলাভাষার নিয়মিত নাটক লিখেছেন, গান লিখেছেন। তিনি ছিলেন মূলত সঙ্গীতজ্ঞ। ভরাট কণ্ঠে গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত। বাজাতেন অর্গ্যান, পিয়ানো অ্যার্কোডিয়ান। কত গান যে তিনি লিখে সুর দিয়েছেন, তার সংখ্যা উড়নচন্ডী রাখেনি। তবে ‘আমার সহচর’ বইয়ে তাঁর বেশ কিছু গান আছে, যা কৃষ্ণনগর ক্যাথলিক চার্চে উপসনায় নিয়মিত গাওয়া হয়। কিন্তু এই গান বইয়ে কোনও সঙ্গীতকারের নাম থাকে না বলেই, মানুষ জানতে পারে না, কোনটি তাঁর গান। উড়নচন্ডীর বেশ মনে আছে, তিনি দুটি নতুন গান রচনা করে ছোটোদের শিখিয়েছিলেন। সম্প্রতি আরেক খ্রিস্টীয় সঙ্গীতকার দিলীপ মজুমদার ফাদার লুচানোর খ্রিষ্টীয় গান সিডিতে ধরে রেখেছেন। এর বাইরেও বেশ কিছু গান আছে। প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা নাটকের বই। সদালাপী, হাসিখুশি মানুষটা ছিলেন কোমলে কঠোর। বাগ্মী হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি কৃষ্ণনগর ধর্মপল্লীর দায়িত্বে ছিলেন, যুব সমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন নানা রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে। ফাদার লুচানোর হাতের লেখা ছিল গোল গোল। বাংলা শব্দের উপর ছিল ভাল দখল। সঙ্গীতে তিনি সুর নিয়ে নিরীক্ষা করেছেন। কখনও ইতালীয় সুর বা পাশ্চাত্যের লোকসঙ্গীত, আবার কখনও দেশি সুরের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে মিশিয়েছেন।
ফাদার অগাস্টিন কিংবা ফাদার লুচানো যেহেতু ধর্মীয় পরিসরের বাইরে বের হননি, ফলে অপরিচিতের গন্ডি অতিক্রম করতে পারেননি। ফাদার লুচানো সঙ্গীতকার হিসাবে হয়তো গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে থেকে যাবেন, কিন্তু ফাদার অগাস্টিন ক্রমশ বিস্মৃতির পথে এগোতে শুরু করেছেন।
এই দুই সাদা চামড়ার যাজকের সঙ্গেই উড়নচন্ডীর ছিল মধুর সম্পর্ক। বিশেষ করে ফাদার অগাস্টিন তো অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আমরা ইতালীয় উচ্চারণে বলতাম আগস্তিন। বেশ মনে আছে, সত্তর দশকের প্রথম দিক। রাজনীতির কারণে কারাবাস, বাংলাদেশ ভ্রমণ সবই সারা হয়ে গিয়েছে। একদিন চার্চ প্রাঙ্গণে বসে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প মারছি, এমন সময় ফাদার আগস্তিন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে। দীর্ঘদেহী ফাদার একটু ঝুঁকে হাঁটতেন। জ্ঞানের গাম্ভীর্য তাঁর মুখমন্ডলে। মৃদুভাষী। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, অফিসে একটু এসো তো।
কথাটা বলেই তিনি সোজা চলে গেলেন প্রেসের দিকে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাধু যোসেফ প্রেস। চার্চ প্রাঙ্গণের এক পাশে পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে তিনি প্রেস খুলেছিলেন। তখনও লেটার প্রেস। ওখানে ছাপা হতো ‘মিলনবীথি’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা আর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ।
গুলতানি মারতে মারতেই নজর রাখছিলাম কখন তিনি অফিসে ঢোকেন। মিনিট পনেরো পরেই দেখলাম সাদা আলখাল্লা (যার পরিচিত নাম ক্যাসাক) পরিহিত ফাদার অফিসের দিকে আসছেন। আমিও উঠে হাঁটা লাগালাম। এটা জানা ছিল, যদি না যাই তিনি অসন্তুষ্ট হতেন, তবে মুখে কিছু বলবেন না।
অফিসের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই বলতেন, এসো। প্রশস্ত টেবিলের একদিকে তিনি কাঠের চেয়ারে বসে, টেবিলের উপরেই একপাশে রাখা টাইপ রাইটার। সামনে ট্রেসিং পেপার ও চাইনিজ কালি আর লম্বা নিবের কলম। কোনও একটা বইয়ের ছবি ট্রেসিং করছিলেন। হ্যাঁ, ফাদার আগস্তিন ভাল ছবি আঁকতেন। সাধু যোসেফ প্রেস থেকে প্রকাশিত অনেক বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি নিজেই আঁকতেন। অনূদিত গ্রন্থের ছবি মূল বই থেকে ট্রেসিং করে নকল করতেন। কিন্তু কদাপি নিজের নামে ব্যবহার করতেন না।
বললেন, বসো।
টেবিলের উল্টো দিকে রাখা খানতিনেক কাঠের চেয়ারের রকটায় উপবেশন করলাম। মনের ভিতর কৌতূহল খেলা করছে, কেন, কী জন্য ডাকলেন। তিনি সব কাগজপত্র একপাশে সযত্নে সরিয়ে রেখে, একটি বই টেনে নিলেন। কোনও ভূমিকা না করেই বসলেন, এই বইটা অনুবাদ করব। তুমি আমায় সাহায্য করবে। কাল সকালে আটটার সময় চলে আসবে। আমার সঙ্গে কাজ করবে। সামান্য কিছু তোমায় সাহায্য করতে পারব। তোমার লেখা আমি পড়েছি। তুমি কাজটা করো।
আমি সম্মোহিত। কোনও রকমে ‘হ্যাঁ’ বললাম। মনে হল তিনি আদেশ করছেন। মৃদুভাষ্যে। বললেন, আজ এসো। কাল আসবে।
কথাটা বলেই তিনি আবার ট্রেসিংয়ে মন দিলেন।
পরদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলাম। তিনি তখন টাইপ মেসিনে খটাখট শব্দ তুলে কী একটা লিখছেন। মাঝে মাঝে হাত জোড় করে ঠোঁটের কাছে ধরছেন, আবার লিখছেন। আমি সোজা অফিস ঘরে ঢুকে খ্রিস্টানি সম্ভাষণ করলাম, যীশুর প্রণাম।
ফাদার মুখ তুলে দেখলেন, আবার লেখায় ডুবে গেলেন। শুধু ইশারায় বসতে বললেন। মিনিট পাঁচেক পর টাইপরাইটার থেকে লেখার কাগজটা বের করে কাগজছাপার নীচে রাখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু বসো।
বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমি বসে টেবিলে রাখা কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে আছি। বেশ কয়েকটা বই। দেখার লোভ লাগছে, কিন্তু অভদ্রতা হবে ভেবে হাত দিচ্ছি না। কখন ফাদার ঢুকেছেন, জানি না। তিনি দু কাপ চা পিরিচে বসিয়ে নিয়ে নিয়ে এলেন। এক কাজ আমার সামনে রাখলেন, অন্যটি তিনি নিলেন। আমার পিরিচে দু পিস পাঁউরুটি মাখন লাগানো। বললেন, আগে খেয়ে নাও।
রুটি এবং চা শেষ করে পাত্রগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ফাদার বললো, রেখে দাও।
একপাশে সরিয়ে রেখে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। আমার দিকে এক দিস্তা লাইন টানা কাগজ আর একটা কলম এগিয়ে দিয়ে, তিনি একটা বই খুললেন। বইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আমি বলে যাব, তুমি লিখবে। পরে তুমি তোমার মত গুছিয়ে লিখে নেবে।
আমি নিশ্চুপে কাগজের ওপর কলম বাগিয়ে বসে আছি। তিনি বললেন, বইটা কিছুদিন আগে বেরিয়েছে।
জিজ্ঞাসা করলাম, লাতিন?
–না, ইতালীয় ভাষায়। বিষয়টা হল যীশুর সমাজবাদী চিন্তাভাবনা। সোস্যালিস্ট যীশু। আমরা পারমিশনের জন্য চিঠি লিখেছি। মনে হচ্ছে পেয়ে যাবো। গভীর আত্মবিশ্বাসী ফাদার। শুরু হল কাজ। তিনি বই সামনে ধরে বাংলায় বলে যাচ্ছেন। আমি শ্রুতিলিখন করছি। বইয়ের শব্দগুলো ইতালি ভাষায়, আর উনি বলে চলেছেন বাংলায়। একটুও হোঁচট খাচ্ছেন না। কথ্য বাংলায় বলে যাচ্ছেন, যেন বইটা বাংলায় লেখা।
প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে লেখা হতো। লেখার কাগজপত্র সেখানেই রেখে আসতে হতো। নিষেধ ছিল কী বইয়ের কাজ চলছে, কাউকে বলা যাবে না। বইয়ের অনুবাদ সম্পূর্ণ হলে, ফাদারের অফিসে বসেই আমাকে সংশোধন বা পুর্ণলিখন করতে হবে। কারণ বইয়ের বিষয় বিতর্কিত। এমন একটা বইয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে ভীষণ উত্তেজিত। নতুন কিছু জানছি। যীশুকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কোনও অবকাশই পাইনি। খুব উৎসাহে কাজটা করে চলেছি।
এভাবে একমাস কাটল। অনুবাদ প্রায় শেষের পর্যায়ে। আর দিন পনেরো বসলেই হয়ে যাবে। ফাদার আমাকে দুশো টাকা দিলেন। বললেন, এটা রাখো।
সাতের দশকে দুশো টাকা মানে অনেক টাকা। এক কাপ চা চার আনা, একটা সিগারেট পাঁচ পয়সা। চারমিনার তিন পয়সা। একজন বেকারের হাতে দুশো টাকা মানে বড়লোক। কাজের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু দিন পাঁচেক পরে আনন্দ ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ফাদার বিষণ্ণ স্বরে বললেন, একটা খারাপ খবর আছে। ইতালিতে বইটি নিষিদ্ধ হয়েছে। এটা নাকি অ্যান্টি ক্রাইস্ট। এই বইয়ের কোনও অনুবাদ বা পুনর্মুদ্রণ রোম থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আমরাও অনুমোদন পাইনি।
হতাশ হলাম। এত ভালো একটা কাজ বাতিল হয়ে গেল। এরপর সেই অনুবাদ পাণ্ডুলিপির ভবিষৎ কী হয়েছিল জানি না। তবে আমার কাজ বজায় ছিল। প্রতিদিন যেতে হতো। কোনও দিন ছোটগল্প, কোনও দিন ছোট প্রবন্ধ অনুবাদ করতে হতো। যে সব ছাপা হতো ‘মিলনবীথি’ পত্রিকায়। কয়েকদিন পর আমায় প্রেসে বসানো হল সহকারী ম্যানেজার করে। প্রেস যিনি দেখাশোনা করতেন সেই লরেন্স স্যার, মানে সমরেন্দ্র লরেন্স বিশ্বাস, শিক্ষকতা করতেন। তিনি বি এড পড়ার জন্য কলকাতায় চলে গেলেন। প্রেসের দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। বছর খানেক পর আমিও পড়াশুনোর জন্য প্রেস ছেড়ে এলাম। আমার জায়গায় অন্যজন বহাল হল। ফিরে এসে আর জায়গা পেলাম না।
কিন্তু একজন সাহিত্যসেবীর পছন্দ মতো কাজ করতে না পারার বেদনা অনুভব করেছিলাম ফাদার অগাস্টিনের মধ্যে। তবে বেশিদিন নয়, আবার তিনি অন্যকাজে ডুবে যান।
(ক্রমশ)