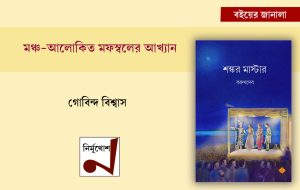উড়নচণ্ডীর পাঁচালি। পর্ব ১৯। লিখছেন সমরেন্দ্র মণ্ডল

নানারঙের দিনগুলি
উড়নচন্ডীর পাঁচালি এলোমেলো হয়ে যায় বয়সের ভারে। এক উড়নচন্ডীর সঙ্গে আরও কত যে উড়নচন্ডী পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটেছিল শহরের পথে, সত্তরের ঝোরো হাওয়ায় উড়ন্ত ধূলো মারিয়ে, সে কথা বিস্মৃত হওয়া মহাপাপ। সেই সব দিনগুলোর কত যে রঙের পরও, যারা বেঁচে বর্তে আছে, তারা প্রান্তিক বয়সে এসে বোধ হয় স্মৃতির ঢেকুর তুলে সময় স্থাপন করেছে। তাদের কথা বলার আগে যে মানুষটির কথা বলা দরকার, তার সান্নিধ্য না পেলে হয়তো শহরে বৃহত্তর মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারতাম না।
মানুষটির নাম বৃন্দাবন গোস্বামী। মূলত গল্প লেখক। চাকরি করতে সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরে। সেই সময়, কংগ্রেসী আমলে, একটা ব্যবস্থা ছিল বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খোঁজ খবর নেওয়ার। দুটো পদ ছিল– বি এইচ ডবলিউ, এস এইচ ডবলিউ। পদগুলোর পুরো নাম আজ আর মনে নেই। সাতাত্তর সালের পর পদগুলি বোধ হয় অবলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা সেই সব মানুষদের আর বাড়ি বাড়ি ঘুরতে দেখা যায়নি।
মাসে একবার করে আসতেন বি এইচ ডবলিউর কর্মী। ওটা বোধহয় ছিল ব্লক হেল্থ ওয়ার্কার। অর্থাৎ ব্লক স্বাস্থ্য কর্মী। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে খোঁজ নিতেন কারো জ্বর আছে কি না বা বড় ধরনের কোনও অসুখ আছে কিনা। থাকলে উপযুক্ত জায়গায় খবর পাঠাতেন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই স্বাস্থ্য কর্মীরা ঘরের দেওয়ালে বা দরজায় রঙিন পেন্সিলে সাক্ষাতের তারিখ আর সই করে যেতেন।
তা বৃন্দাবন গোস্বামীও ছিলেন বি এইচ ডবলিউ। তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খোঁজখবর নিতেন, সই দিয়ে যেতেন। কখনো কখনো অন্য দু-চারটে কথাও বলতেন। একবার পুজোর আগে, তখনও আমার গা থেকে কলেজে পড়ার গন্ধটা সবে সরেছে, তিনি এলেন। তার আজ বোধ করে কাঁধের কাপড়ের ঝোলা থেকে একটা বই বের করলেন। আমি জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে রইলুম। তিনি বিনয়ী কণ্ঠে বললেন, আমরা এই পত্রিকাটি বের করেছি, রাখবেন?
হাতে নিলাম পত্রিকা। পৃথুলা। সবুজ আর লালচে হলুদে এক অপূর্ব প্রচ্ছদ। সূচিপত্র দেখলাম। লেখকদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া সকলেই অপরিচিত। এক, মজনু মোস্তাফা, দুই বৃন্দাবন গোস্বামী। মাকে বলতেই মা দাম মিটিয়ে তিল। পত্রিকাটি রয়ে গেল আমার হেফাজতে।
পুজোর ছুটিটা বেশ কেটে গেল। পত্রিকাটা পড়ে। বেশ কিছু গল্প, কবিতা মগজে গেঁথে গেল। বিশেষ করে ভাল লেগেছিল সমর ভট্টাচার্য, বাবলু বিশ্বাস হরিপদ দের গল্প। তার ‘তিনটি হরিণ শিশু’ তো দীর্ঘ দিন আমাকে ঘোরের মধ্যে রেখেছিল।
পুজোর ছুটি কাটিয়ে মাসিক পরিদর্শনে এলেন বৃন্দাবন গোস্বামী। দেওয়ালে নির্দিষ্ট স্বাক্ষর করার পর জিজ্ঞাসা করলেন, পত্রিকা পড়েছে?
উত্তর দিলাম – পড়েছি।
— কার কার লেখা ভাল লাগল?
বললাম, আপনার গল্পটা বেশ ভাল। একই সঙ্গে জানালাম অন্তযাদের লেখা ভাল লেগেছে, একই সঙ্গে জিজ্ঞাস্য ছিল, বাবলু বিশ্বাস কে?
তিনি জানালেন, চার্চের কাছে বাড়ি।
বললাম, ওখানে যে বাবলুদা থাকে, ফুটবল খেলে -–
বৃন্দাবনবাবু পাদপূরণ করলেন, হ্যাঁ, ওই বাবলু।
বাবলুদাকে আমি চিনতাম। কৃষ্ণনগর কলেজের টিমে খেলত। পরে বোধ হয় কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘের ফরোয়ার্ড ছিল। অপূর্ব পায়ের কাজ ছিল। বেশ নাম ছিল খেলায়। কেটিএস-এর দুটো দল ছিল তখন। একটা বড়দের, অন্যটা ছোটদের। আমি সেই বি গ্রুপে খেলেছি কিছুদিন। বাবলুদারা ছিল ‘এ’ গ্রুপে। সেকারণেই তার সঙ্গে পরিচয় ছিল। যখন জানলাম বাবলুদা গল্পও লেখে, পত্রিকাটা সেই সম্পাদনা করে, বেশ ভাল লাগল।
কিন্তু চমক ছিল অন্যখানে। বললাম, সমর ভট্টাচার্য্যের গল্পটা খুব ভালো লেগেছে।
উনি জিজ্ঞাসা করলেন, সমরকে চেনো না?
হাঁ করে উত্তর দিলাম না তো।
— ও তো এই শ্রীদুর্গা কলোনিতেই থাকে।
আমি অবাক চোখে তাকিয়ে আছি। উনি বললেন, বাছাভাঙা পাওয়ার রাস্তার ডানদিকে সে রাস্তাটা ঢুকেছে, ওখানেই বাড়ি।
বললাম, শীতলদা, গোবিন্দদার বাড়ির কাছে?
উনি সদর্থক উত্তর দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো উত্তর দিলাম, ওখানে তো নানুদার বাড়ি। বিডিও অফিসে কাজ করে। আরে নানুদা তো আমাদের ক্লাবে বই দেয়।
বৃন্দাবন বাবু সহাস্যে উত্তর দিলেন, ওই সমর ভট্টাচার্য। আলাপ করো। বললাম আমি চিনি তো।
এরপরেই তার স্বাভাবিক জিজ্ঞাস্য ছিল আমি লিখি কিনা। এবং হ্যাঁ-সূচক উত্তর পাওয়ার পর লেখা নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলে আহ্বান জানালেন তাদের রবিবাসরীয় সাহিত্যবৈঠকে যোগদান করার। ঠিকানাও দিলেন।
গেলাম একদিন। তারপর আরও একদিন। এরপর মাঝে মধ্যে। এই রবিবারের আড্ডা থেকে বের হত একটা ছোটোপত্রিকা ‘রবিবাসরাৎ’ নামে। সেই পত্রিকাতেও বার কয়েক কবিতা ছেপেছে। সম্পাদক ছিলেন বৃন্দাবন গোস্বামী। পত্রিকা বের হত সেতু সাহিত্য সংস্থা থেকে। অনেকে আড়ালে বলতো বৃন্দাবন গোঁসাইয়ের আড্ডা। কথাটা শুনেছিলাম দেবদাসের মুখে। কিন্তু ওখানে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, যাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল অনেকদিন। ওখানেই আলাপ হয়েছিল সরকার জুটি সুনীল আর মলয়দার সঙ্গে। দুজনেই খবরের কাগজে যে ছোটোদের পাতা থাকত, আনন্দমেলা বা ছোটদের পাতাতাড়ি সেখানে লিখতেন। শারদীয়া সংখ্যাতেও তাদের লেখা থাকত। সুনীল সরকার চাকরি করতেন জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে আর মলয়দা ছিলেন জীবনবীমায়। সুনীলদা নাটক করতেন। তার দলের নাম ছিল ‘সেতু’। জানি না কৃষ্ণনগরে করি ও নাটকাকার তপন ভট্টাচার্য ‘সেতু’ নামে যে দলটি চালায়, তার সঙ্গে কোনও সংযোগ আছে কিনা। মলয়দার বাবার ছিল ওষুধের দোকান। তিনি ছিলেন এল এম এফ ডাক্তার। শহরে বেশ নাম ছিল। দোকানের নাম ছিল সরলা মেডিক্যাল হল। আমরা ওখান থেকে ওষুধ খেতাম।
মলয়দার বাবার একটা নাম ছিল, কিন্তু সেটা প্রায় কেউই জানতো না। সকলে ডাকতো সরলা বুড়ো। দীর্ঘদেহী, ফর্সা, উজ্জ্বল ত্বক, মৃদুভাষী। সাধারণত নিম্নমধ্যবিত্ত আর শ্রমজীবি শ্রেণীর মানুষই তার কাছে যেতো চিকিৎসার আশায়। স্বল্প পয়সায় স্বল্প ওষুধেই রোগীকে সুস্থ করতেন।
সরলা মেডিক্যালের পাশেই বসতেন ডা. কানাইলাল বিশ্বাস। আমরা বলতাম কানাই ডাক্তার। সেকালের এম.বি.। থাকতেন ঘূর্ণির ওদিকে। ছোট কালো রঙের অস্টিন গাড়িতে ক্লিনিকে আসতেন। একদিকে একটা ছোটঘরে তিনি রোগী দেখতেন, পাশের বড় ঘরে, ওষুধ দিতেন তার জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনিও অল্প ওষুধ দিতেন। তার দক্ষিণা ছিল বেশ বেশি। আমরা যকন হাফ প্যান্ট বা ইজের পরার বয়সে সেই ষাটের দশকে পাঁচ টাকার অনেক মূল্য ছিল। বাবার সঙ্গে পূর্ব পরিচিতির সূত্রে আমাদের অসুখ করলে তার কাছেই যেতাম। এখনকার মতো গুচ্ছের বড়ি দিতেন না। কিন্তু অসুখের নিদান পত্রে ওষুধের তালিকাটা দীর্ঘই থাকত। ছোট বয়সে আমরা তো সেসব বুঝতাম না। ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে নিদান পত্র নিয়ে পাশের ঘরে জমা দিয়ে বসে থাকতুম। ডাক্তারবাবুর পুত্র কিংবা কার সহযোগী সেটি নিয়ে আড়ালে চলে যেতেন। এই ওষুধ নেওয়ার গরে সামনের দিকে ছিল দেওয়ালের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছোট মাপের আলমারি, যার মধ্যে থরে থরে ওষুধ সাজানো থাকত। এখনও ওষুধের দোকানে একটা আলমারি দেখা যায়। ঘরের পিছনে থাকত বড় বড় দুটো আলমারি, তার মাঝখানে একজন চলার পথ। সেই আলমারির পিছনে থাকত ওষুধ তৈরির ব্যবস্থা। নিদান পত্র হাতে নিয়ে ডাক্তারের সহকারী, যাদের বলা হত কম্পাউন্ডার, ভিতরে চলে যেতেন। তারপর একটা শিশিতে লাল কিংবা গোলাপী অথবা সবুজ রঙের ওষুধ সামনে রাখতেন। সেই শিশিতে কাগজ কেটে ছ কোণা দাগ দেওয়া হত। আর দিতো কাগজের মোড়কে গুড়ো ওষুধ। আমরা বলতাম পুরিয়া। ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন কখন কিভাবে খেতে হবে। ওষুধের গায়ে বাংলায় লিখে দিতেন।
সরলা বুড়োর ঘরটা ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। ওই একটা ঘরেই তিনি টেবিল-চেয়ারে বসতেন। পাশের আলমারির পিছনে ছিল ওষুধ তৈরির ঘর। তিনি নিদান পত্র লিখে, নিজেই ওষুধ বানিয়ে দিতেন। তার দক্ষিণা ছিল অনেক কম। তবে রোগীর বাড়ি গেলে দক্ষিণার পরিমান একটু বেশিই হত। সঙ্গে রিক্সা ভাড়া। তিনিও গোলা ওষুধ আর পুরিয়া দিতেন। এটাই ছিল সেই সময়ের রেওয়াজ। পরে জেনেছি দু-তিন রকম বড়ি ছোটো হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে পুরিয়া করা হতো। আর কিছু বড়ি গুঁড়ো করে সিরাপ দিয়ে শিশিতে ভরে দিতেন। এর নাম ছিল মিক্সচার। লোকের মুখে মুখে হয়ে গেছিল ‘মিকচার’।
এখন তো সে সব অতীত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে বিশ্বায়নের প্রবাহে সব এলোমেলো হয়ে গেল। ঠিক তেমনই দেবরাজদার দোকানে ঠেক মারার পর থেকেই গোসাই বাগানে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সুনীল সরকারের সঙ্গে দেখা হতো অচিরাও, তবে মলয়দার সঙ্গে দেখা হতো মাঝে মধ্যেই। তবে ওখানেই পরিচয় হয়েছিল স্নেহাশিষ পুকুলের সঙ্গে। পরে তো সে ডাক্তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যায়। আমৃত্যু সে সম্পর্ক বজায় ছিল। আর আলাপ হয়েছিল দীপকের সঙ্গে। ঘন কালো চেহারা, মাথায় ভর্তি চুল, ভালো কবিতা লিখত। পুরোনাম সম্ভবত দীপঙ্কর দাস। আমার ভুল হতেও পারে। তার সঙ্গে কখনো কখনো দেখা হতো। সে রবিবাসরাৎ-এর সঙ্গেই ছিল। আমিই বিচ্ছিন্ন হয়ে লেখরাজদের দোকানে চলে এলাম।
(ক্রমশ)