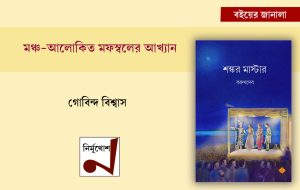রান্নাঘরের গল্প। পর্ব ২। লিখছেন মহুয়া বৈদ্য

সকালবেলায় রান্নাঘরে এসে মায়ের প্রথমকাজ ছিল, রাতে ব্যবহার করা হ্যারিকেনের কালো কাঁচ মুছে, ঘুঁটের ছাই দিয়ে ঘষে তাকে ঝকঝকে করে তোলা, আর তারপর হ্যারিকেনের ডিব্বায় তেল ভরা। এই কাজের পর, বাসি বাসনকোসন কলঘরে রেখে, আগের দিনের ব্যবহার করা জামাকাপড় সাবানজলে ভিজিয়ে, তিনি আঁচ দিতে বসে যেতেন। ততক্ষণে আমি ঘুম থেকে উঠে ব্রাশে মাজন লাগিয়ে সেটিকে হাতে নিয়েছি। দেখতাম, গোবর ল্যাপা পরিষ্কার উনুনে মা প্রথম পরতে দিলেন কাগজের টুকরো অথবা কাঠের পাতলা ছিলা, তারপর ঘুঁটে, তার উপর একটু বড় কাঠের টুকরো, বা কয়েকটা গুল, এবার একেবারে শেষে মায়ের ভেঙে রাখা ছোট ছোট কয়লার টুকরো এক ঝুড়ি। ছোট্ট একটা ঝুড়ি ছিল উনুনের কয়লা তুলে আনার জন্য। তাড়াতাড়ি উনুন ধরার জন্য মা ঘুঁটের উপর একছিপি কেরোসিন তেল দিতেন। এইভাবে উনুন সাজিয়ে তারপর উনুনের নীচের ফোকরে কাগজ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতেন। সেই আগুন উনুনের প্রথম পরতে রাখা কাগজকে জ্বালিয়ে দিত। তারপর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য জিনিসগুলিতে আগুন ধরত, আর উনুনের উপর থেকে বেরিয়ে আসত সেই অদ্ভুত গন্ধের সাদা ধোঁয়া। এই ধোঁয়ার বর্ণ গন্ধ আমাকে এমন টানতো যে আমি অনেকবার মায়ের চোখকে লুকিয়ে এই ধোঁয়ার মধ্যে মুন্ডু গলিয়ে ঘ্রাণ নিয়েছি। কেমন দুলে দুলে ধোঁয়া উঠত তা দেখা আমার একটা প্রিয় বিষয় ছিল। শুধু আমাদের উনুন নয়, একসাথে আঁচ পড়ত আমাদের বাড়িওয়ালা বুম্মির বাড়িতেও। বাড়িওয়ালা বললাম বটে, কিন্তু বুম্মি আমাদের অসম্ভব স্নেহ করতেন। বুম্মির মেয়ে মানাদিদি ফতুদিদির কোলেপিঠে আমি বড় হয়েছি। বুম্মিদের উনুন আর আমাদের উনুনে প্রায় একসাথে আঁচ পড়ত। দুটো আঁচে গলগলিয়ে ওঠা ধোঁয়া কেমন করে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে, সে দেখা আমার কাছে অনেকটা নেশার মতো ছিল। আশপাশের বাড়িতেও প্রায় একই সময়ে আঁচ পড়ত। তখন গ্যাসের চল হয় নি। সমস্ত বাড়ির উঠোন থেকে সকালবেলায় ওঠা ধোঁয়ার সারি আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে খেয়াল করতাম মনে পড়ে। পাড়ায় কার বাড়ির উঠোন থেকে কখন উনুনের ধোঁয়া উঠল সেটা বেশ আলোচ্য বিষয় ও হয়ে উঠত। আজ কারো বাড়িতে আগে বা কারো বাড়িতে পরে আঁচ পড়েছে, অমনি দেখতাম বুম্মি গলা তুলে জেনে নিচ্ছেন, “ কী গো এত সক্কাল সক্কাল আঁচ কেন? “ কিংবা,” আজ এত দেরীতে আঁচ! ঘুমিয়ে পড়েছিলে না কী?” ওপার থেকে কিছু একটা উত্তর ভেসে আসতো, “ এই তো দিদি আজ বাবুর বাবা সকাল সকাল বেরোবে” কিংবা “ না গো দিদি আজ মেয়েটার জ্বর”… এমন কথার উত্তর প্রত্যুত্তর উনানের ধোঁয়ার সাথে আকাশে উড়ে যেতো। পাশাপাশি থাকা দুটি মানুষের সুখদু:খের কথা তাদের আরেকটু কাছাকাছি জুড়ে নিত। অনেকদিন পর, বড় হয়ে মৃণাল সেনের “ চালচিত্র” সিনেমাটি দেখে আমি খুব নস্টালজিক হয়ে পড়েছিলাম। দীপুর ভাই ছাদে দাঁড়িয়ে আশপাশের বাড়ির টালির চাল ফুঁড়ে উঠে আসা উনুনের ধোঁয়া দেখে দাদাকে জিগ্যেস করেছিল, “ কলকাতায় কত উনুন রে?” সিনেমায় ঘুঁটের উপর কয়লা দিয়ে উনুন সাজানোর একটি দৃশ্যও ছিল।
যাইহোক, যে কথা হচ্ছিল, মায়ের আঁচ ধরানোর মধ্যে আমার দাঁতমাজা সারা হত। মা স্নান করতে চলে যেত পুকুরে, আর আমার ডাক পড়ত বুম্মির ঘরেতে। ততক্ষণে বুম্মির বাড়ির সহায়িকা ঘরদোর ঝাঁট দিয়েছেন, আমি সেই ঘরের মেঝে জুড়ে একটুকরো চক নিয়ে অ থেকে ঔ, ক থেকে চন্দ্রবিন্দু, ১ থেকে ১০০ আর a থেকে z লিখবো। আমার লেখা শেষ হলে তারপর সেই ঘর মোছা হবে। আর মায়ের ও চান সারা হ্য়ে যাবে।
বর্ষার দিনে যখন ঢ্যাবঢ্যাবে ভিজে কয়লা আসত, তখন গুলই ছিল সম্বল। ঘেঁষ জল দিয়ে ভিজিয়ে মা গুল তৈরি করে রাখতেন।কয়লার ফুরিয়ে গেলেও এই গুল দিয়েই আঁচ ধরানো হত। দেখতাম গরমকালে যখন রোদ উঠত বেশি, তখন মা গুলের সরঞ্জাম নিয়ে পড়তেন। কয়লার সাথে বস্তাখানেক ঘেঁষ তখন কলঘরের পাশের ঝুপ্সি ঘরে রাখা থাকতো। গরমের ছুটির দিনে রান্নাবান্নার পর মা গুল দিতে বসতেন। আঙুরদিদি সকালবেলার কাজ সেরে ঘেঁষ গুলে রাখত, তারপর মা আর আঙুর দিদি ভাঙা কাঠের টুকরোর উপর টপটপ করে গুল দিয়ে ফেলত। আমিও একটা দুটো দিতাম ধ্যাবড়া করে। কালো ঘেঁষ মাখা দুহাত নিয়ে একবার আঙুর দিদির মুখে একবার মায়ের মুখে মাখিয়ে দেওয়ার ভয় পাওয়াতাম আর হি হি করে হাসতাম। আঙুরদিদি এইসময় মায়ের সহায়িকা ছিলেন। ভালো নাম আঙুরজান খাতুন। আমি আঙুরদিদি বলতাম। টিপটপ পরিচ্ছন্ন বছর বাইশের এই দিদিটি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সকালবেলায় মা উনুনে ধোঁয়া দিয়ে চানে যেতেন, তার মধ্যেই আঙুর দিদি এসে রান্নাঘর মুছে কুটনো বাটনা করতে বসে যেতেন। মা ভেজা কাপড়ে আঁচ তুলে রান্নাঘরে দিতেন। আঙুর দিদি ভাত চড়িয়ে দিত। মা তাঁর সামান্য পুজো-অর্চনা সেরে কাচা শাড়ি পরে মাথার ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে রান্নায় বসতেন। মায়ের হাতের রান্নায় জাদু ছিল সে সময়। সামান্য উপকরণে কী অসামান্য স্বাদের রান্না যে খেয়েছি– সে যেন এক রূপকথার গল্প ।
বিকেল বেলা আমাদের বাড়িতে আর আঁচ পড়ত না। কেরোসিনের জনতা স্টোভে, ভাত ডাল আলু বা পেঁপে বা পটল কিংবা ঝিঙে সেদ্দ আর মাছভাজা এই মেনুই রিপিট হত বেশি। জন্মদিন বিবাহবার্ষিকী এমন বিশেষ দিন হলে আলাদা কথা। এমন একটি দিনের সন্ধ্যার কথা খুব মনে পড়ে। সেদিন অবশ্য কোন বিশেষ দিন ছিল না। কয়েকদিন ধরেই মায়ের কাছে নারকেল দুধের ভাত খাওয়ার বায়না করছিলাম। তখন মা চাম্পাহাটির ভিতর দিকে একটি গ্রামের দিদিমণি। যাতায়াতের জন্য মূলত: বাসই ভরসা। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। মায়ের স্কুলের সময় আমি থাকতাম বড়মাসির কাছে। সন্ধ্যাবেলায় বাবা আমাকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে ফিরতেন। সাইকেলে চড়ে ফিরতামই প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। বাড়ি এসে ঘুমিয়ে যেতাম, আর ঘুমের মধ্যে মা আমাকে খাইয়ে দিতেন। সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে একাহাতে আঁচ ধরিয়ে নারকেল দুধের ভাত রাঁধা চাট্টিখানি কথা ছিল না। তবু, মা রেঁধেছিলেন। খুব মনে পড়ে, মা আমাকে ঘুম থেকে তুলে গোল গোল করে কাটা আলুভাজা দিয়ে নারকেল দুধের ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন, আর বলছেন, “একটু জেগে উঠে খাও, না হলে কী করে মনে থাকবে!” আমার হাতে গোল আলুভাজা ধরিয়ে দিচ্ছেন। আমার তীব্র ভালো লাগছে সেই স্বাদ, কিন্তু ঘুমের আঠায় জড়িয়ে যাচ্ছে দুইচোখ। হাতে আলুভাজা নিয়ে এক গরস ভাত চিবাতে চিবাতেই আবার ঘুমে ঢলে পড়ছি। মায়ের হাতের বিভিন্ন সুস্বাদু রান্নার প্রথমদিকের লিস্টে ছিল এই নারকেল দুধের ভাত।
বোন হওয়ার একবছর পর আমরা দেশের বাড়িতে চলে গেলাম নিজেদের বাড়ি করে। সেখানে রান্নাঘরের ভিত করা হলেও, দেওয়াল ছিল দরমার বেড়ার, মাথায় ছিল টালির চাল। এই রান্নাঘর ঠিক আগের মতো সাজানো হলেও এর সাথে নতুন যে জিনিসটি রান্নাঘরে যুক্ত হল, তা হল কাঠের উনুন। বাড়ির লাগোয়া পেয়ারা বাগানের অসংখ্য পাতা আর শুকনো ডালে সেই কাঠের উনুনে সাঁই সাঁই রান্না হত। এখানে এসে প্রথম মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না শুরু হল। কাঠের জ্বালে মাটির হাঁড়িতে রান্না হওয়া ভাতের সুবাস এখনো আমার নাকে লেগে আছে। হালকা ধোঁয়া আর মাটির গন্ধ মেশা দেশি চালের ভাতের গন্ধের কোনো তুলনা হয় না। এই ভাতের গন্ধ একান্তই আমার মেঠো গ্রামবাংলার ভাতের গন্ধ।
গ্রামে এসে প্রথম নিজেদের রান্নাঘরে খই মুড়ি ভাজা দেখলাম। এইসময় আমাদের বাড়িতে মায়ের সহায়িকা হিসেবে এলেন চাচী। তিনি এসবের উদ্যোক্তা ছিলেন। কালো বালির মধ্যে ধান দিয়ে অনেকগুলি নতুন খ্যাংরা কাঠি বিশেষ কায়দায় ধরে ধান নাড়ানো হত। মুহূর্তের মধ্যে ধান ফুটে সাদা সাদা খই ফুটতো। খই যাতে ছড়িয়ে না যায় সেজন্য একটা বালি চালুনি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। আমার কী ভালো যে লাগতো খই ভাজা দেখতে! যেন কালোবালির অন্ধকারে জোনাকপোকা জ্বলে উঠলো, এমন মনে হত। আর খই এর চেয়ে বেশি সাদা আর কিছুই যেন হতে পারে না, এমন ও মনে হত।
মুড়িভাজার কথাও খুব মনে পড়ে। মুড়ি ভাজার সময় মুড়িগুলো খইয়ের মতো অত ছিটকে যেত না। মুড়ির চাল আধঘন্টা জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর সেগুলিকে নুন হলুদ মাখিয়ে চাচী বস্তার উপর মেলে দিত। চাল শুকিয়ে ঝরঝরে হলে, তাকে প্রথমে বালিতে ফেলে হালকা নেড়ে তুলে নেওয়া হত। তারপর খানিক বাদে আবার সেই চাল যেত তপ্ত বালিতে। এবার সেই খ্যাংরা কাঠির গোছা দিয়ে বিশেষ কায়দায় নাড়লেই ফোলা ফোলা হলদেটে মুড়ি তৈরি হয়ে যেত। হলুদ-নুন মাখা গরম গরম সেই মুড়ির স্বাদই অন্যরকম। সেই স্বাদ চাচীর চলে যাওয়ার সঙ্গে হারিয়ে গেছে একেবারে। শীতের দুপুরে চাচীর সাথে বসে উনানের মুখে অল্প অল্প শুকনো পেয়ারা পাতার জ্বাল দিচ্ছি, আর চাচী প্রায় আট-দশ খোলা মুড়ি ভেজে ফেলছে, এই স্মৃতি খুব মনে পড়ে।
দেশের বাড়িতে আমরা বছর খানেক ছিলাম। তারপর মায়ের স্কুল যেতে অসুবিধা হওয়ায় আমরা আবার বারুইপুরে চলে আসি। আবার ভাড়া বাড়ি। আবার নতুন রান্নাঘর। এবারের রান্নাঘরটি ছিল, মাটি লেপা, কঞ্চি বসানো রান্নাঘর, তাতে টিনের দরজা। খুব অসুবিধা পোহাতে হয়েছে মাকে এই রান্নাঘরে। প্রথমত এখানে মায়ের সাধের আলমারি রাখা যেত না, তারপরে বৃষ্টি হলে এত জলের ঝাট আসত যে রান্না করা যেত না। তারপর ফাঁকফোকর গলে বেড়াল তো এসে যেতই। আজ মাছ কাল দুধ ক্রমাগত তাদের পেটে চালান হতে লাগলো। বর্ষাকালে যখন কিছুতেই আর সে রান্নাঘরে করা যেত না, তখন ঘরের ভিতর একপাশে কেরোসিনের স্টোভে রান্নাবান্না করা হত। কিন্তু ঘরের মধ্যে রান্না করা যাবে না বলে বাড়িওয়ালা ঝামেলা করায় আমাদের খুব হঠাৎ করেই বাসাবদল করতে হল। আমার মনে আছে, দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন যখন সারাপৃথিবী উৎসবে ভাসছে, আমরা তখন বাসাবদলের জন্য পোঁটলাপুটলি বাঁধছি। অষ্টমীর সকালে করা লুচিটুকুও পোঁটলার মধ্যে চলে গেল।
বাসাবদল করে আমরা এলাম কাজী সাহেবদের বাড়ি। এরা আমাদের অসময়ের আশ্রয়দাতা। নবমীর সকালে আমরা কাজীসাহেবের বাড়িতে আমাদের পোঁটলাপুটলি নিয়ে হাজির হলাম। সারারাতের গোছগাছের ক্লান্তির মাঝে আমাদের সেদিন রান্নাবান্না হল না। অষ্টমীর সকালের সেই লুচিই আমরা খেলাম। কারো কিছু হল না, কিন্তু আমার পেটে সেই লুচি সহ্য হল না। বমি পেটখারাপ একসাথে হয়ে এক্কেবারে কাহিল হয়ে পড়লাম আমি। সেবারের পুজো একেবারে জঘন্য কাটলো।
(ক্রমশ)