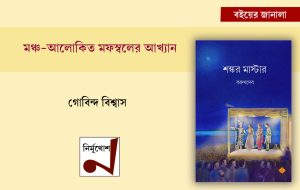রান্নাঘরের গল্প। পর্ব ১। লিখছেন মহুয়া বৈদ্য

এ পর্যন্ত জীবনে পঁচিশটি রান্নাঘরের রান্নার সঙ্গে নিজে সম্পৃক্ত হয়েছি। এর মধ্যে এগারোটি রান্নাঘর আমার নিজের সংসারের। মানে এগারোবার বাসা বদল হয়েছে। বাকি গুলি দিদা মামী মা মাসিদের। জেনারেশন হিসেবে ধরলে তিন জেনারেশনের রান্নাঘরের জ্যান্ত সাক্ষী আমি। রান্না যেহেতু একসময় খুব প্রিয় বিষয় ছিল, তাই রান্নাঘর নিয়ে আদিখ্যেতা ও ছিল প্রচুর। সুদীর্ঘ ২০ বছরের বিবাহিত জীবনে যে কাজটি তুমুল ভালোবেসে করেছি সেটি হল রান্না। ১৯ বছর বয়সে ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করলাম, তার আগে আমার রান্না বলতে, একবার মাত্র কাঠের উনুনে, ভেজে রাখা মাছের ঝোল রান্না। দিদার খুব শরীর খারাপ হলে আমরা মামারবাড়ি ছিলাম রাতে, পরদিন খুব ভোরে বাড়ি ফিরে মায়ের নির্দেশ মতো বাবার জন্য বরবটি কড়াই আর আলু দিয়ে মাছের ঝোল রেঁধেছিলাম। শুধু বাবার জন্যই রাঁধতে বলেছিল মা, বেলায় ফিরে সবার জন্য নিজে রাঁধবে এমনই কথা ছিল। তা প্রথম রান্না বলে কথা, বাবা থালা চেটেপুটে খেয়ে যাওয়ার পর, ছোট্ট একটা বাটিতে মায়ের জন্য রেখেছিলাম, টেস্ট করাব বলে। মা এল, খেল, ফটাস করে আমার গালে একটা চড় কষিয়ে বলল, রাঁধলি যখন পুরোটা রেঁধে রাখলি না কেন। হতভম্ব আমি সেই যে রান্না বিমুখ হলাম, ১৯ বছর বয়স অবধি আর রাঁধি নি। এসব ক্লাস সেভেনের কথা। তখন আমাদের নিজেরদের বাড়ি হয়েছে। মায়ের রান্নাঘর দরমা দিয়ে ঘেরা আর তাতে টালির চাল, মাটির মেঝে। তখন রান্নাঘরে গ্যাস এসেছে। তবু একপাশে ছিল কাঠের উনুনের বন্দোবস্ত। গ্যাসের উনুন জ্বালাতে গিয়ে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, সেইজন্যই মা আমাকে কাঠের জ্বালে রাঁধার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
নারকেল দুধের ভাত
জ্ঞান হওয়া ইস্তক মায়ের যে রান্নাঘর দেখেছি, সেটি এখনকার যে রান্নাঘরের ধারণা, তার সাথে একেবারেই যায় না। আমাদের বাসাবাড়িতে আমাদের শোয়ার ঘরে ছিল একটা তক্তোপোষ, সেটা ইঁট দিয়ে এত্ত উঁচু করা। তার নীচে গোটা চারেক ট্রাঙ্ক, তাতে জামাকাপড় বইপত্তর। আর তার সামনে একটা খোলার টালি দেওয়া বড় জায়গা, যার আদ্দেকটায় সিমেন্টের মেঝে, আদ্দেকটা মাটি। সেখানে জানালা ছিল দুটো, কাঠের ফ্রেম, কাঠের দাঁড়া এবং কপাটের, যা আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। সস্তার জানালা, রাসেরমেলা থেকে কেনা, ঘূণ ধরা থেকে বাঁচাতে তাতে দেওয়া ছিল কালো আলকাতরার পোঁচ। এইখানেই আমার মায়ের রান্নাঘর, এইখানেই আমাদের আসন পেতে খাওয়া— আজকের ভাষায় যারে বলে কিচেন কাম ডাইনিং। এই রান্নাঘরের প্রাণ ছিল একটা এই এত্তবড় কাঠের লম্বা আলমারি, যার পেছনটা কাঁচ দেওয়া। আজকাল মিষ্টির দোকানে যেমন শোকেস থাকে জিনিটা অনেকটা সেইরকম ছিল। মানে কাঁচের দিকটাই সামনে থাকার কথা, মা এটিকে নিজের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করছিল। মায়ের কাছে শুনেছিলাম, বিয়ের পর আমাদের দেশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে বারান্দার এককোণে অতি অবহেলায় মা এটাকে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। দিদিশাশুড়িকে কেন পড়ে আছে জিগ্যেস করায় তিনি বলেছিলেন, রাগ হলে সবাই ওতে নাকি লাথি মেরে রাগ মেটায়। তো আমার মা সেইসময়ের তাঁর টানাটানির সংসারে সবার লাথি-খাওয়া এই শোকেসটিকে রান্নাঘরের আলমারি করেবেন বলে চেয়ে নিয়েছিলেন। ভাঙাচোরা লাথ-খাওয়া সেই শোকেস মায়ের সাধের রান্নাঘরের আলমারি হয়ে ছিল সুদীর্ঘ সময়। মা সেটিকে সারিয়ে নিয়েছিলেন। এই যে আলমারি, এতে মায়ের যাবতীয় রান্নার মশলাপাতি, আমাদের ছোটবেলার দুধ বিস্কুট ছোলাবাদামভাজা ইত্যাদি সবকিছুই থাকতো। এর সাথে রান্নাঘরের সরঞ্জাম বলতে ছিল মায়ের তোলা-উনুন, কয়লা অথবা গুল দিয়ে যাতে আঁচ পড়ত, ছিল কেরোসিনের জনতা স্টোভ আর একটা শিলনোড়া। রান্না-খাওয়ার সমস্ত বাসনপত্র থাকতো এই আলমারিরই উপরে। একটা মস্ত অয়েল ক্লথ বিছানো থাকতো আলমারির কাঠটিকে জলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। এই আলমারিটা এত বড় ছিল মাঝে মাঝে জিনিসপত্র কোন কাণায় হারিয়ে যেন, তারপর বেশ কদিন পর হয়ত ওইদিকে সেই কোণা থেকে আবিষ্কার হল একদলা কালো কুচকুচে তেঁতুল, হরলিক্সের কাঁচের বয়ামে; এইকোণা থেকে আড়াইশো মতো মিছরির দানা, কিংবা ভুলে যাওয়া পাঁপড়ের প্যাকেট…এইরকম আর কি!
তখন বাটা মশলায় রান্না হত বলে শিলনোড়ার খুব যত্ন ছিল। ঠিক পুজোর আগে আগে একজন বোবা শিলকাটিয়ে আসতেন শিলকাটতে। তিনি বাটালি দিয়ে কী অনায়াসে এইটুকু সময়ের মধ্যে শিলের উপর এঁকে দিতেন লাফিয়ে ওঠা মাছ, কিংবা পদ্ম ফুল! আমি নড়তাম না তার পাশ থেকে। পাথরের উপর অমন করে ছবি আঁকা দেখে আমার তাক লেগে যেত!
সেই সময় শিলপাটায় জিরে ধনে আদা লঙ্কা, এসব বাটা তো হতই, এমনকি হলুদ ও বাটা হত। গুঁড়ো মশলার চল তখনো এদিকে শুরু হয় নি। শক্ত হলুদের গাঁট মিহি করে বাটা সহজ কাজ ছিল না। আঙুরদিদি চন্দনের মতো মিহি বাটনা বাটতে পারতো বলে মায়ের কাছে খুব প্রশংসা পেত। মাঝেসাঝে একটু বেশী মশলা বাটা হয়ে গেলে দেখতাম, মা সেই মশলা নুন সর্ষের তেল দিয়ে মেখে কৌটোয় তুলে, সেই কৌটো জলের উপর বসিয়ে রাখতেন। পরের দিন রান্নায় সেই মশলা দিব্যি ব্যবহার করা যেত।
রান্নাঘরের কয়লা ঘুঁটে ঘেঁষ ইত্যাদি থাকত বাইরে কলঘরের পাশে একটা ঝুপসি মতো ঘরে। তখন ঘটেদা মাসের শুরুতে ভ্যানে করে বস্তাভর্তি কয়লা দিয়ে যেতেন। একটু বেঁটে-খাটো ঘটেদার বাড়ি ছিল আমার বড়মাসির বাড়ির পাশে। ফলে কখনো কখনো ছোট্ট ছোট্ট টিফিন কৌটো এইবাড়ি থাকে ওইবাড়িতে পৌঁছে দিত ঘটেদা। ছুটির দিনে কয়লার বস্তা নামিয়ে মায়ের সঙ্গে তার একটুখন গল্পস্বল্প চলত। “ দিদিকে আজ দেখতে পেলে, ও ঘটে? ও বাড়ির সবাই ভালো আছে গো…?” কিংবা “খুব বড় বড় চাঙড় দাও নি তো? আগেরবার সব বড় বড় কয়লা ভাঙতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে..” এমন কথাবার্তাই হত বেশী। একটা মোটা চ্যাপ্টা লোহার রড দিয়ে মাকেই কয়লা ভাঙতে দেখেছি, ছোট ছোট টুকরো করে আঁচ দেওয়ার উপযোগী করে তিনি ভেঙে নিতেন।
আঁচ ধরানোর ঘুঁটে দিতে আসতেন পাশের পাড়ার পাঞ্চালীর মা। আজ থেকে কয়েক দশক আগে তিনি স্পর্ধা করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন পাঞ্চালী, এ ভেবে পরে খুবই বিস্মিত হয়েছি! পাঞ্চালীর মায়ের মুখে সামনের পাটির দাঁত ছিল না। মাথার চুল কোঁকড়া, কাঁচা পাকায় মেশানো, বরাবর তাঁকে কস্তাপেড়ে শাড়ি পরতে দেখেছি। পাঞ্চালীর মায়ের ঘুঁটে বানানোয় যত্ন ছিল। গোবরের মধ্যে খড়ের কুঁচি ধানের ভুষি এসব দিয়ে এই এত্ত বড় বড় পাঞ্জার সাইজে ঘুঁটে বানাতেন তিনি। ফলে তার ঘুঁটের চাহিদা ছিল। বিকেলের দিকে পাঞ্চালীর মা তার কোঁকড়া চুলকে তেল দিয়ে যতদূর সম্ভব বিন্যস্ত করে একটা আলগা খোঁপা বাঁধতেন। ধোয়া শাড়ির সাথে কপালে থাকত একটা বড় লাল সিঁদুরের টিপ আর মাথা ভর্তি সিঁদুর। কানে থাকত সস্তার পিতলের মাকড়ি। হাতে শাঁখা-পলা-নোয়া। কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচলের একংশ তার মাথায় আধাঘোমটা হয়ে উঠে থাকতো। আর, তার পিঠে থাকতো একটা বিশাল বড় এক পাটের বস্তা, অনেকটা সান্টাক্লজের ঝোলার মতো সেটা ঝুলতো। সেই ঝোলা ভর্তি থাকত উৎকৃষ্ট মানের ঘুঁটে। তখন ঘুঁটে বিক্রি হত পণের হিসেবে। ২০ গন্ডায় এক পণ আর চারটেতে এক গন্ডা। এক একবারে পাঞ্চালীর মা পাঁচ-ছ’পণ ঘুঁটে নিয়ে চলে আসতেন এবং তার বস্তা খালি হয়ে যেত।
এই চারটে ঘুঁটে একসঙ্গে করে কুড়ি গন্ডা গোনা, এই বিষয়টিতে আমার দারুণ মজা লাগতো। আছে চার অথচ গুনছে এক, এ আমার কাছে চরম বিস্ময়ের ছিল। আর কোথাও তখন এই হিসেবে গোণাগুন্তি চালু ছিল না। ঘুঁটে গুনে বস্তায় পুরে সেইবস্তার মুখ বেঁধে কলঘরের পাশে রেখে তবে পাঞ্চালীর মা মুখ তুলে চাইতেন। ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে বলতেন,” দিদিমণি একটু চা দিবে না? তোমার হাতে চায়ের সোয়াদ বড় ভালো”। এ গল্পে সে গল্পে চা খেয়ে ঘুঁটে বিক্রির খুচরো পয়সাটুকু আঁচলের খুঁটে বেঁধে কোমরে গুঁজে তিনি উঠে দাঁড়াতেন। তিন ঝাপ্টায় ঘুঁটের বস্তার কুটো ঝেড়ে তাকে পাট করে বগলদাবা করে ঘরের দিকে হাঁটা দিতেন।
আমার মা সেই সময়ে স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। এই সব কাঠ কয়লা ঘুঁটে গুল… এতকিছু সামলে, সঠিক সময়ে রান্নাবান্না সেরে তিনি কী করে স্কুলে পৌঁছাতেন এবং কী ভালোবেসেই না বাচ্চাদের পড়াতেন, সেসব ভেবে আজ এখন আমি বিস্মিত হই।
(ক্রমশ)