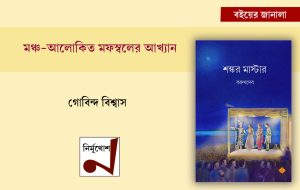উড়নচণ্ডীর পাঁচালি। পর্ব ২৬। লিখছেন সমরেন্দ্র মণ্ডল

আরও কিছু কথা রইলো পড়ে
জীবনের পাঁচালিতে কত কথা হারিয়ে যায়, কত কথা পড়ে থাকে অবহেলায়। স্মৃতিও কখনও কখনও লুকোচুরি খেলে। যখনই মনে হয় এবার বোধহয় শেষ হলো, তখনই কোন গহ্বর থেকে উঠে এসে বলে, ধাপ্পা। অমনি সেইসব মুখ সামনে আসে, অথচ আরো আগেই আসার কথা ছিল যাদের। এই যেমন প্রাণেশ। প্রাণেশ সরকার। বাদকুল্লা, সুরভিস্থান। পড়তো ইংরাজি নিয়ে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে। একটু একা একা থাকত। কিন্তু কেমন করে যেন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে ছেলেবেলা। একদিন সেই দারিদ্র্যকে রুখে দিয়েছে। বাদকুল্লা থেকে কৃষ্ণনগর আসতো পড়তে। সময় নষ্ট করতো না। তারই ফাঁকে দুচার কথা হতো। কখনও ওর বাড়ি গিয়েছি কথা বলতে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই সে কবিতা লিখে বেশ পরিচিতি পেয়েছিল। বেশ কিছুদিন পর জানা গেল প্রাণেশ কৃষ্ণনগর পুরসভায় চাকরি পেয়েছে। আরও সুবিধা হলো আমাদের। কোনও কোনও দুপুরে ওর দপ্তরে হানা দেওয়া হতো আড্ডা মারতে। এই আড্ডাসূত্রে আরও ঘনিষ্ঠ হলাম আমরা। ততদিনে বোধহয় ওর একটা কবিতার বইও বেরিয়ে গেছে। লিখছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কোনও কোনও কবিসভায় চলে যায় হই হই করে। তারপর একদিন চলে গেল স্কুলে মাস্টারি নিয়ে। কালীনগর হাইস্কুলে। ওখান থেকেই অবসর নিয়েছে সে। লিখছে, লিখে যাচ্ছে অবিরাম।
সত্তর দশকে উড়নচন্ডীদের লেখালেখির এই যে প্রবাহ শুরু হয়েছিল, তা আজও বয়ে চলেছে অবিরত। কোনও কোনও নদী যেমন অবহেলায় শুকিয়ে যায়। তেমনই কতজন পথ ভ্রষ্ট হয়ে কলম ছেড়ে দিয়েছে। আবার কতজন জীবনের মাঝ পথে চলে গেছে অন্তরীক্ষে। যেমন, সঞ্জীব প্রামাণিক। গ্রামের ছেলে এসেছিল শহরে। খুব কম বয়সে বিয়েও করে ফেলেছিল। থাকতো ভাড়া বাড়িতে। করতো টুইশানি। কবিতা অন্ত প্রাণ। লিখতো নানা পত্রিকায়। শহরের কবিদের মধ্যে ঠাঁয় করে নিয়েছিল সে। দলের মধ্যে থাকলেও দলে ছিল না সে। একটু একা থাকতে ভালবাসতো। কারো কারো সাথে গভীর সম্পর্ক হয়েছিল, যেমন উড়নচন্ডীর। সাধারণত জজকোর্টের মাঠের একধারে বসে গল্প করতো। কোনওদিন থাকতো শতঞ্জীব। বোধ হয় ছাত্র পড়ানোর চাপ আর দারিদ্র্য তাকে নিরালা খুঁজে নিতে বাধ্য করতো। একদিন সে চাকরি পেয়ে গেল উত্তরবঙ্গে। তখন শহরের সঙ্গে সখ্য কিছুটা কমে গেল। মাসে একবার করে আসতো। তখনই দেখা, কথা। বারবার বলতো, চলো আমার ওখানে। কদিন ঘুরে আসবে। তখন আমার পকেটও তো গড়ের মাঠ। একটা মাত্র ছাত্র পড়ানোর ওপর নির্ভর। ফলে যাওয়া হলো না কোনওদিন। পরে যখন মালদায় গেলাম, তখন সে চলে এসেছে নদীয়ায় এক গ্রামের স্কুলে হেড মাস্টার হয়ে। আমিও কৃষ্ণনগর ছাড়া। তবে কলকাতার রাজপথে, কলেজস্ট্রিটে দেখা হয়ে যেতো অবরে সবরে। একদিন মুঠোফোন বাহিত সংবাদে জানা গেল সজীব অকস্মাৎ পৃথিবী পরিত্যাগ করেছে। রয়ে গেছে তার বেশ কিছু কবিতা বই, পুরস্কারের স্মারক আর সম্পাদিত পত্রিকার ছিন্নসংখ্যা।
সঞ্জীবের মতো নয়, অনিল চলে গেছিল সকলকে জানিয়েই। এবং অনেক দিনের প্রস্তুতি নিয়ে। সকলেই জানতো ওকে ছেড়ে দিতে হবে, তবে সকলেই শেষ চেষ্টা করেছিল আটকে রাখার। বলছি অনিল ঘড়াইয়ের কথা। বাংলাসাহিত্য প্রান্তজনের জীবনসংবেদ লিখে নিজের নাম করে নিয়েছে। অনিল নিজেও ছিল প্রান্তজন গোষ্ঠির মানুষ। নিজের পরিশ্রম আর মেধায় ওপরের সারিতে উঠে আসে। অনিল চলে যাওয়ার পর, ইদানিং দেখা যাচ্ছে অনেকেই দাবি করছেন, তাঁরাই নাকি অনিলকে আবিষ্কার করেছিলেন। হয়তো হবে, হয়তো নয়। তবে মজনুর আগে কেউ তাকে কৃষ্ণনগর শহরে চিনতো বলে মনে হয় না। অন্তত এই উড়নচন্ডীর তো জানা নেই।
বেশ মনে এক বিকেলের কথা। তখন গরমকাল। সেই বিকেলে সঞ্জীব আর আমি জজ কোর্টের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। হঠাৎই ঝড়ের মতো মজনুদা এলেন। হাতে একটা পত্রিকা। কৃষ্ণনগর বিপ্রদাস ইনস্টিটিউড অফ টেকনোলজি, যার চলতি নাম এলসি কলেজ, সেই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকা। মজনুদা পত্রিকা খুলে দেখালেন একটি গল্প। লেখক অনিল ঘড়াই। বৈদ্যুতিক বিভাগের ছাত্র। সম্ভবত দ্বিতীয় বছরে পড়তো সে। এখন আর মনে নেই। মজনুদা বললেন, খুব ভালো লেখে ছেলেটা। ওর সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি। তোমরা যাবে?
আমরা এক কথায় রাজি। ছেলেটি কলেজ হস্টেলে থাকে। পদব্রজে রওনা হলাম।
তিনজনে হাজির হলেম এল সি কলেজের হস্টেলে। মজনু সম্ভবত আগেই কিছু খোঁজখবর নিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সটান উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। আমরাও পশ্চাতে ধাবিত হলাম। খুঁজে পাওয়া গেল তাকে। ঘরেই ছিল। একটা ঘরে বোধ হয় দুজনের বিছানা ছিল দুটি কাঠের চৌকিতে। কালোকুলো, ঘনকালো চুলের ছেলেটির মুখে স্বর্গীয় হাসি। বিনয় ঝরে পড়ছে। আমরা বসলাম ওর বিছানায়, পরিচয় পর্ব সারা হতেই সে আরও বিগলিত। মজনুদা আর সঞ্জীবকে সাক্ষাতে পেয়ে সে আপ্লুত। তাকে আহ্বান জানালেন মজনুদা তার বাড়িতে, আমরা জজ কোর্টের মাঠের আড্ডায়। সে বিগলিত হয়ে জানালো, আসবে নিশ্চয়। ওর বাড়ির হদিশ জেনে নিলেন মজনুদা। দেবগ্রাম স্টেশনে নেমে কালীগঞ্জ হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আবাসনে তারা থাকতেন।
ওদের কলেজের গ্রীষ্মের ছুটিতে এক বিকেলে চলে গেলাম কালীগঞ্জে। অনিলদের বাসায়। মজনুদা, সঞ্জীব আর এই উড়নচন্ডী। সেসব কথা লিখেছি অনেকবার, অনেক জায়গায়, আবারও বলতে হচ্ছে। ওদের আবাসনে অর্থাৎ বাসায় যাওয়া এক অভিজ্ঞতা। তখনই টের পেয়েছিলাম, একজন সামাজিকভাবে অন্ত্যজ শ্রেণির যুবক, অভাব-অনটনের মধ্যে থেকেও কীভাবে প্রতিষ্ঠার লড়াই করে চলেছে। তার না আছে অহঙ্কার, না আছে কৌলিন্য। তার অমলিন হাসি আর বিনয়ের লুকিয়ে আছে জেদ।
ক্রমশ সে বেশ পরিচিত হয়ে গেল আমাদের। পড়াশুনো ঠেকিয়ে সে কখনো সখনো চলে আসতো জজ কোর্টের মাঠে, কিছুক্ষণের জন্য। তবে আসতো ছুটির সকালে। যেতো মজনুদার বাড়ি। বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল আমাদের বন্ধু সুবীর সিংহরায় আর সমর ভট্টাচার্যর সঙ্গে। ও বোধহয় তখন শেষবর্ষের ছাত্র। তখন ওর বন্ধু মানে দেবগ্রামের বন্ধু তাপসকুমার রায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে বের করল একটা পত্রিকা। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। ওই পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল ওর বিখ্যাত গল্প ‘শষ্যকুমারীর চর্যাপদ’। গল্পের অপূর্ব নামকরণ করতো অনিল। তারপর ও একক ভাবে বের করেছিল ‘কোয়েল’ নামে একটা পত্রিকা। হয়তো ‘কোয়েল’ আগে, ‘শব্দযুগ’ পরে। হতেও পারে। স্মৃতি তো সবসময়ে সরল রেখায় হাঁটে না।
অনিল কলেজ শেষ করে যখন চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই সময়টায় কৃষ্ণনগরে আসা বেড়ে গেল। আসতো সুবীরের বাড়ি, সমরদার বাড়ি। আমাদের বাড়িও এসেছে বারদুয়েক। একবার দুপুরে খাওয়াদাওয়াও করেছিল। সমরদার বাড়িতেও আতিথ্য গ্রহণ করেছে। সমরদার অফিসে চলে যেতো কোনও সময়। সমরদা তখন বিডিও অফিসে নৈশপ্রহরীর কাজ করে, অনিল একবার সেখানে রাত্রিবাসও করে।
কৃষ্ণনগর শহরের অপর প্রান্তে, শক্তিনগরের প্রবীর আচার্যর সঙ্গেও ওর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রবীর একসময় সেনাবিভাগে কাজ নিয়ে চলে গেল। তখন আর অনিলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না। পরে যখন সে সেনাডাক বিভাগে কাজের চুক্তি শেষ করে কৃষ্ণনগরে মুখ্য ডাকঘরে এলো তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ গড়ে উঠল। ততদিনে অনিল সাহিত্যের বাজারে বেশ পরিচিত নাম। অনেকগুলো জাতীয় পুরষ্কার তার ঝুলিতে। পেয়েছে বঙ্কিম পুরষ্কার। কিন্তু তখনও তার হাসি অনলিন। রয়েছে বিনয়। রেল দপ্তরে সে তখন অনেক উঁচু ও দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরি করছে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণনগরের সঙ্গে তার যোগাযোগ কমে গেছে।
বেশ মনে আছে, এর প্রথম গল্পগ্রন্থ বেরোবার আগে কিছুক্ষণের আলাপচারিতা। আটের দশকের প্রথম দিন। তখন সদ্য যুক্ত হয়েছি ইত্যাদি প্রকাশনীর নবম-দশম পত্রিকায়। তখনও পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেনি। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। হঠাৎই দপ্তরের দরজায় কে যেন ডাক দিল। তাকিয়ে দেখি অনিল!
বিস্মিত আমি। দ্রুত বাইরে এলাম – তুমি!
-শুনলাম তুমি এখানে জয়েন করেছ। দেখা করতে এলাম।
-এখন কোথায়?
-চত্রধরপুরে আছি। গতকাল এসেছি। দমদমে এক বন্ধুর বাড়িতে আছি। সুব্রতদার কাছে এসেছিলাম। ওখানে মৃদুলদা বলল তুমি এখানে আছো।
এখানে ফুটনোট দিই, সুব্রতদা মানে গল্পকার সুব্রত রাহা। ‘কালপুরুষ’ নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন করতেন। আর মৃদুল হলেন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত। আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু। ওরা দুজনেই পরিবর্তন পত্রিকায় সম্পাদনা বিভাগে ছিলেন। মৃদুল সাংবাদিকতাও করতেন।
যাহোক, দপ্তরে বলে অনিলকে নিয়ে বের হলাম পাশের চায়ের দোকানে। দু ভাঁড় চা নিয়ে চলল কুশল বিনিময় আর নানাজনের খোঁজ খবর। তখনই সে জানালো তার ‘কাক’ নামে একটি গল্পের বই বেরোচ্ছে। একটু আগেই আনন্দবাজার পত্রিকার চিত্রবিভাগের শিল্পী প্রবীর সেনের কাছ থেকে প্রচ্ছদ নিয়ে এসেছে। কাঁধের ঝোলা থেকে প্রচ্ছদটি দেখালো। ওর ভিতর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের আনন্দ টগবগ করছে।
-এখন কোথায় যাবে?
-মণিদার কাছে যাবো। গল্পকার মণি মুখোপাধ্যায়। তুমি চেনো?
-একবার আলাপ হয়েছিল। সি পি আই করেন।
-আমাকে ছেলের মতো ভালবাসেন। উনিই আবার বই ছাপার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। সেদিন আর বেশিক্ষণ ছিল না। আমিও সময় দিতে পারিনি। নতুন চাকরি। সদ্য যোগ দিয়েছি। সহকর্মীদের সকলকে বুঝে উঠতে পারিনি তখনও। বাণিজ্যিক পত্রিকা বা সংবাদপত্রে কাজ করার সময় বেশ সাবধানী হতে হয়। বিশেষ করে প্রথমদিকে। কে যে কখন চোরাগোপ্তা আক্রমণ করবে বোঝা মুশকিল। এই বাজারে হয়তো বেচারার চাকরিটাই চলে যাবে।
অনিল নিজেই বলল, তোমাকে আর আটকাবো না। কলকাতায় এলে দেখা করে যাবো।
সে কথা অনিল খুব একটা যে রাখতে পেরেছিল, এমন নয়। সে নিজেই আসতে পারতো না রেলের চাকরির ভার কাঁধে নিয়ে। আমিও তখন দৈনিক যাত্রী। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা মাসিক টিকিট পকেটে নিয়ে ঘুরি। ফলে অনিলের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় ঘোরা সম্ভব ছিল না।
তবে গেলাম বইমেলায়। তখন কলকাতায় মাথা গোঁজার একটা আস্তানা পেয়েছি। শিয়ালদার সন্নিকটে। তখন বইমেলায় ছাতার নীচে টেবিল নিয়ে বসতো লিটল ম্যাগাজিন। এখানেই ‘অমৃতলোক’ পত্রিকার টেবিলে অনিল বসেছিল। পত্রিকা হাতে তুলে দিল ওর গ্রাম উপন্যাস ‘নুনবাড়ি’। বেরিয়েছিল অমৃতলোক থেকেই। এই উপন্যাস অনিলকে বড় পরিচিত এনে দেয়। এরপরেই ওর একটার পর একটা বইপ্রকাশ হতে লাগল। অনিল বাংলা সাহিত্যে আলোচিত লেখক হয়ে গেল।
বেশ মনে আছে ওর বঙ্কিম পুরষ্কার পাওয়ার সন্ধ্যার কথা। ওই অনুষ্ঠানে ওর বসে থাকা, অভিভাষণে যে কুণ্ঠা দেখেছিলাম, তা আমার অভিজ্ঞতায় ছিল না। পুরষ্কার প্রাপ্তির পরেও প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এসে দুদণ্ড কথা কওয়ার সময় সে শুধু কৃষ্ণনগরের কথাই বলে গেল। তখনই জেনেছিলাম, তার শরীরে শর্করা বাসা বেঁধেছে। জানি না, অনিলের ভিতর অহঙ্কার ছিল কিনা, কারণ তার বহিঃপ্রকাশ কোনওদিন দেখা যায়নি। লেখকের অহঙ্কার থাকবে না, তাতো হয় না। ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তার আচরণে ধরা পড়েনি। একথা বললাম কারণ, অনেক লেখক, এমন কি ঘোষিত বামপন্থী লেখককেও দেখেছি পুরস্কার নেওয়ার আগে বা পরে তাদের মাটিতে পা পড়ে না। অনিল ছিল ব্যাতিক্রমী।
তখন ওর কিডনি বেশ অকেজো হয়ে গেছে। প্রায়ই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। থাকে খড়গপুরে, রেল আবাসনে। অনেক উঁচু পদে সে তখন। বেশিরভাগ সময় নিজের গাড়িতেই যাতায়াত করে। ট্রেনে একজন সঙ্গী পায়। প্রথম শ্রেণির আধিকারিক সে। শারীরিক কারণে স্ত্রী সর্বানী থাকেন সঙ্গে। এমন অবস্থাতেও সে হাজির থাকতো ছোটবড় যে কোনও সাহিত্য অনুষ্ঠানে। সেবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এসেছিল সে। কোন করেছিল, এসো দেখা হবে।
সেদিন ছিলাম দক্ষিণ ২৪ পরগণার একটি গ্রামে একটি সচেতনা শিবিরে। অনিলকে বলেছিলাম তিনটের দিকে যাবো। সরকারি অনুষ্ঠান এড়াতে পারিনি। অর্থপ্রাপ্তির যোগ ছিল। অনুষ্ঠান শেষে সরকারি গাড়িই পৌঁছে দিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায়। দ্বিতলে উঠে দেখি অনিল দাঁড়িয়ে আছে। অনিলকে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা সংবর্ধিত করেছে। কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, সেও বুঝি কবিতা পড়তে ছুটে এসেছে। সে এগিয়ে এলো। হাতধরে বলল, কেমন আছো?
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, চা খাবে?
জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি?
সর্বানী সতর্ক করল অনিলকে, তুমি দুধ-চা খেয়ো না। ফ্লাক্সে লিকার আছে।
বললাম, এদের তো চিনি দিয়ে ফোটানো চা।
অনিল কোনও সময় না নিয়ে উত্তর দিল, আজ তোমার জন্য একটু অনিয়ম করি। কিছু হবে না। সঙ্গে ওষুধ আছে।
সর্বানী খুব সন্তুষ্ট না হলেও নিশ্চুপ রইল। অনিল তৃপ্তিতে পান করল ভাঁড়ে দুধ-চা। দীর্ঘ বরষ স্বাদে। তারপর বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেল হাওড়ার উদ্দেশ্যে।
তারও আগের এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। রবীন্দ্র সদনের চত্বর জুড়ে লিটল ম্যাগাজিন মেলা বসছে তখন। উনিশ শো আটানব্বই কি নিরানব্বই হবে। সেদিন অনিলের গল্প পাঠ ছিল। পৌঁছানোর পর জানতে পারলাম অনিল গল্প পড়ে চলে গেছে। ওই মেলায় আমাদেরও ‘অন্তরীক্ষ’ পত্রিকার ঠাঁয় মিলেছিল। নিজেদের পত্রিকার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। অনেকের সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, দেঁতো হাসি হাসছি। হঠাৎই চোখ পড়ল একটু কোনার দিকে আধো-অন্ধকারে অনিল বসে। বসে আছে স্টলে ঢোকার মুখে কাঠের পাটাতনে। ওকে দেখে এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে অনিলই ডাক দিল, সমরদা।
দুজন মুখোমুখি। -তুমি এখানে?
-আড়ালে থাকাই ভাল। হাসল অনিল। শোন, তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তোমার স্টল থেকে দুটো পত্রিকা দিয়েছে। ওদের সঙ্গে আলাপ হল। থাক, তোমাকে একটা অনুরোধ করছি। আমাকে নিয়ে একটা সংখ্যা করছে এরা। মেদিনীপুর থেকে পত্রিকা বের করে। ভাল কাগজ করে। তুমি একটা লেখা দিও। আমার ঠিকানায় পাঠাবে। সুবীরদাকে বলেছি। তুমি আর সুবীরদা ছাড়া কৃষ্ণনগরে আর তো কেউ নেই এখন আমাকে নিয়ে লেখার।
আরও পরে কৃষ্ণনগর থেকে প্রবীর আচার্য মৌসুমী পত্রিকার একটা সংখ্যা করেছিল অনিলকে নিয়ে। সেই অনিল শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে, হাসপাতালের বিছানায় জীবনের সঙ্গে জীবন শেষের নিদান তুচ্ছ করে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার করতে হাসপাতালে, সেই সময় কয়েকজন সাহিত্যসুহৃদ এগিয়ে এসেছিলেন আর্থিক সাহায্য নিয়ে। বেশ মনে আছে, তখন প্রাত্যাহিক সংবাদ নামে একটা দৈনিক বের হতো। তারই দপ্তরে সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রতন বসু মজুমদার জানালেন, অনিল ঘড়াই হাসপাতালে। আমরা একটা তহবিল তৈরি করছি। আমিও সামান্য কিছু তহবিলে জমা করেছিলাম। ক্ষুদ্রপত্র পত্রিকা সমন্বয় কমিটির আজীবন সম্পাদক অমল করও অর্থ সংগ্রহ করে সর্বানীর হাতে দিয়ে এসেছিল।
ওর বড় ইচ্ছে ছিল অবসরের পর কলকাতা বাসিন্দা হবে। একটা বাসস্থানও খরিদ করেছিল। একটি প্রকাশনীও স্থাপন করেছিল কলেজস্ট্রীট অঞ্চলে। ওর এক আত্মীয়কে দায়িত্ব দিয়েছিল। বলেছিল, আমার বইগুলো দিয়ে শুরু করুক। আমি স্বেচ্ছবসর নিয়ে এসে বসব। তখন তোমাদের কাছাকাছি থাকব।
হলো না। হাসপাতালের শয্যাতেই তাকে বিদায় নিতে হল অপূর্ণতার ঝুলি কাঁধে নিয়ে।
(ক্রমশ)