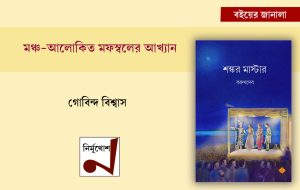উড়নচণ্ডীর পাঁচালি। পর্ব ২১। লিখছেন সমরেন্দ্র মণ্ডল

বৃত্ত থেকে বৃত্তে গমনাগমন
লেখরাজদার দোকান ঘিরে যে বৃত্ত তৈরি হয়েছিল, মাঝে মাঝে সেই বৃত্ত ভেঙে আমরা বেরিয়ে পড়তাম। এক বৃত্তের সঙ্গে অন্যবৃত্ত মিশে যেতো, তার ফলে আমাদের বৃত্তটা যেমন বড় হতো, তেমনই বৃত্ত ভেঙেও যেতো।
বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। যারা এসেছিলেন এখানে, ভারত সরকারের আতিথ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁবুর মধ্যে অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তাদের ছিল ঘরে ফেরার পালা। তার কিছুদিন আগেই উড়নচন্ডী কারামুক্ত হয়েছে। জেলে বসেই শুনেছিল মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি। নকশাল সেলে খবরের কাগজ যেতো। তাতেই চোখ বুলিয়ে জেনেছিল কিছুটা। কারামুক্তির পর জানতে পেরেছিল তাদের একজন নিকট আত্মীয় পরিবার চাপড়ায় তাঁবুতে বাস করেছে। উড়নচন্ডী চলে গেল সেখানে। পড়ে রইল লেখরাজদার দোকানের আড্ডা, সাহিত্য চর্চা। সে তখন বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে।
চাপড়ার মিশনবাড়ির কাছে এক মাঠে বাঁশ আর ত্রিপল দিয়ে মেলার দোকানের মতো ঘর করে দেওয়া হয়েছে। মেঝেতে পাতা খড়, তার উপর মোটা কালো পলিথিন। ওই তৃণশয্যায় শয়ন। প্রাত্যকৃত্যের জন্য রয়েছে হাতের নাগালে থাকা বাঁশ বাগান। ওই বাগানে উড়নচন্ডীদের পৈর্তৃকসূত্রে প্রান্ত দু আড় বাঁশ ছিল। দেখা গেল তার অনেকটাই কাটা হয়ে গেছে সরকারি তাঁবু তৈরির কাজে। গ্রামের যারা মাথা, যাদের দায়িত্ব ছিল তাঁবু তৈরির, তারা নিশ্চয় ওই বাঁশের দাম নিয়ে নিয়েছে। যেমন, কথা ছিল সপ্তাহে একদিন কীটনাশক ছড়াতে হবে। হতো না। অন্তত উড়নচন্ডীর চোখে পড়েনি। সে যাহোক, তবুও তো চলছিল ভালোই। সরকার থেকে প্রথম দিকে কিছু চালডাল দেওয়া হয়েছিল। তারপর তাদের কাছে যা কিছু অর্থ ছিল, তাই দিয়েই চালিয়ে নিতো। ওই তাঁবুর বাইরে উনুন পেতে রান্না করা। বেশির ভাগ সময় ডাল, আলু সিদ্ধ অথবা সামান্য একটা তরকারি। কারো অসুখ হলে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লাইন দিতে হতো। উদ্বাস্তুদের জন্য একটা অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়া হয়েছিল, সেখানেই যেতে হতো।
সময়ে-অসময়ে দু-দশজন একজায়গায় উবু হয়ে বসে বা ঘাসের জাজিমে পাছা পেতে যুদ্ধের খবর চালাচালি করত। ওপার থেকে কখনও কোনও মুক্তিযোদ্ধা এলে তাকে ঘিরে চলত নানান আলাপ।
উড়নচন্ডী গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে খবর জোগার করে নিয়ে এসে ওদের জানাতো। একটা খবর ডিঙিয়ে অন্য খবরে চলে যেতো আলাপ-সালাপ। আর ছিল দিন গোনা। কবে ফিরতে পারবে স্বদেশে। একদিন খবর এলো আকাশবাণী মারফৎ, খান সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। ওপারে বল্লভপুর গ্রামের কাছে আমবাগানে যে মন্ত্রীসভা হয়েছিল, যে এলাকার নাম হয়েছিল মুজিবনগর, সেখানকার মানুষেরা উল্লাস ধ্বনি করল। কেউ কেউ তো হৃদয়পুর সীমান্ত পেরিয়ে ঘুরেও এসেছে সেখান থেকে। স্বাধীন হল বাংলাদেশ। ভারতীয় সৈন্যরা খানসেনাদের গ্রেপ্তার করে পুব পাকিস্তানকে মুক্ত করল। রাজাকার বাহিনীর অনেকেই গ্রেপ্তার হলো। মৌলানা ভাসানির নেতৃত্বে বামপন্থীদের হাতে অনেক রাজাকার নিহত হয়েছিল, আর যারা তখনও রয়ে গিয়েছিল, তারা ভয়ে লুকিয়ে পড়ল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও মুক্তি যোদ্ধারা বহু রাজকার বাহিনীর লোকদের গ্রেপ্তার করে। তখন পশ্চিম বাংলার সীমান্তগুলো ছিল উন্মুক্ত। ইচ্ছে মতো এপার-ওপার করা যেতো। উড়নচন্ডী কয়েকজনের সঙ্গে একবার ঘুরে এলো বাংলাদেশ। সম্পর্ক করে এলো শৈশবের স্মৃতিঘেরা গ্রামের মাটি। তারপর একদিন তো সকলকে চলে যেতে হলো ওপারে। যারা উদ্বাস্তু হয়ে বাস করেছিল এখানে, তারা ফিরে গেল স্বদেশে। চাপড়ার মানুষ, যাদের তারা আত্মীয়র মতো পেয়েছিল, তাদের হাতে হাত মিলিয়ে, বিষণ্ণতায় ফেলে রেখে এগিয়ে গেল। উড়নচন্ডীর আত্মীয়রা, যারা বাস করছিল উদ্বাস্তু ছাউনিতে, তারাও ফিরে যাওয়ার তোড়জোর করল। প্রায় সকলেই গ্রাম থেকে আসার সময় গরুর গাড়িতে এসেছিল। যাওয়ার সময় সেই গাড়িতেই সওয়ার হওয়া গেল। দুটো গাড়ি বোঝাই মালপত্র, অন্য একটা গাড়িতে মহিলা, শিশু আর বৃদ্ধরা। এক গাড়িতে জনা দশ বারো। এপ্রিলের মাঝামাঝি। চৈত্র-বৈশাখের খর রোদ মাথায় নিয়ে সকলে চলেছে স্বাধীনদেশের স্বাদ নিতে। কয়েকজন চলছিল পদব্রজে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে। উড়নচন্ডীও তাদের সঙ্গী। কাঁধের ঝোলায় সামান্য পরিধেয় আর লেখার খাতা-কলম। হাঁটতে হাঁটতে শিকড়ের মাঠ পেরিয়ে হাটখোলা। সেই আদিগন্ত বিস্তৃত শিকরের মাঠ, যা কোন আদিকালে জানাতদের কবলে ছিল।, আজ তার অস্তিত্ব নেই। বেশ কিছু বাংলাদেশী সেখানে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলেছে। তা সেই হাটখোলায় এসে থাকতে হল। এটাই ভারতের শেষ গ্রাম। মাঝে খাল! খালের ওপারে মুনসিপুর। বাংলাদেশের শুরু। খালে জল নেই। গ্রীষ্মের দাবদাহ সব জল প্রায় শুষে নিয়েছে। শিশুদের কোলে-কাঁখে-কাঁধে নিয়ে হাঁটু জল ভেঙে ওপারে ভূমিতে পৌঁছে দেওয়া হল। খালি গরুর গাড়ি চলে গেল হড়হড়িয়ে। মাল বোঝাই গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাওয়া হল। যত ঠেলা হয়, ততই কাদায় আটকে যায় চাকা। দু’হাতে টেনে তুলতে হয় চাকা। শেষ পর্যন্ত সকলে ওপারে পৌঁছে তৃপ্তির শ্বাস ছাড়ল। মুনসিপুর থেকে কাপাসডাঙ্গা প্রায় মাইল চাড়েক পথ। তার বেশিও হতে পারে। গাড়িতে শিশুরা আনন্দে টগবগ করে ফুটছে। এগিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি। উড়নচন্ডীর চোখে বিস্ময়। যে ভেঙে পড়া গ্রাম, খানসেনা আর রাজাকার বাহিনীর অত্যাচারের চিহ্ন দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। কত মাটির বাড়ি ধূলিসাৎ হয়েছে, কত পাকা বাড়ির দরজা-জানালা উধাও। বিকেল নাগাদ পৌঁছানো হল কাপাসডাঙ্গায়। এ আমার দাদুর বাড়ি। শৈশবের স্মৃতি খেলা করতে শুরু করল। সঙ্গে বেদনাও। সেই আটচালা মাটির বাড়ি আর নেই। সমস্ত লুট হয়ে গেছে। ভিটেয় কারা তামাকের চাষ করেছে। ধানের গোলা দুটি আছে একই রকম। আর আছে গোয়াল ঘর। সেও তো বড় কম নয়। ঠিক হল সেই গোয়ালঘরেই থাকা হবে। ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া কালো ত্রিপল দিয়ে সেই গোয়ালকেই থাকার ঘন করে নেওয়া হল। সঙ্গে ছিল খড়। তাই বিছিয়ে দেওয়া হল। তার উপর কালো পলিথিন। এভাবেই থাকা হল ঢালা বিছানায়। শৌচ কর্মের জন্য আছে গোয়ালের পিছনের বাঁশবন, আর তিরতির বয়ে চলা ভৈরব নদী। সে নদীর জল এসে ধাক্কা মারে গ্রামের পৈঠাতে।
উড়নচন্ডী ঘোরে গ্রাম থেকে গ্রামে। দেখে মানুষের উচ্ছ্বাস। একই সঙ্গে একবুক ক্রন্দন, বাসস্থানের হতকুচ্ছিত চেহারা দেখে। কেউ বা বুক চাপড়াচ্ছেন স্বজন হারানোর বেদনায়। এ কমাসে কত কুমারী অথবা বিবাহিত যৌবনা হারিয়ে গেছে, তার গণনা হয়নি। মাটির নীচে বড় বড় বাঙ্কারে চলছে তারই খোঁজ। ভাঙা হচ্ছে বাঙ্কার। গ্রামের মানুষেরা সেই ইট নিয়ে যাচ্ছে ঘর তোলার জন্য। কয়েকদিন ধরে সেই ইট নিয়ে আসা হল।
এরই মধ্যে একদিন ঘুরে আনা হল দর্শনা। গ্রামেই দুজনকে সঙ্গী করে। উড়নচন্ডীতো পথ চেনে না। কোন শৈশবে দর্শনা থেকে কাপাসডাঙ্গায় আসতো গরুর গাড়িতে। সেই স্মৃতি সম্বল করে কি পথ চলা যায়? সব স্মৃতি কি গোছানো থাকে, সেওতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, সেকারণেই দুজন সঙ্গী। সওয়ার হওয়া গেল গরুর গাড়িতে। গ্রামের নাম জানিনে। জিজ্ঞেস করতে করতে যাই। সেই মাথাভাঙা নদী। সে নদী পেরিয়ে আরও কিছু দূরে দর্শনা।
আমার স্মৃতির দর্শনা। এগিয়ে যাই পায়ে পায়ে শিশুকালে ফেলে আসা স্কুলের দিকে। সেই একতলা স্কুল এখন দোতলা। তার দেওয়ালে বুলেটের দাগ। রেহাই পায়নি শিক্ষার অঙ্গন। ফেলে যাওয়া দর্শনা আর নেই। সে এখন পূর্ণ যৌবনা শহুরে। ঘুরে ঘুরে দেখি। কিছু স্মৃতি মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে না। কিছু স্মৃতি বিবর্ণ সেলুলয়েডের মতন। স্কুলের পাশে ছিল এক দিদিমণির টিনে ছাওয়া দরমার ঘর। সেখানে এখন দৈত্যকার বাড়ি। কেরু কোম্পানির শ্রমিক-কর্মচারীদের বাসস্থানগুলো রয়েছে একইরকম। স্মৃতি হাতড়ে শৈশবের সেই বাসস্থানে চোখ বুলিয়ে এলাম। ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের পাতা। বুকের ভিতর দলা পাকিয়ে ঠেলা দিচ্ছে ক্রন্দন। সরে এলাম। না, সবটা পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না তাদের, যাদের ফেলে রেখে গেছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণির বয়সে।
ফিরে এসেছিলাম সেই গরুর গাড়ি চেপে। সেবার পথে বুকের ভিতর থেকে আসল খুলে বেরিয়ে এলেন রবিঠাকুর, ‘আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় আমার মনে’। খোঁজার কোনও অন্ত নেই। মানুষ তো সারাজীবন খুঁজে বেড়ায়, কখনো পায়, কখনো পায় না, আমার মনে যে ছিল গোপনবাসিনী, তাকে কি আমি চিনেছি? তার অবয়ব থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। কিন্তু খোঁজার তো কোনও বিরাম নেই। সারাজীবন খুঁজেও কেউ পায়, কেউ পায় না। তবুও খোঁজ চলে, অবিরাম চলে।
মাতৃভূমির মাটিতে দাঁড়িয়ে শৈশব খুঁজতে গিয়ে দেখি যুদ্ধের পর, বিশেষ করে ভারত থেকে ফিরে আসার পর মানুষের আচরণ, বচনভঙ্গী কেমন বদলে গেছে। মাত্র কয়েক মাসের ভারত যাপন তাদের বদলে দিয়েছে। সেই সরল ঔদার্য হারিয়ে এখন জায়গা করে নিয়েছে গোপন ঈর্ষা। মানুষ আগলে রাখতে চায় তার সব কিছু। সম্ভবত সব হারানোর বেদনা থেকেই এই আত্মস্বার্থপরতা তার শিরায় ঢুকে গেছে।
(ক্রমশ)