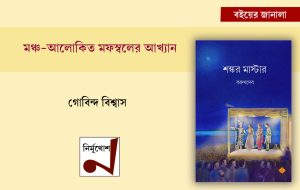ভাটিপুত্র মিহিরের ‘টাঁড় পাহাড়ের পদাবলি’। পড়লেন সুমনা রহমান চৌধুরী।

‘টাঁড় পাহাড়ের পদাবলি’ এক বনভূমির গল্প। ঝাঁটি, ঝাড়, জঙ্গল, খাঁ-খাঁ ভূমি, পাথর নিয়ে বাঙালির পশ্চিম এবং সেখানকার অসম্ভব দরিদ্র মানুষজনের যাপিত জীবনগাথা এই আখ্যানের মূল উপজীব্য। মিহিরের পাঠক জানেন, মিহিরের লেখাকে গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিগদ্য সবই বলা চলে, আবার নাও বলা চলে। বাস্তবিকপক্ষে মিহিরের লেখাকে ‘মিহির-গদ্য’ বলাই বোধহয় সমীচীন। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মিহির কোনো কল্প-কাহিনী লেখেননি, যা দেখেছেন, তাই-ই লিখেছেন, বহিরঙ্গের খণ্ডিত দেখার অন্তর্কথাকে বুঝতে চেয়েছেন নিজের ইতিহাসবোধ, প্রজ্ঞায়। মানুষকে বুঝতে চেয়েছেন, মানুষেের সঙ্গে মিশতে চেয়েছেন অসীম সহমর্মিতায়, ভালোবাসায়।
সত্তরের দশকে দেশজোড়া চাপানো রাষ্ট্রীয় ‘অনুশাসন পর্বে’র দমবন্ধ পরিস্থিতিতে লেখক কীভাবে নাবাল ছেড়ে টাঁড়ে এসে পৌঁছোলেন তার বিবরণ প্রথম পর্বেই মিহির সেনগুপ্ত দিয়েছেন। বড়ো স্পষ্ট এবং সাহসী সে উচ্চারণ। তারপরের আখ্যান বয়ে গেছে বহমান শাখা-প্রশাখাযুক্ত এক নদীর মতো। বহমান প্রবাহিকায় কখনো মাঝে মাঝে তার দিক পরিবর্তন হয়েছে, সেখানে এসে মিশেছে নানান চরিত্র নিজ-নিজ ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি, যাপন আর জীবনবোধ নিয়ে। মিহিরের আখ্যানের বিশেষত্ব হলো, প্রকৃতি বা নিসর্গকে তিনি একটা সীমাবদ্ধ প্রকৃতির রূপ হিসেবে দেখেননি কখনো, মিহিরের আখ্যানের প্রথমকথা মানুষ, শেষকথাও মানুষই এবং সেই মানুষকে আর তার সংস্কৃতিকে নির্মাণ করছে প্রকৃতি।
মিহিরের পাঠক আরও জানেন যে, মিহিরের লেখাকে স্মৃতিগদ্যের পর্যায়ভুক্ত করা হলেও কোথাও ‘আমি-ময়’ হয়ে ওঠে না সে লেখা, লেখক এখানে যেন কেবলই সূত্রধর। সে আখ্যানে এসে মিশে যান কত আজস্র মানুষ তাদের জীবনসংগ্রাম, জীবনবোধ, বিপন্নতা, সংস্কৃতি এবং ভেঙে পড়া সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্ষত হৃদয়ে নিয়ে। তারা কেউই মিহিরের তৈরি চরিত্র নন, ফলে লেখা হয়ে ওঠে সম্মিলিত মানুষের স্মৃতির আখ্যান। একটা সময়ের আখ্যান। ছবি। এটাই মিহির সেনগুপ্তের নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে দিয়েছে। বাংলা ভাষার নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, সৎ, ভনিতাহীন একজন ভাষ্যকার হিসেবে মিহিরের স্থান যে উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকবে, তা নয়, মিহিরের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত উচ্চতা লেখা থাকবে তাঁর মতাদর্শনিষ্ঠতায়, দেশ-কাল-সমাজের যাবতীয় অসঙ্গতির প্রশ্নে তাঁর স্পষ্ট পক্ষাবলম্বনে।
‘টাঁড় পাহাড়ের পদাবলি’তেও পাঠক দেখতে পাবেন এরকমই সম্মিলিত মানুষের স্মৃতির আখ্যান। মিহির ভূমিকাতে বলছেন বটে ‘যেমন ঘটেছে, যেমন দেখেছি, আনুপূর্বিক তারই এক স্মৃতির রোমন্থন এই রচনা’, কিন্তু কোথাও গিয়ে এই পর্যবেক্ষণ, এই সময়ের আলেখ্য শুধু লেখকের থাকছে না, তাতে মিশে যাচ্ছেন চন্দ্রশেখর ত্রিবেদী, শত্রুঘন সরেন, বিক্রম সিং, পৃথ্বীনারায়ণ, হৃষীকেশ চতুর্বেদী, চিন্তাখুড়ো, বিশুবাবু, দিপুবাবু, বুধন, যোগেশ্বর, পাতাবাহার, ফুলবাহার, সিনগি সহ অসংখ্য মানুষের জীবনের, যাপনের আলেখ্য। বিভিন্ন আদিবাসী জাতির সমাজ সংস্কৃতি উৎসব প্রথার আলেখ্য। এবং কোথাও কিন্তু মিহির যিনি কিনা শহর থেকে গিয়ে টাঁড়ে এইসব মানুষদের মাঝে পৌঁছেছেন তাঁর ভাষ্যে আমরা শুনছি না। বরং ত্রিবেদী, শত্রুঘন সহ সেইসব মানুষেরা নিজেদের কথা নিজেরা বয়ান করছেন। যা বাংলা সাহিত্যে অরণ্য আদিবাসী বিষয়ক কোনো গ্রন্থ উপন্যাসে দুর্লভ। বরং সেখানে আমরা দেখেছি শহুরে বাবুদের চোখে অরণ্য জঙ্গলের ‘গরিব ডিংলাপারা মানুষজনের’ বর্ণনা। আর এখানেই মিহিরের ভাষ্যের, চিন্তার এবং মতপথের ম্যাজিক। যা পাঠকের কাছে ভনিতাহীন বিশ্বাসযোগ্য এক আলেখ্য হয়ে উঠে।
আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বইটির ভাষা। টাঁড়ের মানুষের ব্যবহৃত ভাষায়-ই তাঁদের বয়ানে তুলে ধরেছেন মিহির। অনুবাদ করে মান্য বাংলায় রঙচঙে মোড়কে মুড়ে তা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেননি তিনি। ভূমিকাতে এ বিষয়েই মিহির একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন—
প্রতিবেশীর ভাষা বিষয়ে উদাসীনতা আত্মম্ভরিতার জন্ম দেয়। আমার কাছে তা খুবই লজ্জাজনক, আপত্তিকর এবং দূষণীয় বলে বোধ হয়। যাঁদের সাংস্কৃতিক নির্যাস নিয়ে ব্যাপক বাঙালি সংস্কৃতির রসপুষ্টি, সেই শিকড়-সংস্কৃতির ভাষা, আচরণ বা ব্যবহারজগৎ আমরা জানব না, এ অতি ঘৃণ্য মনোভাব। এইসব চিন্তনে রেখেই রচনাটি ফুটনোট-কন্টকিত করলাম না। প্রয়োজনবোধে গানগুলোর অনুবাদে কিছু ভাষাগত স্বাধীনতা নিয়েছি বটে, তবে তা খুবই সন্তর্পণে এবং মূলকে চিন্তায় রেখে। পড়শির ভাষা আদ্যন্ত অনুবাদ করে আরশির জনেদের কাছে বলতে হলে, আমি ‘মাহিঁতে’ অর্থাৎ লজ্জায় মরে যাব।
গোটা বইটিতে আরেকটি বিষয়ও মিহির খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়ে যান। সেটি হলো শ্রেণীর গল্প। রইসদের শ্রেণী। এবং আদিবাসী ও পিছড়ি জাতির ‘কেলেকুলো ডিংলাপারা’র শ্রেণী। রইসদের চোঁয়াঢেকুর আর সেকালের খানাপিনা, সস্তায় আদিবাসী যুবতী সম্ভোগের অসুমার নস্টালজিয়ার কহাবৎ-এর মাঝে ডিংলাপারা শ্রেণীর জীবনাশ্রয়ী এবং আকর্ষক আড্ডার ছবিও তিনি তুলে ধরেন। এবং তা লেখক নন, বরং ত্রিবেদীর মতো চরিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। ত্রিবেদীর ভাষ্য এবং চিন্তা-চিন্তন, প্রগাঢ় জীবনবোধ পাঠকের সামনে এই দুই শ্রেণীর গল্প বলে যায়। দুই শ্রেণীর স্পষ্ট তফাৎও দেখিয়ে যায়।
‘চিন্তাখুড়ো এবং অপারেশন পাগলা গণেশ’ পর্বে মিহির এক মত্ত হাতি শিকারের গল্প বয়ান করেছেন। এবং এই পর্বেই একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি উচ্চারণ করেছেন। তিনি মিহির সেনগুপ্ত বলেই এত স্পষ্ট এবং নির্ভীকভাবে সেকথা উচ্চারণ করতে পেরেছেন। তিনি বলছেন—”বর্তমান ক্ষেত্রে, যে হাতিটাকে শিকার করতে হবে, সেটি আইনত ‘পাগলা’ কিনা, কেন তাকে মারা হল, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের স্বার্থে তাকে অন্য ভাবে সংযত করা যেত কিনা, অথবা যেসব সমাজহিতৈষী, হিতৈষীণীরা আদিবাসী-হরিজনের জীবনের চাইতে এই সব উন্মত্ত পশুদের জীবন সংরক্ষণ অধিক মূল্যবান মনে করেন, সংসদে তাঁদের কূট প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেওয়া সম্ভব হবে,—এমত হাজারো ফ্যাকড়া উপস্থিত হবে। তাই শিকারের সময় যদি কোনো বড়ো পুলিশ সাহেব বা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সঙ্গে থাকেন এবং যদি শিকারের বীরত্ব তথা কৃতিত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা যায়, তবে ঝঞ্ঝাট নেই।” এই অংশটুকু পড়তে পড়তে আমার মনে পড়লো কবছর আগের এক ঘটনা। সম্ভবত চেন্নাই বা তার আশেপাশের কোনো সমুদ্র তটঅঞ্চলে হিংস্র কিছু কুকুর সমুদ্রের আশেপাশে কোনো মানুষ গেলে অথবা অনেকক্ষেত্রে আশেপাশের লোকালয়েও একা মানুষ, শিশুকে দলবেঁধে আক্রমণ করে টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতো। সমুদ্র তটের আশেপাশে যারা বাস অথবা জীবিকা নির্বাহ করেন তারা সবাই ই গরীব মৎসজীবী শ্রেণীর। কয়েকটা এরকম ঘটনা ঘটার পর প্রশাসন থেকে ওই কুকুরগুলোকে গুলি করে মারার নির্দেশ আসে। এবং জানা যায় কোনোভাবে এই কুকুরগুলোর সাথে পাহাড়ি নেকড়ে সংমিশ্রণ ঘটেছিলো যার ফলস্বরূপ নেকড়ে ও কুকুরের মিক্সড ব্রিড এই কুকুরের দলটা। তাই এহেন মাংশাসী হিংস্র। যাইহোক, তখন দেশজোড়া ‘সমাজ হিতৈষী-হিতৈষীণীরা’ কেন ওই কুকুরগুলোকে মারা হবে তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও বিশাল হৈচৈ করেছিলেন। মিহির মনে করিয়ে দিলেন আবারও শুধু অরণ্য অঞ্চলেই নয় অথবা শুধু সত্তরের দশকেই নয়, এ দশকেও সমাজহিতৈষী, হিতৈষীণীরা প্রান্তিক গরীব মানুষের জীবন থেকে এই সব উন্মত্ত পশুদের জীবন সংরক্ষণ অধিক মূল্যবান মনে করেন। তা নিয়ে হৈচৈ করেন। শুধু সংসদে এঁদের কূট প্রশ্নের উত্তর দিতে রায়সাহেবের মতো কোন সাহেবদের নিয়োগ করা হয়েছিলো তা জানা নেই আমার।
এই যে মিহির সেনগুপ্তের স্পষ্ট উচ্চারণ, কারোর কাছে খারাপ-ভালো হওয়ার দায়হীন উচ্চারণ, এটাই মিহিরের বিশেষত্ব। মিহির এই পর্বটিতেই বলছেন কিভাবে চিন্তাখুড়োর বুলেটে গতাসু হাতির উপর সেবাদাসীদের কাঁথার ফুলশয্যা থেকে জবরদস্তি তুলে আনা রায়সাহেবকে বন্দুক হাতে ঠ্যাং তুলিয়ে দাঁড় করিয়ে ফোটো খিঁচা হলো এবং তারপর সেই সাহেবকেই হাতির দাঁত দুটি উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হলো। লেখকের বিস্ময়ের উত্তরে চিন্তাখুড়ো সহাস্যে জবাব দেন—”উট্যা আপনার হাথি শিকার করবার পরমান্ বট্যে আইজ্ঞা।” লেখক যখন ফটো প্রমাণ নয় জানতে চান চিন্তাখুড়ো বলেন,” সেট্যা তো পরমান নয়। সেট্যা আপনাকে ভি দিত্যে পারি। লেকিন, মানুখ মাইনব নাই। বইলবে, বনাওটি। রাজা-লোগোকো ভি অ্যায়সাই তসবির রহা করত। অসলি কাম থোড়িহি করতো ও লোগ, ছোড়িয়ে ও বাত্।” ‘ছোড়িয়ে ও বাত্’-এর মাধ্যমেই চিন্তাখুড়ো কথিত রাজপুরুষদের শিকার গৌরবের অসলি বাত বয়ান করে যান। যুগে যুগে ‘গরীব ডিংলাপারাদের’ শ্রম আর সাহসের ভিতের উপর-ই সাহেব-রাজপুরুষদের গৌরবের কাহিনী রচিত হয়েছে।
গোটা বইটিতে টাঁড় এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের নিখুঁত ছবি এঁকে গেছেন মিহির। সেখানে যেমন এসেছে অরণ্যের সৌন্দর্য, তেমন ভাবে এসেছে সেখানকার ভূমির বৈচিত্র, মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, আচার, অনুষ্ঠান, দুঃখ, সুখ। এসেছে আর্য ও অনার্যের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের বৃহত্তর পটভূমিও। উঠে এসেছে বঞ্চনার ইতিহাস। মিহির বলছেন,’ এখানের বৃক্ষ-বনস্পতির চরিত্র ভিন্ন। তাদের শরীরে ক্লান্তভাব কম। কিন্তু তারাও কি ছায়া দেয় না? দেয়, তবে তফাত আছে। এই তফাতটি প্রকৃতি এবং মানুষের এক নতুন অধ্যায় খুলে দেয় চোখের সামনে। রুক্ষ কঠোর আদিম এই সৌন্দর্য।” সত্যিই তাই। টাঁড় পাহাড়ে পদাবলি বইটি রুক্ষ কঠোর আদিম সৌন্দর্যের এক নতুন অধ্যায় খুলে দেয় পাঠকের সামনে। ভাবতে শেখায়। জানতে ও বুঝতে শেখায় পড়শির আচার অনুষ্ঠান ইতিহাসকে। পড়শির উপর হওয়া নির্যাতন এবং সহিংসতার ইতিহাসকেও। সেইসব ইতিহাস এক শহুরে বাবুর উপর থেকে দেখা কালো মানুষের দুখী ইতিহাস নয়। বরং আদিবাসী কালোমানুষের নিজের মুখের ভাষ্যে নিজেদের যাপন, নির্যাতনের ইতিহাসকে। অতীতের সুখ আনন্দের ইতিহাসও। গোটা বই জুড়ে আছে প্রচুর গান। সেসব গানে গানে যেমন আনন্দ সুখ বয়ান করা আছে, তেমনি আছে দু্ঃখ, নির্যাতনের বয়ান। আছে জীবনবোধের কথা। যার শেষ ছবি সিনগি এঁকে দিয়ে যাবে পাঠকের মনে। তবে সে প্রসঙ্গ পরে। এখনও শহরায় উৎসব বাকি।
কি শহরায় উৎসব? ‘বড়ি মহত্ত্বপূর্ণ’ এক উৎসব। শহরায় উৎসব বোনের ‘নেইহর’ অর্থাৎ নাইঅর আসার উৎসব। ফসলের ঘরে তোলার উৎসব। পশু এবং কৃষিকাজের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশের উৎসব। নাচে গানে মত্ত হওয়ার উৎসব। সব মিলিয়ে শহরায় উৎসব। যে উৎসবে টাঁড়ের সমস্ত মানুষ একসাথে যোগদান করেন। হায় ভাটিপুত্র মিহির— সেই নেইহর উৎসবেও তিনি এনে বাঁধছেন পূর্ববাংলাকে। আনছেন ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়ার কথা। পদ্মাপারের মাঝি, কীর্তনখোলার গুনটানাইয়ার কথা। তাঁর মনে পড়ছে ভাটির দেশের গান—
‘কে যাসরে ভাটির গাঙ্ বাইয়া—
আমার ভাই ধনরে কইও নাইঅর নিতে আইয়া—
তোরা কে যাসরে—কে যাস্?
পড়তে পড়তে মনে হয় আবারো দেশ মানে তো কোনো কাঁটাতারে ঘেরা ভুখন্ড নয়! দেশ মানে তো মানুষ। আর মানুষ জন্মাবধি তার দেশকে বুকের মাঝে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। এ বয়ে বেড়ানোর শেষ বুঝিবা নেই। বরিশাইল্লা এক ব্যাটা যেমন তাঁর দেশকে বুকে করে বয়ে বেড়াতে বেড়াতে টাঁড় অব্দি উপস্থিত হয়েছেন। নেইঅরের সাথে সুতোয় বাঁধছেন নাইওরকে।
শহরায় উৎসবের বিবরণে নাচ গান আনন্দের সাথে উঠে আসছে সমস্ত আদিবাসী ইতিহাস। ভাষা-সংস্কৃতি-রীতি-যাপন সহ অরণ্যের ইতিহাস। শত্রুঘন, যোগেশ্বর, ত্রিবেদীর ভাষ্যে। বিক্রম সিং নামক রাজপুরুষও কখনো আসছেন। ফুলবাহার, পাতাবাহারের উৎসব পালনের আন্তরিকতায় উঠে আসছে কৃষিমাতৃক সভ্যতার প্রতি অরণ্যের আদি আদিবাসীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। আর আসছে গান। গানে গানে জীবনবোধের কথা। গান শেষ হতেই উপস্থিত সবার ‘জোহর জোহর’ জ্ঞাপন।
শহরায় উৎসবের দিনেরই সন্ধ্যার বর্ণনা করছেন মিহির। বড়ো মায়াময় সে উচ্চারণ। শুরুর খানিকটা বলা যাক। মিহিরের ভাষার টানের, দৃশ্য রচনার মহত্ত্ব এখানেই। মিহির বলছেন, “শহরায়ের প্রথম দিনের এখন সায়ংসন্ধ্যা। ঘাসের জাজিমঅলা উঁচু-নীচু জমির আড়ালে সিংবোঙ্গা ডুব মারছেন। মৌসুমি পাখিরা, অর্থাৎ আশেপাশের ঝিল বা হ্রদগুলোতে যে সব হাঁসেরা হিমালয়, এমনকি সাইবেরিয়া থেকে আসে, তারা এখন হ্রদ ছেড়ে সবান্ধবে বিভিন্ন টিলা বা পাহাড়ে নৈশ আশ্রয়ের সন্ধানে উড়ে যাচ্ছে। তাদের পাখার শব্দ এই শীতকালীন আকাশ এবং প্রকৃতিকে নতুন এক চেতনায় যেন জীবন্ত করে। তোপচাঁচির হ্রদের জলের বিস্তার বা গহীনতা খুব কম নয়। এখানে আশ্বিনের শেষ থেকেই শুরু হয় এইসব হাঁসেদের আগমনী। শাল-মহুলের শাখায়, পাতায় তখন তাদের পাখার আওয়াজের রেশ রেশ আগাম অনুভব হয়। তখনই এইসব অরণ্য-উপকন্ঠী বা অরণ্যচর মানুষেরা জানতে পারে, এবং দশজনকে জানিয়েও দেয়, ‘শহরায় আ গৈল। আভি তো মজাহি মজা।’ এই সব হাঁস যেন শহরায়ের বার্তাবহ অগ্রদূত।”
—এই সন্ধ্যার মায়াঘন পরিবেশের মাঝেই শুরু হবে শহরায়ের রাতের উৎসব। অগ্নিকুন্ডের চারধারে নাচ-গানে মত্ত হওয়ার যোগাড়যন্ত। নাচ-গানের আসরে এসে দেখা যাবে ‘বুঢ়াগুলান বড়্যঅ লিশা কইরেছে গ’। আর ছোকরাগুলান চোখা চাহুনি ছুঁইড়েছে ছুকরিগুলান দিকে। আজ যে কী হব্যেক কে জানে!’ এবং এঁদের মতো করে পাঠকেরও মনে মনে বলতে ইচ্ছে হবে— ‘জগমাঝিকে ডাক্ কেন্যে। সে আইস্যে ব্যাপারটো বুঝ্যে লিক।’ এই আসরেই পাঠকের পরিচয় হবে সিনগির সাথে। তার জীবনের দুঃখ আর শূন্যতার সাথে। সিনগির মাধ্যমেই আরেকবার নতুন করে জানা যাবে রাজপুত-ভূমিহর বা অন্যান্য উঁচু জাতের মানুষের সঙ্গে আদিবাসী, পিছড়িবর্গের মানুষদের সংঘর্ষের পরম্পরার কথা। কীভাবে উঁচু জাতের অঙ্গুলিহেলনে, স্বার্থ আর লোভের কাছে বলি হয়ে যায় এক একটা প্রান্তিক মানুষের গোটা জীবন। তাদের হাসি-আনন্দ। কতটা চরম মূল্য দিতে হয় উঁচু জাতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুললে। সিনগির গানের নিঃসঙ্গতা লেখকের সাথে সাথে পাঠকের মনও ভারাক্রান্ত করে তুলবে।
শহরায় উৎসবের রাতব্যাপী উৎসব আর গানের পর পরদিন ভোরে লেখক ফিরে যাবেন নিজস্ব জীবনের গন্ডিতে। সাথে থেকে যাবে সিনগির গাওয়া গানের বোধ—
জনমজখা তেলাং জানাম আকানা।
জেগৎ জেলা রেলাং চাডো আকানা…
যার মান বাংলায় মানেটা মিহিরই বলে দিয়েছেন—
জন্ম নিলাম আমরা দুজন জন্ম পরম্পরায়
ভাসছি মহা সমুদ্দুরে অথৈ জল গড়ায়…
পাহাড়ের উৎরাই দিয়ে নামতে নামতে লেখকের স্বগোক্তির মাঝেই আলেখ্যটি শেষ হয়। শেষটুকু আবার লেখকের ভাষ্যেই বলা যাক—” উৎরাই দিয়ে নামতে নামতে সিনগিকে উদ্দেশ্য করে বলি, তোমার ভুরপা ইপিলকে আমার আদর জানিও। কিন্তু তার মতো আমার তো ওই রকম চমৎকার সব গানের বাণী নেই, তাই একান্ত করে তাকে কিছুই বলে আসতে পারলাম না। কুয়াশা মাখানো উৎরাই ভেঙে বেশ খানিকটা নেমে পিছনে একবার তাকালাম। সারা শরীরে কুয়াশার আস্তরণ নিয়ে সিনগি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে।”
যতবার মিহির সেনগুপ্ত পড়ি অদ্ভুত এক ঘোরে চলে যাই। যেমনটা সিদ্ধিগঞ্জের মোকামের বেলায়ও হয়েছিলো। মাথায় ভর করে থাকেন মিহির। তখন আমার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কুশিয়ারার কাছে গেলে মিহিরের কীর্তিপাশাকে মনে পড়ে। টাঁড় পাহাড়ে পদাবলি পড়ে যেমন কুয়াশায় দাঁড়ালে সিনগির দাঁড়িয়ে থাকা মাথায় ভর করে আসে। বুকের ভেতরের খাঁ-খাঁ শূন্যতায় গোটাজীবনের মতো এসে ভর করে থাকেন মিহির। তাঁর সমস্ত দৃশ্য নিয়ে। কালীগঙ্গার ঘাট, কীর্তিপাশা নদী, তোপচাঁচি, বেলামু পাহাড়ের ঝোরা, মোকছেদ, ছোমেদ, খলিল ঠাহুর, সিনগিকে নিয়ে….।
এই স্মৃতিগদ্যটি, না শুধু স্মৃতিগদ্য তো এ নয়, শরতের আকাশে একটুকরো ভাসমান মেঘের মতো নিস্তরঙ্গ এই দৃশ্যআখ্যান, যা প্রত্যেক পাঠকের জীবনে একবার হলেও অবশ্যই পড়া উচিত।
বইয়ের নাম : টাঁড় পাহাড়ের পদাবলি
লেখক : মিহির সেনগুপ্ত
প্রচ্ছদ : শুভশ্রী দাস
অলংকরণ : পার্থপ্রতিম সরকার, আত্রেয়ী সাহা
মুদ্রিত মূল্য : ৩০০ টাকা
প্রকাশক : সুপ্রকাশ
সুপ্রকাশের পক্ষ থেকে এই বইয়ের অংশবিশেষ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘টাঁড় পাহাড়ের পদাবলি পড়ার ভূমিকা-পুস্তিকা’।
এই লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন বিনামূল্যে, বন্ধুদের সঙ্গেও ভাগ করে নিতে পারেন।