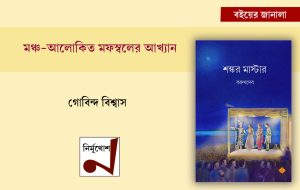দুর্লভ সূত্রধরের ‘আহাম্মকের খুদকুড়ো’। পর্ব ১। পড়লেন অর্দ্ধেন্দুশেখর গোস্বামী

এক
মিহির সেনগুপ্তের সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম যখন সুপ্রকাশ থেকে নবরূপে প্রকাশিত হল, তখন আমি ‘পরবাস’ ওয়েবজিনে বইটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। মিহিরের স্মৃতিগদ্যের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে সেখানে বলেছিলাম যে বাংলাসাহিত্যের স্মৃতিগদ্যের নবকিশোরীর মতো সলজ্জ মেদুর চলনরেখায় মিহিরের গদ্য বাঁধভাঙ্গা জলের মতো তৎসম-চান্দ্রদ্বীপি বাকবন্ধের ঢেউ তুলে এক পৌরুষ গতির সঞ্চার করেছে।আজ দুর্লভ সুত্রধরের আহাম্মকের খুদকুড়ো পড়া শেষ করার পর প্রথম যে কথাটা মাথায় আসছে, সেটা হল, স্মৃতিগদ্যের আরও একটি স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট চলন যুক্ত হল বাংলাসাহিত্যে।
মিহিরের গদ্যের সঙ্গে দুর্লভ সূত্রধরের গদ্যের মিল যৎসামান্য। যেটুকু আছে সেটা কৌতুকপ্রবণতায়। কিন্তু প্রথম জনের উচ্চকিত পরিহাস যেখানে রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙ্গে আলি সাহেবের রঙ্গরসিকতাকে মনে করিয়ে দেয়, দুর্লভের কৌতুকবোধ সেখানে এক স্নিগ্ধ রসসিঞ্চনে তাঁর গদ্যকে সরসতায় ভিজিয়ে রাখে। এই কৌতুকের বেশিটাই নিজের এবং তাঁর নিজকৃত সংজ্ঞালব্ধ আহাম্মকদের প্রতি সস্নেহ বিদ্রুপ-সঞ্জাত।
কে বা কারা আহাম্মক? লেখক তিনটে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন পাঠককে। এক তো খুদকুড়ো জমানোর মস্তকহীন আহাম্মক, যার হাত থেকে কাকেরা জিলিপির ঠোঙা কেড়ে নেয়, লুডো খেলতে গিয়ে যে ছক্কার বদলে কেবলই পুট ফেলে যায়, যে বিড়াল-কুকুরের আঁচড়-কামড় খায়, এমনকি শেয়ালও যাকে শিকার করার তালে থাকে এবং যার কপালে লেমনি স্নিকেটের ব্ল্যাক কমেডির নায়ক হওয়া অবধারিত থাকে। দ্বিতীয় আহাম্মক হল ফ্লবেয়ার সংজ্ঞায়িত ইডিয়ট, ‘দোজ় হু ডিফার উইথ ইউ’; হাওয়া না বুঝেই যে নিজের মত প্রকাশ করে বসে। তিন নম্বর আহাম্মক হল এথেনিয়ান রিপাবলিকের দাস-রূপী লেখকের স্কুলের সাদামাটা ছাত্ররা, যারা চিরকাল মঞ্চের আলোর বাইরে থেকে মঞ্চকে আলোকিত করার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করার ফুর্তিতে ডগমগ হয়ে থাকে।
এই তিন সুত্রের বাইরে আমরা অন্য এক ইডিয়টকেও জানি যার কথা লেখক সরাসরি বলেননি কিন্তু লেখকের ডুমোটোলার দাদু সেটা প্রকারান্তরে বলে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক ঠিক কোন গোত্রের আহাম্মক। এই ইডিয়ট দস্তয়ভস্কির, যে মনশ্চক্ষে দেখতে পায় মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা তার আনন্দ-বেদনার মণিমুক্তামণ্ডিত অবিকৃত হৃদয়টিকে। দাদু বলেছেন, “…তোমার জমানো খুদকুড়োর মধ্যে আছে কত লোকের জীবনের দিনরাত,…কতজনের কত কথার কত শব্দ, দিল কি বাত, কতজনের কত গান…,”। তাই শেষ পর্যন্ত স্নিকেটের ‘ধারাবাহিক দুর্ভাগ্যমালা’ না হয়ে আহাম্মকের স্মৃতির সেইসব খুদকুড়োই সময়ের এপারে এসে অন্য এক গল্প-কাহিনি হয়ে উঠেছে।
এসব নাকি নেহাতই অনাবশ্যক কথা আর এই অনাবশ্যক কথা দিয়েই দুর্লভ তাঁর এই স্মৃতিগ্রন্থের সূচনা করেছেন। তবে পাঠকের মনে হতে পারে সূচনার অনাবশ্যক কথা দিয়ে তিনি সমগ্রের সুরটি বেঁধে দিলেন। পাঠকমনকে তিনি এক সরস অথচ ব্যঞ্জনাময় স্মৃতিগল্প পাঠের জন্য প্রস্তুত করে তুললেন।
দুই
শিয়ালে খাওয়া কুলে পোকার সোনার নাগরা দর্শন
যাকে শিয়ালে খায় তার ‘কুলে পোকা’ হতে বাধ্য এবং সোনার নাগরা দর্শনও তার অবধারিত। এ-সবই আহাম্মকের সাধারণ লক্ষণ।
শিয়াল প্রসঙ্গে আমার ছোটবেলার কথা মনে এসে যায়। আমি একদা অজ গাঁয়ের এক হাঁ-করা বালক ছিলাম। এই হাঁ করে থাকা অতি সন্দেহজনক লক্ষণ এবং সর্বদা যার মুখ হাঁ হয়ে থাকে তাকেও যে আহাম্মক আখ্যা দেওয়া যায়, সেটা দুর্লভ সূত্রধর প্রকারান্তরে একটু পরেই বলে দেবেন।
তো আমাদের বাড়িতে হাঁস পোষার চল ছিল। গোয়ালের এক পাশে হাঁসের খোঁয়াড়। সেই খোঁয়াড়ে নদী-বাঁধের লকগেটের মতো কাঠের পাতলা তক্তার দরজা ছিল। উপরের দিকে আটকানো দুটি বাঁশের ফাঁক দিয়ে দরজাটিকে নামিয়ে দিলেই খোঁয়াড় বন্ধ। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই খোঁয়াড়ের ভেতরে প্রবল প্যাঁকপ্যাঁক। কেউ একজন ছুটে এসে দরজাটিকে টেনে উপরে তুলে দিতেন। অমনি তারা খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে লাইন দিয়ে খিড়কির পুকুরের দিকে হেলেদুলে চলতে শুরু করত। মরাল-গমনের মাঝে মাঝে কেউ কেউ আবার দুই ডানা মেলে দ্রুতগামী হয়ে আগেভাগে পুকুরের জলে ঝাঁপ মারত। আবার দিনের আলো নিভে গেলেই পুকুর ও তার আনাচকানাচ থেকে সব হাঁস খোঁয়াড়ে ঢুকে যেত। একজন কেউ গুনতির দায়িত্বে থাকতেন। গুনতিতে কম পড়লেই শিয়ালে খাওয়া নিয়ে হইচই হত। বর্ষা-হেমন্তে ঝোপঝাড়ের বাড়বাড়ন্ত, মাঠও ভর্তি বেড়ে ওঠা ধানগাছে। সেই দুর্ভেদ্য ক্ষেত্রে শিয়ালের খোঁজে কুকুরের পাল সহ দুরন্ত বালকবাহিনীও সুবিধে করত পারত না। হাঁসেদের মধ্যেও আহাম্মক থাকে, তারা আবার গেঁড়ি-গুগলি বা ধানের কচি দানার লোভে ধানভরা মাঠে ঢুকে পড়ে এবং শিয়াল ‘স্পেশালিষ্ট’ ডুমাটোলার দাদুর ভাষায় শিয়াল তাদের ‘বড়ি সাফাইসে’ তুলে নিয়ে চলে যায়। কখনও কখনও এমনকি, রাতের বেলায় রহস্যজনকভাবে খোঁয়াড়ের গেট আলগা করে দু-একটাকে নিয়ে বহুত বড়ি সাফাইসে ভেগে যায়।
হাঁস নিয়ে এত কথা কেন? কেননা হাঁস না থাকলে শিয়াল আসবে না। এবং শিয়াল নিয়ে চর্চা না হলে এমন কোনো বালকের কথা মাথায় আসার সম্ভাবনা নেই যাকে কিনা শিয়ালে খেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইতি টানার আগে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, আমার গ্রামের এমন কোনো বালকের কথা আমার মাথায় এল না, যে শিয়ালের শিকার হয়েছিল।
অতএব শিয়ালে খাওয়া বালক বিখ্যাত হতে বাধ্য। এমন অদ্ভুতকর্মা বালককে দেখতে জনে জনে ছুটে আসবে বা তাকে দেখলেই মনে পড়বে এই সেই বালক যাহাকে শৃগালে খাইয়াছিল – এ তো বলাই বাহুল্য।
ডুমোটোলার দাদু বলেছিলেন, “শেয়ালের কামড় ইত্না খরাব নেহি”।
দুঃখের বিষয় তিনি যতটা পণ্ডিত ও দার্শনিক, ততটা রসিক বোধহয় ছিলেন না। তাই তিনি বালকের বিখ্যাত হওয়ার গৌরবকে গুরুত্ব না দিয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শেয়ালের কামড়কে শংসাপত্র দিয়েছিলেন।
ইস্কুলে যাওয়া না-যাওয়ার ‘কান্না বিষয়ে মনীষী-বাক্য’ জানে না বলে সেই বিখ্যাত বালকের ইস্কুল যাওয়ার বায়না করে কান্না জুড়তে কোনো সমস্যা হল না। অতএব বালককে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু প্রথম দিনেই হাঁ করে(যা বলেছিলাম)দরজার দিকে তাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মাস্টারমশাই তার মাথায় টোকা দিয়ে জীবনের জটিলতম প্রশ্নটি করে বসলেন, “মন থাকে কোথায়?”
লেখকের কৌতুকবোধ নিমেষেই কীভাবে গভীর নান্দনিকতার সঙ্গে মিলেমিশে এগিয়ে যেতে পারে পাঠক এখানে তার ছোট্ট একটু নমুনা পেয়ে যাবেন। এরপরই বালকের ‘কুলে পোকা’ জনিত কান্না বা পরবর্তী সময়ে সোনার নাগরা জুতোর ছাইদানিতে বদলে যাওয়ার আজব কাণ্ড ইত্যাদি বৃত্তান্ত বিশদ করলে বইটি পড়ার টাটকা আনন্দলাভ থেকে পাঠককে অনেকটাই বঞ্চিত করা হবে। এই পর্বে লেখকের হিউমার-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। বাকি যেসব অবান্তর প্রসঙ্গ এল সেসব তাঁর লেখার ধরনকে অনুকরণ করার চেষ্টা মাত্র। পাঠক নিজের চোখে খুদকুড়ো চেখে দেখলে তবেই তার প্রকৃত আস্বাদ পাবেন।
তিন
অন্নপূর্ণা মা ও দয়াবতী দিদিরা
এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্র ছাড়াও দু-দুটি অধ্যায় আলোকিত করে বিরাজ করছেন অন্নপূর্ণা মা এবং দয়াবতী দিদিরা।
ক্ষুধার সংসারে “জীবনের সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো দু-বেলা দু-থালা ভাতের গল্প—”, “শুধু মা বোঝেন সন্তানের খিদের দামামা— সন্তানও বোঝে ‘মা’ নামের মহিমা”।
এই ভাতের গল্পটাকে মন্ত্রবলে যিনি জীবন্ত রাখেন, ‘বুদ্ধি, শ্রম আর কল্পনাশক্তির অসামান্য মিশ্রণ’ দিয়ে যিনি অখাদ্যকে সুখাদ্যে পরিণত করতে পারেন তিনিই হলেন মা অন্নপূর্ণা। কেবল স্বামী সন্তান নয়, অতিথি অভ্যাগতদের জন্যও তার ভাঁড়ার অফুরন্ত থাকে। এই অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যে যেমন মান্যগণ্য বিশিষ্ট মানুষজন থাকেন, তেমনিই থাকেন কাসুন্দ-বিক্রেতা এবং শাকওলি মাসিরাও। অন্নপূর্ণা মায়ের সংসারে ফেলনা এবং খুদকুড়ো সহযোগে জলখাবারের এমনই সমারোহ যে পুরো একটি উপাদেয় অধ্যায় লেখক রেখে দিয়েছেন পাঠকদের পাতে সেগুলি পরিবেশন করার জন্য।
আগ্রাসী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার মূল স্তম্ভ যদি মা হন, তাহলে মায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর কন্যাদের হতেই হয় তাঁর যোগ্য সহকারী। এই কন্যারা হলেন দুর্লভ সূত্রধরের দয়াবতী দিদিরা। ভাইদের ‘অনাচার’-এ রাখা তাঁরা সইতে পারেন না। হরেক রকমের আচার তৈরি, শুকোনো এবং ‘দুর্বৃত্ত’-দের হাত থেকে রক্ষা করাই তাদের সবচেয়ে বড়ো ব্রত। কোন সুভদ্রদের রসনা বারোমাস রসস্থ রাখতে কোন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে তাঁদেরকে আচার রক্ষা করে রাখতে হয় সে এক অন্য বৃত্তান্ত, পাঠক বইটির ভেতরে ঢুকলে তবে টের পাবেন।
দিদিদের দয়াবতী অভিধা পাওয়ার আরও একটি নিগূঢ় কারণ আছে। মায়ের সুশৃঙ্খল সংসারে ছোটো ভাইদেরও ভাগেও পড়ত চালের কাঁকর বাছার দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব দিদিদের ‘পকিয়ে পাকিয়ে’ তাদের ঘাড়ে যদি চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাদের তুল্য দয়াবতী আর কে আছে এই কর্মময় সংসারে!
অন্নপূর্ণা মায়ের দুয়ারে অভ্যাগতদের মধ্যে এক উজ্জ্বল চরিত্র বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক কাসন্দ বিক্রেতা। পরিচ্ছন্নতার প্রতীক সেই বৃদ্ধের সঙ্গে মায়ের মুল্যের বিনিময়ে কাসন্দ বেচাকেনা আসলেই ছিল আরও মহার্ঘ সব বিনিময়ের নান্দীমুখ মাত্র। পণ্য বেচাকেনা সাঙ্গ হলে বৃদ্ধের প্রথম প্রস্থ বিনিময় হতো ছোটোদের সঙ্গে। তিন-চারটি প্রসারিত ডান হাতে কাসন্দ মাখা আমসির টুকরো একটি একটি করে তুলে দেওয়ার আগে তাঁর অবধারিত প্রশ্নটি ছিল— ‘হাত-টাত পয়ঃপোষ্কার তো?’
অন্যদিকে কী উত্তর আসবে জেনেও ছোটোদের অবধারিত প্রতিপ্রশ্ন ছিল—‘এমন কাসন্দ কে বানিয়ে দিল গো?’
—‘আমার মা গো। আমার মা ছাড়া এ পৃথিমীতে আর কেউ কি এমন কাসন্ বানাতে পারে গো!’
যে নিজেই এতো বুড়ো তাঁর মা কতো বুড়ো— এই নিয়ে ছোটোরা যতই চিন্তিত হয়ে পড়ুক, পাঠকের নিশ্চয় জানা আছে যে মা ‘অনন্তকাল ধরে তাঁর সন্তানদের জন্য অতুলনীয় কাসন্দ বানিয়ে চলেছেন।’
সময় অনন্ত জানেন বলেই সেই কাসন্দ বিক্রেতার প্রশান্ত চরিত্রে কোনো অস্থিরতা নেই। এরপরেই শুরু হবে অন্নপূর্ণা মায়ের সঙ্গে তাঁর আসল বিনিময় পর্ব। তিনি মাকে শোনাবেন পুরাণকথা, রান্নার গল্প এবং বিনিময়ে মায়ের মুখে অতি অবশ্যই শুনবেন একটি রবীন্দ্র-কবিতা।
অন্নপূর্ণা মা এবং দয়াবতী দিদিদের পাশাপাশি একের পর এক অনুপম চরিত্র আঁকতে আঁকতে একটি স্রোতোধারার মতো এগিয়ে চলেছে দুর্লভ সূত্রধরের স্মৃতি-আখ্যান। সেখানে হাজির কচুরিওলা বেণী ঘোষের সঙ্গে সাফাইওলা বিজুরিয়া, কিংবা ডালপুরি সহ নবীনবাবু এবং জিলিপি নিয়ে ভুবনবাবু। সবশেষে হাজির মায়ের সবচেয়ে কাছের মানুষ, তাঁর সখিপ্রতিম শাকওলি মাসিরা। তারা নিজের অধিকারে মাকে ‘দিদি’ বলে ডেকে আতিথ্য নিয়ে যেত। বদলে, দিয়েও যেত অনেক কিছুই। সেসব অকিঞ্চিৎকর বস্তুর গায়ে লেগে থাকত অন্তরের ছোঁয়া।
মায়ের ধম্মোকম্মো, ব্রত উদযাপন নিহিত থাকত সংসারকে এইভাবে বিস্তৃত করার মধ্যেই। মন্বন্তরের রক্তচক্ষুকে হয়তো এই পুণ্যফলেই উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন তিনি।
“এখন সম্পর্কের সময় কম, সুখ দুঃখ বিনিময়ের অবকাশ নেই। এখন নদী-মাঠ-ডোবায় কলমি শাকের ফুলগুলো হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে মাসিদের ডাকে না, গরমকালের দুপুরে আকাশনিম গাছে ঝুপ্পুর পাতার আড়ালে বসে হা-ক্লান্ত খয়রাপাখ পাপিয়া আর গরমের ছুটিটাকে ভরিয়ে দিতে আসে না। পাখিগুলো এখনও টিকে আছে কী-না তারই বা ঠিক কি, গরমের ছুটির মতো সেগুলোও হয়তো বা বিলুপ্ত হয়েছে! পুরনোকালের সেই কষ্টের বোধটাই তো আজ উধাও।”
আহাম্মক “দুঃখু-দুঃখু মুখ করে ভাবে— মায়েদের অনন্ত পরমায়ু পাওয়া দরকার—”
এইভাবেই স্মৃতিগদ্যের চলনে বাঁকে বাঁকে বদল আসে, ভাষা তরল থেকে অনুভবের ব্যঞ্জনায় গাঢ় হয়, আর তারই মাঝে আহাম্মকের নিজস্ব দর্শন উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।
(ক্রমশ)