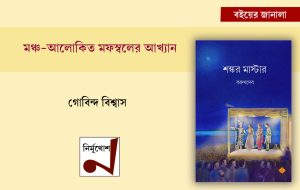পুনর্ভবাপুত্র। অষ্টম পর্ব। লিখছেন আহমেদ খান হীরক

বছর শেষের মাস
বছর শেষের মাস, মানে ডিসেম্বর, ডিসেম্বরের ভোরগুলো ছিল কেমই অদ্ভুতুরে, একেবারে ধোঁয়া ওঠা।
আকাশ থেকে কুয়াশা নেমে এমনভাবে সব কিছুকে জড়িয়ে থাকত, যেন মাখনের প্রলেপ, আমরা সেদিকে চোখ রেখে বুঝতে পারতাম না, আকাশ থেকেই কিছু নেমে এসেছে কিনা, নাকি মাটির বস্তুগুলোই তাদের সকালের আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজেদের বিভা।
আমাদের আনন্দ হত স্কুল ছুটি হয়ে যেত বলে। ডিসেম্বর — ছুটির মাস। বছর শেষ। পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন এদিকে ওদিকে বেড়াতে যাওয়া। মুক্তির আনন্দও বলা যায়। সঙ্গে জানুয়ারির নতুন দিন… নতুন বই… এইসব বহন করতাম ছোট্ট মাথাতে। আর ছিলে আম্মার হাতের ‘ধুপি’।
তা ‘ধুপি’ শব্দটার সাথে নিশ্চয়ই আপনাদের পরিচয় নেই? এই ধুপি আমার এতটাই প্রিয় ছিল যে, পরবর্তীতে, একটু বড় হওয়ার পর, আমি রীতিমতো ধুপি উৎসব করেছি। অনেক পরে, যখন আপনাদের কাছাকাছি জ্ঞান আমার হয়, তখন জেনেছি একে বলে ভাপাপিঠা। কিন্তু বাজারে পাওয়া ভাপাপিঠা আর আমার আম্মার হাতের ধুপির মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। স্বাদের, এমনকি আকারেরও।
আম্মা ধুপি বানাতেন বড় একটা বাটির মাপে। আর তার ভেতর থাকত খেজুরের গুড়। কখনও কখনও ফালি ফালি করে কাটা নারিকেলও। আমরা চুলার পাশে, আগুনের উত্তাপ নিতে নিতে, শূন্য থালা নিয়ে বসে থাকতাম। আর আম্মা একটা একটা করে ধুপি উঠিয়ে সাথে সাথে রাখতেন আমাদের প্লেটে। ধুপি থেকে ধোঁয়া উঠত, সেই ধোঁয়া–আমরা যেগুলোকে বলতাম ভাপ — আমরা অতি আগ্রহের সাথে চোখে-মুখে মাখিয়ে নিতাম। আর হাসতাম। মিঠা ধুপির আনন্দে সে হাসি। আর আমাদের ডিসেম্বরগুলো সত্যি সত্যি ধোঁয়া-ওঠা হয়ে যেত।
এসময় বাজারে যেতে বড় মজা ছিল। অবশ্য কিছুটা বড় হয়ে ওঠার পর বাজারের প্রতি আর কোনও আকর্ষণ অনুভব করিনি। কিন্তু বাবার হাত ধরে, বাবার ঘোলাটে চাদরের ভেতর নিজেকে অর্ধেক মতো ঢুকিয়ে, মাছের খলুই নিয়ে, তা দোলাতে দোলাতে, বাজার করতে যাওয়ার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ ছিল, ছিল রোমাঞ্চও। আনন্দ, কারণ দেখো আমি বাবার সাথে যাচ্ছি বাজারে — অর্থাৎ আমি বড় হয়ে গেছি। রোমাঞ্চ, কারণ বাবা প্রথমেই ঢুকবেন মাছবাজারে। আর সেখানে চোখ জুড়ানোর জন্য অপেক্ষা করছে এই বড় বড় মুখ হা করা বোয়াল মাছ। তাদের ঠোঁটের ওপরে চিনাম্যানদের মতো লম্বাটে গোঁফ। তাদের গোঁফ নাড়তে নাড়তে আমি ভাবি আমারও একদিন দাড়িগোঁফ তো হবে। তখন এত বড় বড় গোঁফ আমিও রাখব। আর পাশের হাঁড়িতে জিয়ানো শিং ও মাগুর। কিছুক্ষণ পর পর খলবল করে ওঠে। আমার শিঙে খুব ভয়। আরও ছোট অবস্থায় তার কাঁটা আমাকে হজম করতে হয়েছিল। সেই বেদনা এখনও টের পাই তর্জনীর মাথায়।
আর কী রঙিন সবজি বাজার! বাঁধাকপি — আমরা বলতাম পাতকপি — আর ফুলকপিতে ভরা। ফুলকপি আমার দেখতে, ছুঁতে এবং খেতে ভালো লাগত। মনে হত আস্ত একটা ফুল। আর ফুলই তো, কী আশ্চর্য! হোক না যতই সবজি! অদ্ভুত তার বিন্যাস। অদ্ভুত তার হাসিমুখে ছড়িয়ে থাকা। বাবা বেছে বেছে ব্যাগভর্তি করে ফুলকপি কিনলে আমার মুখে ফুলকপির মতোই উদ্ভাসিত হাসি ছড়িয়ে পড়ত। সঙ্গে কাঁচাপাকা টমাটো, শিম, পালং শাক। খলুইয়ে আমাদের মাছ ভরা থাকত। আর চটের ব্যাগটা ভরে উঠত এইসব সবজিতে।
শীতকালে আরেকটা জিনিস ছিল কেনার… শীতের পাখি। অতিথি পাখি।
শীতের পাখি তো আসত নানান কিসিমের। আমাদের প্রিয় ছিল সামকেল আর বতক পাখি। বতক মানে হাঁস, এইটা এই ফাঁকে বলে রাখি। শীতকালে শীতের দেশ থেকে একটু উষ্ণতার খোঁজে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে আমাদের আশে-পাশের নদী-নালা খাল-বিলে যে অতিথি পাখিগুলো আসত তাদের দেখতে যেমন নয়ন জুড়াত, খেতেও কিন্তু ছিল অদ্ভুত স্বাদ। আপনারা নিশ্চয়ই এখন ভ্রূ কুঁচকাচ্ছেন? কিন্তু শুধু বাজারে গিয়ে না, হামেশায় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হতেন পাখিবিক্রেতারা। তাদের বড় বড় খলুই ভর্তি থাকত ছোট বড় নানান সাইজের পাখি। বাবা খুবই আগ্রহের সাথে পাখি কিনতেন। আমাদেরও আগ্রহের কমতি ছিল না।
শুধু যে পাখি বিক্রেতা এই ডিসেম্বরে এসে হাজির হতেন তা তো নয়। বাড়িতে এসে হাজির হতেন রস বিক্রেতারাও। খেজুর রস। মেঘলা দিন থাকলে, কুয়াশামোড়া দিন থাকলে সেই রস কখনওই আহামরি হত না। কিন্তু ঝলমলে রোদ্রের দিনে সেই রস হত মধুর চেয়েও মিষ্টি। আমি তো গ্লাসের পর গ্লাস খতম করে দিতাম। আম্মা বলত, এত খাস না। পেট খারাপ করবে! আমি পেট খারাপের থোড়াই কেয়ার করতাম। প্রথমে দুই তিন গ্লাস এমনি এমনি, পরে আবার বাটিতে নিয়ে মুড়ির সাথে মিশিয়ে। মিষ্টি কিন্তু শীতল সে রস খেতে খেতে শীত আরও তীব্রতা পেত ভেতরে ভেতরে — উত্তরের হাওয়া এসে আমাদের কাঁপিয়ে দিয়ে যেত ঠিকই, কিন্তু আমরা ছাদের কোণার এক চিলতে রোদের ওপর ভর করে, আর পেঁচিয়ে পরানো চাদর জড়িয়ে বাটি বাটি রস শেষ করে ফেলতাম।
তা প্রাকৃতিক এই সব মধু ছাড়াও আরও কিছু আসত ডিসেম্বরে। আরও কিছু আয়োজন, আরও কিছু প্রস্তুতি। বিজয় দিবস আর ক্রিসমাস। ক্রিসমাসকে তখন ক্রিসমাস বলতে তো শিখিনি। বলছি শুধু বড়দিন। আর এই বড়দিনে কী কী হয় তাও আমরা সঠিক জানি না। শুধু একটা ধারণা থাকে যে, কেউ কেউ বলে, ঈশা নবীকে নিয়ে কোনও ঘটনা। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগত ঈশা নবীকে নিয়ে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা আমরা কেন পালন করছি না। কেন অন্যরা করছে? কিন্তু এই প্রশ্ন বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। বড়দিন এলেই আমরা ছুটে যেতাম বেশ ক’ মাইল। ওখানে একটা বড় গির্জা আছে। আর গির্জাটা কি গম্ভীর। সাঁওতাল পল্লীর সাথে লাগোয়া এই গির্জাকে ঘিরে বড়দিনে বসত মেলা। মেলা, তা যেমনই হোক না কেন, আমাদের কাছে ছিল আকর্ষণীয়। আমরা মেলার বাঁশি কিনতাম। মাটির কত জিনিস থাকত… সেগুলো কিনতাম। আর ঘুরে ঘুরে দেখতাম এত বড় গির্জাটাকে কীভাবে সাজিয়েছে ওরা। গির্জার মাথায় যে বিশাল ঘণ্টাটা ছিল সেটা আমাদের মতো ছোটদের আগ্রহের মূল কেন্দ্রে থাকত অবশ্য। আমরা ঘণ্টাটা নিয়ে নানা রকম ধারণা করতাম। ধারণায় কত যে অদ্ভুত জিনিস উঠে আসত। বলতাম, অনেক বড় একটা পাখি একদিন ঠোঁটে করে উড়তে উড়তে সাঁই সাঁই করে এসে ওই চূড়ায় ঘণ্টাটা বসিয়ে দিয়েছে! কিংবা বলতাম এই ঘণ্টাটা ছিল একটা পাহাড়ের গুহার ভেতর। আগে কেউ তা দেখেনি, কিন্তু এই চার্চের ফাদার একদিন তা দেখতে পেয়ে অনেক বড় একটা গরুর গাড়িতে করে ঘণ্টাটা নিয়ে এসেছে! দুটোই হতে পারে… আমরা কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিই না।
কিন্তু আমরা যখন আমাদের বন্ধুর কাছে যাই, যার নাম র্যাফল আর যাকে আমরা রাইফেল বলে ডাকতাম, সে আমাদের অনেক মুড়ি-মুড়কি খেতে দিয়ে বলে, ঘণ্টাটা আসলে রাজমিস্ত্রিরা বানিয়েছে… তখন আমরা খুবই হতাশ হই। রাজমিস্ত্রি আমাদের পরিচিত ব্যাপার। তারাই যদি এই জিনিস বানাতে পারে তাহলে আর কোনও মজা থাকে না। কিন্তু আমরা মজা পেয়ে যাই অন্য জায়গায়। চার্চের পাশে ছোট্ট একটা পুকুর। আর সে পুকুরে দেখছি ভাসছে অনেকগুলো প্রদীপ। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে… প্রদীপগুলো মাছের চোখের মতন জ্বলছে। কে জ্বালাল প্রদীপগুলো? রাইফেল বলে, এখানে তো হিন্দুরাও আসে। তারাও পুজো দেয়। বড়দিনের দিন তো সবার আনন্দ, সবার মজা! আমরা প্রদীপগুলো ধরতে চাই, কিন্তু সেগুলো মাঝ পুকুরে চলে গেছে। এই শীতের মধ্যে কষ্ট করে নেমে প্রদীপগুলো আনার কথা আমরা শুধু কল্পনাতেই ভাবি। আর এরই মধ্যে চার্চের দরজা থেকে ওড়ানো হয় ঢাউস একটা জ্বলন্ত বেলুন। আমরা ছুটে যাই সেদিকে। বেলুনটা উড়তে উড়তে, ওপরে যেতে যেতে, আমাদের মনে হয় চাঁদে চলে যাবে। আমরা বেলুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বড়দিনের কথা ভাবি। ঈশা নবীর কথা ভাবি। আর অন্যদিকে তখন বাজি ফুটতে শুরু করে। ডিসেম্বর আমাদের আনন্দে ফুরায়।
কিন্তু এই বড়দিনের আগেই তো চলে আসে ১৬ ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাস এলেই বাবা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলত। তখন অনেককে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হাসাহাসি করতেও দেখেছি। আবার বলত, আগেই তো দিন ভালো ছিল… এখন গদিতে বাঙালিরা বইসা সব লুটপাট কইরা খাইতেছে!
বাবা অবশ্য এমন বলতেন না। তবে বাবার বোধহয় একটা অনুশোচনা ছিল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সন্তান-সন্ততি নিয়ে তিনি বর্ডার পার হয়ে চলে গিয়েছিলেন ইন্ডিয়ায়। সেখানে মানবেতর রিফুজি জীবন-যাপন করতেন। বুভুক্ষু অবস্থায় দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং পাকিস্তানী সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। কয়েক দিন তাঁকে ক্যাম্পে কাটাতে হয়। সেটা নিশ্চয় সুখের হয়নি। কিন্তু বাবা এ সম্পর্কে আর কিছুই বলেন না। শুধু বলেন যে একদিন শুনতে পেলেন দেশ স্বাধীন হয়েছে। জয় বাংলার ধ্বনি চারিদিক থেকে আসতে শুরু করে। বাবা তাঁর বিছানার তোষকের নিচে লুকানো ফ্ল্যাগটা নিয়ে পতপত করে ওড়াতে থাকেন। সেই পতাকা বিবর্ণ হয়ে তখনও আমাদের বাড়িতে উড়ত। অ্যান্টেনার পাশে একটা বাঁশের মাথায় আমরা সেই পতাকা ১৬ ডিসেম্বরের অনেক সকালেই বেঁধে দিতাম। আর জবাগাছ থেকে ছেঁড়া ফুলসহ গাঁদা, রজনীগন্ধা নিয়ে সকাল সকালই চলে যেতাম শহীদ মিনারে। অবশ্য আমাদের এমনিতেই যেতে হত। স্কুল থেকে। ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম পরে কুয়াশামাখানো মাঠে আমাদের পিটি-প্যারেড চলত।
দল, আরামে দাঁড়াবে আরামে দাঁড়া…
দল, সোজা হবে সোজা হ…
দল, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে সালাম জানাবে সালাম জানা…
আমরা একসাথে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে সালাম জানাতাম। এই পতাকা আমাদের বাড়ির পতাকাটার মতো বিবর্ণ না। উজ্জ্বল। সবুজ আর লাল। পূবের মাথায় তখন সূর্য চিকচিক করতে শুরু করেছে। আমাদের চোখে পতাকা আর সূর্য মিলেমিশে যেত। আমরা সালাম জানাতে জানাতে দেখতাম ডিসেম্বরের কুয়াশার মাঝেও আমাদের পতাকাটা চকচক করছে।
আমাদের বুক ভরে আসত।
(ক্রমশ)