আমার মিহির। সন্ধ্যা রায় সেনগুপ্ত। মিহির সেনগুপ্ত-স্মরণে ‘সিদ্ধিগঞ্জের ভাটিকুমার’।

প্রাককথনঃ বৈদেহী সেনগুপ্ত (মিহির সেনগুপ্তর কন্যা)
ব্যক্তিগত আলেখ্য ইতিহাস বহন করে একথা তো জানাই ছিল। সে কথা আরো একবার টের পাই বাবার অসুস্থতার সময়। একদিন দুপুরে মা-এর সাথে কথা বলতে বলতে বলেছিলাম, ‘তুমি কেন লেখনা মা তোমাদের দুজনের কথা? সে তো শুধু তোমাদের নিজেদের নয়। যে সময় তোমরা দেখেছো একসাথে, আলাদাভাবে, যাদের ও দেশে রেখে এসেছিলে আর যাদের সাথে করে নিয়ে আসতে পেরেছিল- তাদের সবার দেখার মধ্যে দিয়ে – এ সবই তো জরুরি কথা। এ সবই তো সেই সব যাপনের খুঁটিনাটি আর তা পার হয়ে আসার ইতিহাস কে আগলে রাখে।’
এর মাঝে একদিন ভোর রাতে উঠে মা লিখতে বসেছিল। ঘটনার অভিঘাত সামলে উঠে লেখার কাজে মন দিতে আরো অনেক সময় লেগে যাবে জানা সত্বেও আমাকে জানিয়েছিল, ‘আজকে একটুখানি লিখেছি। আমি লিখব। যে ঝড়ের সময় পার করেছি, তার অনেক কথাই বলা জরুরি।’ এখানে মায়ের খাতা থেকে সেই কয়েক লাইন তুলে দিলাম। আশা রাখি এই কাজে মা দ্রুত হাত দেবার মতো মানসিক সুস্থিতি খুঁজে পাবে—
মনে আছে কবে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল?
১৯৫৯ সাল। ৩রা জানুয়ারি। ২ জানুয়ারি আমাদের নতুন বছরের, অর্থাৎ ক্লাস নাইনের ক্লাস শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমি সেদিন অনুপস্থিত ছিলাম। আমার ছোড়দি, অঞ্জলি, যে আমার সহপাঠী, স্কুলে গিয়েছিল। ছুটির পর বাড়িতে এসেই আমাকে স্কুলের খবর জানিয়েছিল– ‘একটা ছ্যামরা নতুন ভর্তি হইছে – খুউব ফডর ফডর করে।’ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আর? আর কী করে? ঠিক আছে। কাইল তো ইস্কুলে যামু, তহন দেখমু।’ এরকমই মনে মনে ভেবে নিলাম।
পরদিন স্কুলে গিয়ে দেখলাম আরো তিন চার জন ছাত্র আমাদের স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে।
আমরা মাস্টারমশাইদের সঙ্গেই ক্লাসে ঢুকতাম। আবার ক্লাস শেষ হলে মাস্টারমশাইদের সঙ্গেই ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসতাম। টিচার্স রুমে একটা সাইডে আমাদের বসার জন্য বেঞ্চ থাকতো।
আমাদের প্রথম ক্লাস নিতেন অশ্বিনীবাবু। উনি ক্লাসে ঢুকতেন কথা বলতে বলতে। উনি যা বলবেন সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করে খাতা নিয়ে দিতে গেছি, অমনি তুমি আমাকে প্রায় টপকে স্যারের কাছে খাতা দিতে গেছ। স্যার কিন্তু হাত বাড়িয়ে আমার খাতাটা আগেই নিয়েছিলেন। তোমার কি রাগ সেদিন! রেগেমেগে বলেই ফেলেছিলে, ‘এরকম পক্ষপাতিত্ব মানবো না।’ স্যার তোমাকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু সেই থেকেই শুরু হয়েছিল তোমার সঙ্গে রেষারেষি। অঙ্ক ক্লাসে সবসময়ই আমি আগে অঙ্ক কষে ফেলতাম। তোমার রাগ ছিল সেইজন্যও…
……………………………………………………………………..
সন্ধ্যা রায় সেনগুপ্তর স্মৃতিগ্রন্থ ‘একদা একাত্তর’ থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধার করা হলো–
আমাদের বিয়ে
১৯৭২ সালের ৬ মার্চ আমার সামাজিক তথা শাস্ত্রানুগ বিয়ে হয়। এই বিয়েতে বরিশালের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। নিখিলদা, আব্বাসভাই, সতু মেসোমশাই (রুচিরার মালিক সতু সেন), আরও অনেকজন উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা থেকে সুকুমারদা, আমার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে দু-একজন আত্মীয় এসেছিলেন। বিয়েতে গণ্ডগোলের একটা আশঙ্কা করে আগে থাকতেই সতর্ক ছিলেন বাবা। ফকু ভাই ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। ফকু ভাই, মালেক ভাই সেই সময়টা সতর্ক না থাকলে ব্যাপক ঝামেলা হতো।
আমাদের বিয়েতে প্রথাসম্মত নিয়মকানুনের বাইরেও অনেক নিয়ম পালিত হয়েছে। আমার মা এবং লতিকা কুঞ্জের মাসিমা (বন্দনার মা) দুজনে প্রাণভরে তাঁদের জানা সব রকম স্ত্রী-আচার পালন করেছেন। তাছাড়া আমার জ্যেঠশ্বশুর, হিরণ্যকুমার সেনমশাই এবং আমার বাবা সুশীলকুমার রায়মশাই তাঁদের সামন্ত পরম্পরার রীতি মেনে সমস্ত আচার-আচরণ পালন করিয়েছেন। অনেক কষ্টে পালকিতে চাপাটা বন্ধ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু স্ত্রী আচার বন্ধ হয়নি। সব কিছুই মেনে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে। মিহিরকে ও আমাকে সারাদিনই না খেয়ে থাকতে হয়েছে। প্রথা অনুযায়ী বিয়ের পর দিন না হলে তার পরদিন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার নিয়ম মেয়েদের। কিন্তু কিন্তু কিছু কিছু ব্যবস্থাপনার অসুবিধা থাকায় আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হয়েছিল চতুর্থদিনে। যাওয়া হয়েছিল সন্ধ্যাবেলার পরিবর্তে সকালবেলায়। নতুন গজিয়ে ওঠা একদল মুক্তিযোদ্ধা (আদৌ কিনা সন্দেহ) এই পরিবর্তনের কারণ। যা হোক, যাত্রার সময় আসন্ন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় বাঙালি মায়েদের চিরকালীন কান্না সবাইকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। হঠাৎ আমার সেজভাই কমল মা-র গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, ‘মা, তুমিও তো একদিন এমন করেই তোমার মাকে ছেড়ে এসেছ, এখন, তুমি আর তোমার পিছনের কথা মনেও করতে চাও না’। এই চিরন্তন সত্যি কথাটা কমল (তখন তার বয়স দশ বছর) এমনভাবে বলল যে সবার মনের বিষণ্ণতা প্রায় নিমেষেই কেটে গেল।
নৌকার পথ। রুণসী-তারপাশা-কেওড়া। আমরা কীর্তিপাশার খাল পেরিয়ে কেওড়ার খালে পড়লাম। নৌকা খুব ধীর গতিতে যাচ্ছিল। খালে জলের পরিমাণ খুবই কম। মাঝি লগি বেয়ে বেয়ে এগোচ্ছিল। অবশেষে কেওড়া জমিদার বাড়ির ঘাটে এসে নৌকা লাগলো। কিন্তু পাড় খুবই উঁচু। জল খালের একেবারে তলায়। কীভাবে পাড়ে উঠব, সেটাই চিন্তা। বধূবরণের এয়োস্ত্রীরা পাড়ে উপস্থিত। মিহির এবং মিহিরের বোন কৃষ্ণা ঘাটে দণ্ডায়মান গ্রামের ছেলেদের সাহায্যে পাড়ে উঠে গেল। কিন্তু আমি উঠব কীভাবে? হঠাৎ করে ফটিকদাদু (মিহিরদের বাড়ির পূর্বতন চাকর) আমাকে পাঁজাকোলে করে পাড়ে উঠে এল। বলল, ‘দেখ, তোমার শাশুড়িকে এভাবেই পাড়ে তোলা হয়েছিল। তোমার শাশুড়ি, মানে আমাগো সোনা খুড়িমাও এভাবেই আইচিলেন ঘাট থিকা। তার পর তুমি বৌমা আইলা।’ নানা আচার আচরণ পালনের পর আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে বউ হিসেবে প্রবেশ করলাম। মুক্তিবাহিনীর লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়ে একবার এখানে এসেছিলাম। জ্যাঠামশাই তা জানতেন না। একটু পরে জ্যাঠামশাই ও জেঠিমা আমাকে একটা বড়ো ঘরে নিয়ে গেলেন। সেই ঘরের দেওয়ালে কয়েকটা বড়ো বড়ো অয়েল পেন্টিং। জ্যাঠামশাই একটা ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন– ইনি জগৎচন্দ্র সেন। আমাদের এই জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ। ইনি চন্দ্রমোহন সেন, জগৎচন্দ্র সেন মশাইয়ের অগ্রজ। এই রকম আরও কয়েকটি ছবি আমাকে দেখাচ্ছিলেন। জেঠিমা চোখের নানাবিধ সমস্যায় একটু কম দেখতেন। তিনি আমার হাত ধরে এগোচ্ছিলেন। এই সব পর্ব মিটে যাবার পর যখন পরিবর্তন করতে এলাম, তখন দেখি আমার আঙুলের আংটি, যেটি দিয়ে আমাকে সিঁদুর পরানো হয়েছিল– সেটি আঙুলে নেই। আমি কৃষ্ণাকে একথা জানালে কৃষ্ণা একথা অন্য কাউকে জানাতে বারণ করল। জানালে নানা লোক নানা কথা বলবে। গ্রামীণ সমাজে একটা ভুল বার্তা যাবে। কৃষ্ণা ছাড়া মিহিরকেও একথা জানিয়েছিলাম। আর কাউকেই কিছু জানালাম না। সন্ধ্যাবেলায়ই আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। গ্রামে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা তখন ছিল না। দোতলার যে ঘরটিতে অর্থাৎ দক্ষিণের বড়ো কোঠায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই ঘরে বই ঠাসা। সবই প্রায় আধপোড়া। পাক মিলিটারি আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সব বই পোড়েনি। সেই পোড়া বই একপাশে সরিয়ে আমাদের জন্য বিছানা করা হয়েছিল। সেই বইয়ের পাহাড়ে আমরা যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য– নানা ধরনের বই। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি। মিহির আক্ষেপ করছিল, বলেছিল– ‘আমাদের পুরুষানুক্রমে সংগৃহীত বই। ছাই হয়ে গেছে প্রায়। টাকা পয়সা গেলে কোনো না কোনোদিন হয়তো তা সংগ্রহ করতে পারতাম। কিন্তু এই অমূল্য সংগ্রহ কি আর পাব!’
পরদিন ভোরে উঠে নীচে চলে এসে দেখি গ্রামের বেশ কয়েকজন বয়স্ক ভদ্রলোক জ্যেঠামশাইয়ের কাছে বসে আছেন। আমি যথারীতি মাথায় ঘোমটা দিয়ে তাঁদের সামনে এলে জ্যেঠামশাই তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বললেন, ‘এই আমার বউমা। দেখছেন কেমন ঘোমটা দিয়ে আপনাদের সামনে এসেছে। ঘোমটা অবশ্য আজকাল আউট অফ এটিকেট। যদিও এটিকেট স্পেলিংটা অনেকেই জানে না’। জ্যেঠামশাই এভাবেই কথা বলতেন, প্রতিটা উচ্চারণে দাম্ভিকতা– যেন সামন্ত পরম্পরার ইঙ্গিত বহন করে। শ্বশুরবাড়িতে আসার আগে আমার মা আমাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন জ্যেঠামাসাইয়ের বিষয়ে। মা বলেছিলেন, ‘উনি অত্যন্ত মান্য ব্যক্তি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। আমার আচার-আচরণে উনি কোনোভাবেই যেন অসন্তুষ্ট না হন।’ কৃষ্ণাও এ বিষয়ে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। আমার ভাগ্য ভালো। জ্যেঠামশাই আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে স্নেহচ্ছায়া দিয়েছেন।
এ বাড়িতে আসার তৃতীয় দিনে আমার বউভাত। জ্যেঠামশাই বলতেন পাকস্পর্শ। সেই সময়ে অর্থাৎ এই রকম একটা বিধ্বংসী যুদ্ধের পর গ্রামে রাঁধুনি বামুন একেবারেই পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিক নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অনেক। জ্যেঠিমা নিজে করতে পারছেন না। তার উপর জ্যেঠিমার চোখের দৃষ্টি তখন প্রায় ক্ষীণ। জ্যেঠামশাই বললেন, বউমাকেই রান্না করতে হবে। এতবড় বাড়ির বউ, তাকে তো এটা করতে হবে। জেঠিমা আপত্তি করলে তিনি বললেন, বউমা পাকের ঘরে চেয়ারে বসে থাকবে। চাকর ফটিক আর তার স্ত্রী বউমার নির্দেশমতো যা করার করবে। এরকমভাবেই আমার বইভাত পর্ব সমাধা হলো। আমার বাপের বাড়ি থেকে আসা দিদিরা, ভাইবোনেরা এবং অন্যান্যরা দেখে তো অবাক। আমার বাবা গর্বের হাসি হাসছেন। গ্রামের যাঁরা নিমন্ত্রিত ছিলেন, তাঁরা আমার জ্যেঠশ্বশুরমশাই এবং আমার বাবার খুবই প্রশংসা করছিলেন। ‘এই হলো গিয়ে বড়োবাড়ির ব্যাপার। বড়কর্তা কেমন ব্যবস্থা করলেন, দ্যাখলা তোমরা?’ এই প্রসঙ্গে একটা হাসির কথা না বলে পারছি না। মিহিরের ধাত্রী মা ধোপা ঝি, এবং আমার ধাত্রী মা ধোপা বউ সম্পর্কে বেয়ান। রঙ্গরসিকতার সম্পর্ক তাদের। হঠাৎ আমাদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। ধাপা বউ চিৎকার করে বলতে লাগল যে, তাদের মেয়ে একেবারে জাহাজের ল্যাহান। এইরকম মেয়ে এই বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, এ বাড়ির ভাগ্য। ধোপা ঝি আরও সুর চড়িয়ে বলতে লাগলো যে, তাদের ছেলের মতো ভালো ছেলে আর হয় না। রুণসীর সুশীল রায়মশাই ধন্য হয়ে গেছে এই বাড়িতে মেয়ে দিয়ে। অনেক কষ্টে তাদের থামানো গেছে।
কিন্তু গ্রামের যে-সব বউ নিমন্ত্রণে এসেছিল, তাদের কৌতূহল অপরিসীম। আমার বাবা কী কী দিয়েছেন, বড়বাবুই বা আশীর্বাদী কী দিয়েছেন.. ইত্যাদি। গ্রামীণ সমাজের তথাকথিত মূল্যবোধের এ-ও অঙ্গ। এই ভাবেই শ্বশুরবাড়িতে দিনটা আমার কেটে গেল। পরদিন আমার বাপের বাড়ি ফেরার পালা।
শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আসা অর্থাৎ এই দ্বিরাগমন পর্বে আবার নানারকম আচার-আচরণ। জ্য়েঠামসাই পুনঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই নিয়ম যাতে পালিত হয়, তার তদারকি করছিলেন। জেঠিমা আমি চলে আসব, তাই মন খারাপ করছিলেন। বলছিলেন, অনেক কাল পরে বাড়িতে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হলো। বাড়িটাকে বাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। আবার তো সব অন্ধকার।
আবার সেই খালের ঘাট থেকে নৌকোয় উঠতে হবে। জোয়ার ভাটার টানাপোড়েনে খালে জলের পরিমাণ তলানিতে। অনেকের সঙ্গে পাড়ের রাস্তাটা পার হচ্ছিলাম। যেতে হবে সেই জায়গাটায়, যেখান থেকে ফটিকদাদু পাঁজাকোলা করে আমাকে তুলে এনেছিল। হঠাৎ মনে হলো আমার আঙুলের আংটি সম্ভবত এখানেই পড়ে গিয়েছিল। নীচের দিকে তাকিয়ে আংটিটাকে দেখলাম মেঠো রাস্তার ফাটলে আটকে। পেয়েছি বলে চিৎকার করে আংটিটাকে তুলে নিলাম। আশ্চর্য!পাঁচদিন আগে এখানে আংটিটা পড়ে গিয়েছিল। পাঁচদিন পরে ফিরে পেলাম। আমার সঙ্গে যে সমস্ত বউ-ঝিরা আমাকে তুলে দিতে এসেছিল, তারা ছুটে গিয়ে জ্যেঠামশাইকে খবর দিল। তিনি তো আংটি হারানোর খবরটাই জানতেন না। খুব খুশি হলেন জ্যাঠামশাই। সবার কাছে বলতে লাগলেন, বউমা খুবই সুলক্ষণা।






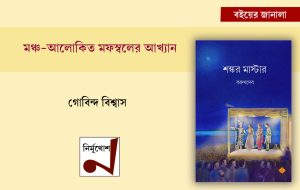

যা চেয়েছিলাম খুব প্রাণ ভরে। তা ছাপার অক্ষরে দেখে মনটা ভরে গেল. 🙏🏻
বৌদি, পুরো জীবনটা লিখুন। পুরো জীবনটাই পাঠ করেত চাই।