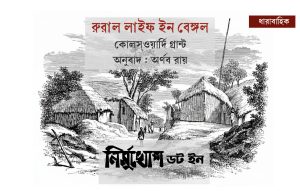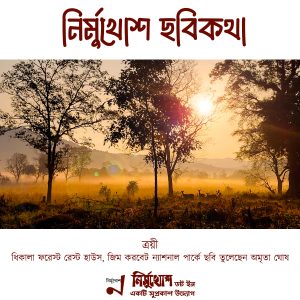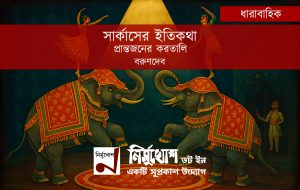অক্ষর-চরিত্র ও জ্ঞাপন-বাণিজ্য : এক অন্তহীন এপিটাফ। পর্ব ৫। অনন্ত জানা

আক্ষরিক পথযাত্রা
এই হলো শুরু।
দিন-কয় পরে গোপাল বাড়ুজ্যের পরামর্শে সুমন তিনু পোদ্দারের সঙ্গে দেখা করে এলেন।
হাজার হলেও তাঁর কথার সূত্রেই সুমন সুধালাভ করেছিলেন।
আসলে এই গঞ্জে লালাদের যাপনের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। তিনু পোদ্দার তো শুধু তিনু পোদ্দার নন তিনি বাবু লালার নাতি! যে বাবু লালা একার উদ্যোগে স্থানীয় চণ্ডীমাতার মন্দির চত্বর ঘিরে একটা সাপ্তাহিক হাট বসিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। এখানকার চণ্ডীমাতা গার্লস স্কুলটা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডীমাতার মন্দিরের বিশাল চণ্ডীমণ্ডপটিও তাঁরই অর্থানুকূল্যে নির্মিত। সুতরাং এই গঞ্জে পোদ্দার পরিবারের প্রভাব অপ্রতিহত।
রাধাকৃষ্ণ টেলার্সের নামলিপির সংবাদ তিনু পোদ্দারের কানে গিয়েছিল।
তিনি এক বিকেলে গোপাল বাড়ুজ্যের দোকানের সাইনবোর্ড দেখে গেলেন। সুমন গঞ্জে আপাতত থাকতে এসেছেন শুনে তিনু পোদ্দার অনেক সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

তিনু পোদ্দারের দোকানে এতকাল মজুত ও মূল্য তালিকা ছোটো ব্ল্যাকবোর্ড আর শ্লেটে চক দিয়ে লিখেই চলে গেছে, এবার তিনু পোদ্দার সুমনকে দিয়ে হালকা মেরুণের ওপর ডার্ক মেরুণের জমিতে সাদা রঙ দিয়ে খোপ-কাটা দুটো বোর্ড (আজকের মজুত তালিকা ও আজকের মূল্য তালিকা) করিয়ে নিলেন। কাঠের লম্বা পাটার চারপাশে বাদল মুন্সির হাতে সরু ওভাল-টপ বাটামের বর্ডার একেবারে হিট করে গেল।
এই অভিজ্ঞতা থেকে পরে এম আর ডিলার বা অখিল মণ্ডলের রেশন দোকানের প্রাইস আর স্টক-বোর্ড বানাবার সময় তাঁরা এমন বর্ডারের জন্য সূর্যি লেটের ফটো-বাঁধাইয়ের দোকান থেকে ফ্রেমের রেডিমেড ডিজাইনড্ বাটাম আনিয়ে নিলেন।
এবার সাহা সু হাউজ, মা তারা বস্ত্রালয় থেকে শুরু করে কালীমাতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার পর্যন্ত সকলেই সাইনবোর্ড লেখাতে শুরু করে দিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই গঞ্জ-বাজারের, দোকানপাটের চেহারা অনেকটা বদলে গেল। এমন-কী রেল লাইনের পুবপারে বিস্তীর্ণ মাঠটার শেষে ধোঁয়া ধোঁয়া যে ছোট্ট খুদ্দক টিলাটা দেখা যায়, তার কাছের ইতস্তত পাথরের টুকরো-ছড়ানো মাঠটায় জানুয়ারির কড়া-শীতে যে পীরবাবার মেলা বসে তার বিজ্ঞাপনের জন্য মেলার মুরুব্বিরা দশটা কাপড়ের ব্যানার তৈরি করে নিয়ে গেলেন। বাড়ির নেমপ্লেট, ইস্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাইদের নামের তালিকা-সম্বলিত অনার-বোর্ড, রাজ্য সড়কে বাস স্টপেজের কাছে সারি সারি হোটেলের সাইনবোর্ড থেকে মেনুবোর্ড, লেটার বক্স―এমন অজস্র অর্ডার আসতে লাগলো।
এসব কাজে সাহায্যকারী একমাত্র কাঠ মিস্ত্রী বাদল মুন্সি।
লোকটা নিতান্তই অন্যরকমের। সারাদিন যেমন-তেমন, কিন্তু রাত্রে গোপাল বাড়ুজ্যের দোকান বন্ধ হবার পর কী হবে তা বলা মুস্কিল―রেলবাজারের পশ্চিম বাগে লালু বাগারের ঠেকের কোণে―মাঠপাড়ার ঝুপসি ভাঁটিতে― কিংবা সালাম মিয়ার চালকলের পিছনের পাঁচিলের লাগোয়া মস্তিখানা―কোথা থেকে তার বউ মাঝরাত্রে তাকে কুড়িয়ে আনবে অথবা কোনদিন রাত্রি আটটাতেই বাড়ি ফিরে চাড্ডি গরম ভাতের জন্য বাড়ি মাথায় তুলবে―তা কেউ জানে না, সেখানে একেবার ‘নট গ্যারান্টি পাকা রসিদ!’
বাদল মুন্সি জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক।
সাইনবোর্ডের নানা কিসিমের ফ্রেম বানাতে দিয়ে সুমন দেখলেন―কাঠের কাজে বাদল মুন্সি একটা প্রতিভা। যে-কোনো কাঠের পুরু টুকরো, তক্তা, ছোটো পাটা বা বাটামকে সবচেয়ে কম কেটে-ফেড়ে, সবচেয়ে কম চেঁছে, সবচেয়ে কম ঘষে বাদলের মতো অমন প্রার্থিত আকার দিতে আর কেউ পারবে বলে মনে হলো না। তার চোখের আন্দাজ ও হাতের মাপও মারাত্মক!

গোপাল বাড়ুজ্যের দোকানে নিয়মিত আড্ডা মারা ছাড়া বাদলের জীবনের বাকি সবই নিতান্ত অনিয়মিত। এই গঞ্জের সবচেয়ে বড়ো কাঠের গোলা এবং ফার্নিচারের দোকান ‘অধিকারী ফার্নিচার’-এ তার কাজের খুব কদর। কিন্তু সেখানে বাদল বাঁধা মাইনের কাজে কখনই ঘাড় পাতেনি। অধিকারীরা তো ছোটোখাটো―সদরের ফর্নিচারওয়ালারা ডবল মাইনে কবুল করেও বাঁধা কাজে তাকে আটকাতে পারেনি। কাটো, ঘষো, বিঁদ করো পেরেক ঠোকো, স্ক্রু ঘোরাও, কিংবা বড়োজোর ফুল-লতা-পাতা হরিণ-ময়ূর-মাছের নক্সা কাটো, খাটের কুৎসিতদর্শন পায়ায় করো হাতির মাথা! ইচ্ছা না-থাকলেও লোকের প্রচলিত ফরমাশের পেছনে দিনের-পর-দিন লেগে থাকা বাদলের পছন্দ নয় বলেই সে কোথাও স্থায়ী হয়নি।
গোপাল বাড়ুজ্যে বলেন―‘আরে বাপু, আমাদের বাদলা কি মিস্ত্রী বা কারিগর নাকি! বাদলা একটা আস্ত শিল্পী! শিল্পীরা তো একটু-আধটু ‘ই’-মতো হবেই!’
সুধা বলল―‘হ্যাঁ, শিল্পীরা একটু-আধটু ‘ই’-মতো যে হবে তা তোমারে দেখলেই মালুম হয়। তুমিও তো কিছুতেই দোকানের কাজে মন দিবা না!’
―‘আরে ভাই, এর চেয়ে বেশি মন দিলে গঞ্জের সব লোক এই রাধাকিষ্ট টেলার্সেই এসে ভিড় জমাবে, আর গঞ্জের তামাম ওস্তাগরেরা না খেতে পেয়ে মরবে যে!’
সুমন এমন বিবেচনার কথা ইহাজীবনের শুনতে পাবেন তা কখনও ভাবেননি।
বাদল মুন্সি সাইন বা অন্যান্য বোর্ডের ফ্রেমের কাজে কী শিল্পের সন্ধান পেয়েছিল তা সে-ই জানে। সে প্রত্যেকদিন নিয়ম করে সুমনের দেওয়া সমস্ত কাজ করে চলেছিল। সুমন প্রথম থেকেই তাঁর লেখার আকার-প্রকার ছাঁদ-ধরন বদল করে চলছিলেন।
গোপাল বাড়ুজ্যের রাধাকৃষ্ণ টেলার্সের বোর্ডটার আয়তনের তুলনায় অক্ষরগুলো ছোটো হয়েছিল―ছোটোত্ব উপেক্ষা করলেও বোর্ডে ম্যাটারের বা ক্যারেকটারের সংখ্যা অনুযায়ী অক্ষরগুলো আরও-একটু বড়ো হতেই পারতো। এই অভিজ্ঞতায় মা তারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের বোর্ডটা বানালেন চওড়ায় বড়ো একেবারে দোকানঘরের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত মেপে একেবারে সমান সমান, আর উচ্চতায় দু-ফুট মাত্র। দুপাশে এক-ফুট করে জায়গা ছেড়ে পুরো বোর্ড জুড়ে দোকানের নাম লেখা হলো। দু-পাশের জায়গায় দোকান মালিক নেত্য ময়রার দাবি অনুযায়ী দোকানে প্রস্তুত সেরা সেরা মিষ্টির নাম―রসগোল্লা, ল্যাংচা, মিহিদানা, গোলাপসুন্দরী, পক্কান্ন ইত্যাদি। এই সাইনবোর্ড নেত্য ময়রার এত পছন্দ হয়ে গেল যে, তিনি সুমন, বাদল মুন্সি, বাদল মুন্সির জোগানদার চ্যালা লক্কা নিমাইকে পর্যন্ত পেটভরে রসগোল্লা ও স্পেশাল গোলাপসুন্দরী খাইয়েই ছাড়লেন!

সুমন রাধাকৃষ্ণ টেলার্স লেখার কাজ শুরু করেছিলেন প্রাচীন বাংলা লিপির কিংবা বলা যায় কিছুটা মৈথিলি লিপির ধাঁচ অনুসরণ করে, কিন্তু তিনু পোদ্দারের মজুত ও মূল্য তালিকার ছোট্ট ওয়ালবোর্ড দুটি করার সময় ছোটো হরফ নির্মাণে তিনি একেবারে প্রচলিত সাধারণ বাংলা অক্ষরে উত্তীর্ণ হলেন।
মা বলতেন―‘জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।’ সেকথা সারা জীবন মেনে চলেছেন। এই গঞ্জে থাকার সময় পীরবাবার মেলা থেকে কেনা কাঠের দুটি হাতা ও খুন্তি তিনি কলকাতা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নারকেলের নাড়ুর ছাই বানাবার সময়, আম, কুল বা তেঁতুলের আচার বানাবার সময়, ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা কাসন্দ ঘঁুটবার সময় মা কাঠের হাতা-খুন্তি ব্যবহার করতেন। কলকাতায় গিয়ে আর সেগুলো কাজে লাগেনি। উত্তর কলকাতার পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা ভাড়াবাড়িতে রোদ ছিল না। তবু মা সেগুলোকে ফেলে দেননি। বলতেন―‘তুই কলকাতা থেকে দূরে, কোনো গ্রামে থাকবি কেমন! সেখানে তোকে নাড়ু, তিলতক্তি, গুড়-বাদাম, আমের আচার বানিয়ে দেবো। আমি আর তোর বাবা তো তোর সঙ্গেই থাকব। তোর বউকে সব শিখিয়ে দিয়ে যাব।’

কিন্তু বাবা মারা যাবার পর সব বদলে গেল। বউদিরা মায়ের জমানো সাংসারিক জিনিসপত্রকে বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখত। বাবার নিষ্ক্রমণে মা একেবারে ভেঙে গিয়েছিলেন, নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের জমিয়ে তোলা সংসারের সবকিছু বিসর্জিত হলো, শুধু মায়ের জমানো টাকা-পয়সা, বড়ো আর মেজো ছেলের বউদের দেওয়ার পর ছোটোবউকে দেওয়ার জন্য মায়ের বাকি গয়না-গাঁটি―সবকিছু নিজেদের বাড়ি কেনার সময় দাদা-বউদিদের হস্তগত হলো। মায়ের অনুরোধ বা জেদেও নতুন বাড়ির মালিকানায় ছোটোভাইয়ের কোনো অধিকার রইলো না। অবশ্য তার দরকারও ছিল না―কেননা অনিন্দিতা বউদিদের আগেই সুমনের অপদার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল।
―‘জীবন বানানোটা এক অসম্ভব শিল্প―সবাই তা পারে না!’―বলেছিল অনিন্দিতা। নিজে তা করেও দেখিয়েছিল।
তখন এম এন সি কথাটার সদ্য আমদানি হয়েছে। বেতনের প্যাকেজ ব্যবস্থা, পার্শ্বশিক্ষক, চুক্তিিভত্তিক কর্মচারী নিয়োগ তখন সদ্য দেখা দিয়েছে। গ্লোবাল-পাবলিক-ওয়ার্ল্ড-মডেল-অ্যাকাডেমি-সেন্ট যোসেফ-সেন্ট বিশপ-বিদেশি পুষ্প নামাঙ্কিত স্কুলের সারি―সংখ্যাহীন বিদ্যালয়ের পাশে ঢালাও মদ্যালয়ের তখন সূচনা হচ্ছে, অগণন প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয় সবে মেলছে তার অর্থাঙ্কনির্ভর জয়ধ্বজা। তবু তখনও বায়ুশূন্য তীব্র ভরবেগের মতো পাঁচ-দশ-বারো-বাইশ হাজার টাকার অনিশ্চয়তা, কাজের ঘন্টার সীমাহীনতা আর এককোটির প্যাকেজ উচ্চ-নিচের বেতালা মাতলামির তখনও শুরু হয়নি―তখনই অনিন্দিতা নির্ভুল বুঝেছিল জীবন বানানোর শিল্প ইহজীবনে সুমনের আয়ত্তাধীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং…
আর্ট কলেজে অনিন্দিতা ওয়াশের কাজ করতে পছন্দ করত। খুব সার্থকভাবে সে নিজের জীবন থেকে সুমন নামের রঙটুকুকে মুছে ফেলেছিল, ―রঙ তো নয়ই, রঙের দাগও এতটুকু অবশিষ্ট ছিল না, যার ওপর কোনো মায়াবি টেক্সচার ফুটে ওঠার অবকাশ পায়! অভিজাত শিল্পমহলে, আর্টিস্টদের ক্ষমতাশালী লবির বৃত্তে অনিন্দিতার আনাগোনা, ধনী স্বামীর অর্থে দিল্লী-মুম্বইয়ে তার একক প্রদর্শনী!
সব হারিয়েও মা কিন্তু জীবনের ধন সংগ্রহের স্বভাব বর্জন করতে পারেননি। যতদিন শক্তি ছিল তিনি দিনে একবার হলেও বউদিদের চোখ এড়িয়ে সুমনের অন্ধকূপের মতো একচিলতে ঘরে এসে সারা ঘরে ছড়িয়ে থাকা সুমনের আঁকিবুকি কাটা টুকরো কাগজগুলোকে জড়ো করে নড়বড়ে টেবলের ওপর রাখা প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতেন। তার মধ্যে টুকরো স্কেচ আর মনের খেয়ালে অক্ষর-লিখনের অজস্র নমুনা ছিল।
ছোটোবেলা থেকে কাগজ হাতে পেলেই পেন, পেন্সিল হাতের কাছে যা পাওয়া যেতো তাই নিয়েই অক্ষর ডিজাইনের খেলা করা ছিল সুমনের স্বভাব। বিশেষভাবে স্কুলে স্যারেদের অসার সময়নিধনের কালে অঙ্ক খাতার পাতায়, দিদিদের দেওয়া বইয়ের মলাটে অবাধে চলত অক্ষরচর্চা! সব ছেলেই পেন বা ছুরি দিয়ে ক্লাশের বেঞ্চে নিজের নাম ফাঁকাতো, বেড়াতে গেলে গাছের গায়ে নিজের ও পাত্তা না-পাওয়া মেয়েটির নাম লিখত কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটির সঙ্গে যোগচিহ্ন দিয়ে কুরূপা কোনো কাল্পনিক মেয়ের নাম। সেটা ছিল সেকালের মধ্যবিত্তের ভীরু কুৎসা-কালচারের একটা সস্তা ছুঁচোমি। কিন্তু নিজের নাম সুমন খুব বেশিবার আর্ট করে লিখতে, কোনো সৌধের গায়ে কছু লিখে দেয়াল নোংরা করতে চিরকালই তাঁর রুচিতে বাধত।
(ক্রমশ)
…………………………………
(রচনার সঙ্গের ডিজাইনগুলি শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত বা পুনরঙ্কিত, আন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত ও সম্পাদিত এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গৃহীত। রচনার শেষে একটি বিস্তারিত সূত্র পরিচয়ে তা উল্লেখিত হবে)