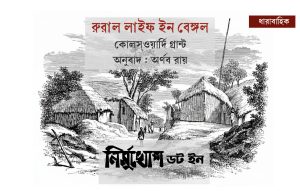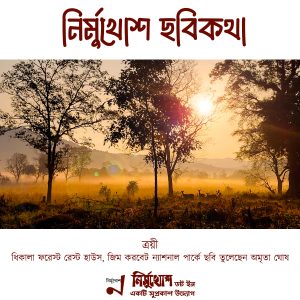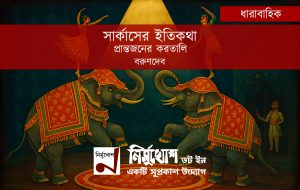অক্ষর-চরিত্র ও জ্ঞাপন-বাণিজ্য : এক অন্তহীন এপিটাফ। পর্ব ৩৪। অনন্ত জানা

খ. বাংলার শিল্প-ঐতিহ্যের অব্যক্ত কোলাহল ও ‘গ্রাফিতি’-র ইতিবৃত্ত
নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্পকলা নিয়ে সব জাতির মতোই বাঙালির একধরনের গর্ব আছে―সেই গর্ব আদৌ প্রচ্ছন্ন নয়, বরং আত্মাভিমানের উদবেজনে আক্রান্ত। বাঙালির উতল আবেগের সঙ্গে জড়িত আছে মধ্যযুগীয় চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের নবায়ন থেকে শুরু করে উনিশ শতকীয় বহুকথিত নবজাগরণের কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত বঙ্গীয় পূর্বাধিকার নিয়ে আত্মম্ভর কিংবদন্তী। শিল্পকলা তথা চিত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে বঙ্গের গৌরবগাথা বেশ উচ্চকিত। তার কারণ এই যে বিদ্যাশৃঙ্খলাকেন্দ্রিক শিল্পানুশীলনের প্রথম যুগে (১৮৫৪ সাল নাগাদ) বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত আর্ট স্কুল, পরে সরকারি গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট প্রতিষ্ঠার (১৮৬৪) মধ্য দিয়ে, আধুনিক শিল্পচর্চার বিকাশ হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতের একদা প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র ও তদুপরি সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত বঙ্গে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতীয় শিল্পচর্চার সূত্রপাত এবং পরিশেষে কলাভবনের প্রতিষ্ঠা (১৯১৯ নাগাদ)-র গৌরবের কথাও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ভারতশিল্পের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে বঙ্গের অবদান কিংবা উনিশ শতকীয় নব্য শিল্পতত্ত্বের আলোচনাতেও অবনীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম অর্জন করেছে। এমন একটা সময় শিল্পশাস্ত্রবিষয়ক এই সমস্ত ভাষ্য বিকিরিত হয়েছে, যখন ভারতীয় চিত্রকলার পূর্বতন তাত্ত্বিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনঃসংগ্রহ করার প্রচেষ্টাও বেশ কঠিন কাজ বলেই বিবেচিত হতো। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘শিল্পশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ সব যা ছিল বলেই শুনি, সেই সব প্রাচীন শাস্ত্রের সারসংগ্রহ বলে যে সব পুঁথি নানা কালে এ-দেবতা ও-ঋষি বা অমুক তমুকের কথিত বলে লেখা হল―রাজরাজড়ার পুস্তকাগারে ধরার জন্য সেইগুলোই কতক কতক এখন পাওয়া যাচ্ছে। তা থেকে দেখা যায় যে ধর্মের সেবায় শিল্পের যে সব দিক জড়িয়ে ছিল তারি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হল কিন্তু অন্যান্য কলা যা শৌখিন রাজরাজড়ার সেবায় লাগতো তাদের বিস্তারিত বিবরণ লেখাই গেল না।’ অবনীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন : ‘…বলতেই হয় আমাদের শিল্পশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র বলতে যা বোঝায় তা নয়, তাতে অঙ্গবিদ্যা হিসেবে আংশিকভাবে কোন কোন কলাবিদ্যার কথা বলা হয়েছে, ভারতশিল্পের প্রায় সাড়ে পনেরো আনা অংশের কথাই পাড়া হয়নি তাতে।’ (অবনীন্দ্রনাথ : ১৯২১-১৯১৯, গ্রন্থাকারে ১৯৪১)
ভারতশিল্প সম্পর্কে সেই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক কথাগুলিই এসেছে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সংক্রান্ত আলোচনায়। বাংলার শিল্পসংসারে এটা কম শ্লাঘার কথা নয়। কেননা, উনিশ শতকের আনুমানিক শেষ দশক থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতশিল্পের সিংহভাগ বা প্রায় সব আলোচনাই হয় বিদেশী তাত্ত্বিকদের দ্বারা অথবা দেশীয় আলোচকদের দ্বারা ইংরেজি ভাষায় করা। ভারতীয় শিল্পদর্শনের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার সিংহলজাত তামিল পণ্ডিত-তাত্ত্বিক-দার্শনিক আনন্দ কেন্টিশ মুথু কুমারস্বামী (১৮৭৭-১৯৪৭)-র ‘ইন্ট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান আর্ট’ (১৯২৩) গ্রন্থে উল্লিখিত ভারতীয় শিল্পালোচনার গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নামগুলি দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কুমারস্বামীর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ড্যান্স অব শিভা’ প্রকাশিত (১৯১৮) হয় নিউ ইয়র্ক থেকে। এসব কথা জানা থাকলে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-আলোচনাকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে অনুধাবন করাই যায়।
কিন্তু গোড়ার কথাটা এই যে অবনীন্দ্রনাথ নিজে মুখ্যত শিল্পী, আপাদমাথা শিল্পী। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব এই যে তিনি একাধারে রঙ-তুলির শিল্পী এবং কলম-কাগজে লিপির শিল্পীও। অধিকন্তু তিনি শিল্পালোচক ও শিল্পতাত্ত্বিকও। অবনীন্দ্রনাথের কথা বঙ্গের রাস্তার শিল্প, গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্রলিখন সম্বন্ধে বিশেষভাবে এসে পড়ে এই জন্যই যে, তিনি শিল্পকলার চর্চাকে সচেতন প্রচেষ্টা ও স্বেদাক্ত শ্রমের সৃষ্টি বলে মনে করেছিলেন : ‘প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন-ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে থাকা―বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে, চুপটি করে নয়―সজাগ হয়ে। এই সজাগ সাধনার গোড়ায় শ্রান্তিকে বরণ করতে হয়―আর্ট ইজ নট এ প্লেজার ট্রিপ, ইট ইজ এ ব্যাটেল, এ মিল দ্যাট গ্রাইণ্ডস।’
শিল্পের স্বভাব সম্পর্কে ফরাসি শিল্পী জাঁ ফ্রাঙ্কুইস মিলেট (১৮১৪-১৮৭৫)-এর এই উদ্ধৃতির মোক্ষম ব্যবহার বস্তুত শিল্প সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের প্রকৃত মনোভাব বুঝতেও সাহায্য করে। মিলেট কৃযক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে চিত্রিত করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। জমি আবাদ, ফসলের তদারক করা, ফসল তোলা, শ্রমবিরতিতে বিশ্রাম, কৃষকরমণীদের ঘরে-বাইরে শ্রমখিন্ন যাপন, পশুসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা’ ইত্যাদি মিলেটের ছবির পরিচিত বিষয়। মিলেট সম্ভবত বিশ্বাস করতেন যে, শিল্প সাধারণভাবে শ্রমনির্মিত জীবনের, জীবিকার, বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং শিল্পীর প্রকাশের যাবতীয় অভীপ্সাসমূহ সমাজ, সামাজিক অবস্থান, বেঁচে থাকার আবেগ ও প্রকৃতিসহ পরিবেশের সঙ্গে কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই আসে―অনায়াস অনুপ্রেরণা থেকে নয়। চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগ (১৮৫৩-১৮৯০) প্রাথমিক পর্যায়ে মিলেটের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর অগুস্ত রোদাঁ (১৮৮০-১৯১৭)-র মতোই অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর অনুপ্রেরণার দৈবী ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছেন। ইন্সপিরেশনের খেয়ালকে তিনি একেবারেই বাতিল করে দিয়েছেন। জীবনের সত্যমূল্য চুকিয়েই ‘শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়।’ সম্ভবত এই কারণেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-বক্তৃতায় প্রথমে এসেছিল ‘শিল্পে অনধিকার’-এর প্রসঙ্গ, তারপরে এসেছে ‘শিল্পে অধিকার’-এর কথা।
বঙ্গভঙ্গের কালে (১৯০৫) অবনীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন ‘বঙ্গমাতা’কে। এই বঙ্গমাতাই পরে ‘ভারতমাতা’ হিসেবে পরিচিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক ও অকাদেমিক ব্যবহারের পৌনপুনিকতার ফলে সুপরিচিত এই চিত্রকর্মে দেশমাতা সম্পদের দেবীর রূপকল্পে বেশভূষায় যোগিনী। জাফরান রঙের শাড়ি পরিহিতা, তাঁর চার হাতে যথাক্রমে ধানের শিস, রুদ্রাক্ষের জপমালা, একটি পঁুথি এবং এক টুকরো সাদা কাপড়, গলায়, হাতে বাজুতে রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার পেছনে জ্যোতির্বলয়, পুষ্পাকীর্ণ তাঁর অধিষ্ঠান। শান্তি, শক্তি ও সংগ্রামের প্রেরণাদাত্রী তিনি। বঙ্গমাতা ও ভারতমাতার এই রূপকল্পের পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) উপন্যাসে উপস্থাপিত দেশ ও দেবীবন্দনা এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননি! ভারতবর্ষ’ গানটি। (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২০)
বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস ও অবনীন্দ্রনাথের ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি ক্রমেই রাষ্ট্রনীতির কারবারিদের কাছে হিন্দু জাতীয়তাবাদের একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমকে ধর্মীয় ভক্তির সঙ্গে বিজড়িত করে দেখা, রাজনীতির কলা ও কৌশলে দেশমুক্তির পথটিকে ভক্তিরসে কাদা করে দেওয়া, ন্যাশনালিজমের অছিলায় পরজাতিবিদ্বেষ, দেশকে মা মা করে ন্যাশনালিজমের জিগির তোলা ইত্যাদিকে নিঃশেষে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ‘ভারতমাতা’ চিত্রটির সার্বিক পরিচিতি সত্ত্বেও গোষ্ঠীগত স্বার্থে ধর্মের সঙ্গে চিত্রকলার রসনিষ্পত্তিকে গুলিয়ে ফেলাটাকে অবনীন্দ্রনাথ আদৌ শিল্প বলেঅনুমোদন করেননি। তিনি ১৯২০-র দশকে যতটা স্পষ্ট করে সম্ভব ততটা স্পষ্ট করে ইউরোপীয় শিল্পের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন : ‘শিল্পকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে না দেখে শিল্পের দিক দিয়ে দেখা খুব অল্প দিন হল ইউরোপে চলিত হয়েছে। প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে এই ভাবে শিল্পরসের দিক দিয়ে কলা সমস্তকে দেখা আলঙ্কারিকগণ প্রচলিত করে গেছেন।’ কিন্তু কে শোনে! স্বয়ং স্রষ্টার কথা, শিল্পের সুললিত মানবিক ভাষ্য? রাজনীতির স্বার্থলাঞ্ছিত ন্যারেটিভ তৈরির কৌশলের কাছে শিল্প ও শিল্পী দুই-ই তুচ্ছ!
শিল্প রঙে-রেখায়-রূপনির্মাণে বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। শিল্প দুটি বিপরীতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টাকে অনুসরণ করে চলেছে, ―প্রকৃতির প্রতি সবচেয়ে দাসত্বপূর্ণ আনুগত্য এবং মানববিশ্বের জন্য সবচেয়ে পরম স্বাধীনতা, ―এতটাই পরম যে প্রতিটি শিল্পকর্ম নিজেকে এক-একটি নতুন সৃষ্টি বলে দাবি করতে পারে। এই পরম স্বাধীনতার জন্য শিল্পীকে যত সংগ্রাম করতে হয়, যত মনন, ধীশক্তি এবং দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়, স্বল্পায়োজনেই ফুটিয়ে তুলতে হয় মননবিশ্বকে, শ্রমেঘামে মানুষের বেঁচে থাকার, মনুষ্যত্বের জীববৃত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তির জীবন-উদযাপনের উপাদানগুলিকে গ্রহণ ও উপভোগ করার অধিকারকে সুরক্ষা দেবার কথা বলার জন্য যাবতীয় ভয়কে জয় করার আনন্দরেখাগুলিকে।
চারুশিল্পের এলাকাই যদি শিল্পীর পক্ষে একটি যুদ্ধক্ষেত্র হয়, হয় পেষাই-যন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামলিপ্ত শস্যকণার শ্রমলিপি―তাহলে রাস্তার শিল্প, দেয়ালচিত্রলিপিমালা, বিশেষভাবে গ্রাফিতি আর কিছু নয়―যে-সব ‘কবি ক্ষুধা-প্রেম আগুনের সেঁক’ চান’―‘হাঙরের ঢেউয়ে’ খান ‘লুটোপুটি’ (সমারূঢ় : জীবনানন্দ) সেই সব কবির তুলির লাভাস্রোতে ফুটে ওঠা উত্তপ্ত আগ্নেয় কবিতা!
একদা জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭৮), দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৯১) মন্বন্তর খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষ (১৩৫০-এর মন্বন্তর), কৃষক ও শ্রমিকের অতীতের ও বর্তমানের চলমান সংগ্রাম [যেমন : চুয়াড় বিদ্রোহ (১৯৬৬-১৮৩৪), সন্দ্বীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৪-১৮৩৩), ১৮২৭ সালের পালকি বেহারাদের ধর্মঘট, দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তুদের উচ্ছিন্ন জীবন (১৯৪৭ পরবর্তী সময়), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৮) ইত্যাদি] গণআন্দোলন, মানবিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় (মনপুরা ঝড় ১৯৭০ নামে জয়নুল আবেদিনের স্ক্রোলচিত্র), স্বাধীনতাপূর্বকালে উপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতা, স্বাধীনতা পরবর্তী বঞ্চনার ছবি এঁকে বঙ্গে জনগণের শিল্পী হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। চিত্রকলার লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে এইসব অঙ্কন পোস্টারে, ―কোনো কোনো ক্ষেত্রে পোস্টারের সীমারেখা অতিক্রম করে গ্রাফিতিক-পোস্টারে মুক্তি পেয়েছিল। গ্যালারিবন্দী বৈভবের চর্চা, এলিটের বাগ্্বিস্তারের আবহ ও নিছক বুদ্ধিচর্চার বলয়কে এঁদের ছবির বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা ভেঙে দিয়েছিল। শিল্পবিষয় ও শক্তিশালী রেখার সাহসী ব্যবহারে বঙ্গের শিল্পাঙ্গনকে (থিয়েটারসহ যাবতীয় নাট্যচর্চায়, বুদ্ধিদীপ্ত, চলচ্চিত্র নির্মাণে, গণসংহতির গানে এবং…শিল্পচর্চায়ও) দিয়েছিলেন বিরল স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচিতি এবং একধরনের গণশিল্পের সমাজপ্রেক্ষিত।
কলকাতার দেয়ালশিল্প এবং প্রকাশ্য রাস্তার চিত্রকলার প্রাথমিক যুগযাত্রার মূলে বামপন্থার উত্থান ও সক্রিয়তা ছিল তর্কাতীত। যাঁরা এই কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী শানু লাহিড়ী (১৯২৮-২০১৩) : ‘কলকাতার এসব চিত্রকলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শানু লাহিড়ীর নাম। চলে আসে চিত্তপ্রসাদের নামও। দুজনেই বামপন্থী ঘরানায় চেয়েছিলেন রাস্তায় ছবি আঁকতে। মানুষের মধ্যে চলে যেতে বারবার।…রামকিঙ্করের শান্তিনিকেতনের মুক্ত ভাস্কর্যর কথাও। খোলা আকাশের নিচে সেসব কাজকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।’ ( দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় : ২০২১)
শানু লাহিড়ী কলকাতায় তাঁর প্রথম গ্রাফিতিটি এঁকেছিলেন লা মার্টিনিয়ের স্কুল ফর গার্লসের দেয়ালে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিস্যুয়াল আর্ট বিভাগে যোগ দেওয়ার পর সেখানকার ছাত্রদের সহায়তায় এবং নিজ উদ্যোগে তিনি প্রচুর দেয়াল চিত্রিত করেন। তাঁর সেইসব অসামান্য দেয়াল-চিত্রকর্মের প্রায় সবই শুধুমাত্র ছবির অ্যালবামে টিকে রয়েছে। গ্রাফিতি শিল্পী সাধারণভাবে যতটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী হয়ে থাকেন শানু তার থেকে সম্ভবত বেশিই প্রতিষ্ঠান বিরোধী ছিলেন। (শমিক বাগ : ২০১০) লা মার্টিনেয়ার স্কুল ফর গার্লসের দেয়ালে কিশোরীদের নিষ্পাপ মন গড়ে তোলার জন্য ছবি আঁকবার পর তিনি শহরের দেয়ালে বহু আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক গ্রাফিতি রচনা করেছিলেন।
শানু লাহিড়ী ও চিত্তপ্রসাদের স্ট্রীট আর্ট প্রসঙ্গে শিল্পভাষ্যকার সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন প্রতিবেদক। সেখানে মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন : ‘চল্লিশের দশকের দৈনন্দিনতাকে যেভাবে সবল রেখায় চিত্তপ্রসাদ ধরেছিলেন, আজ পেলব শান্তিনিকেতন যখন ভেঙে পড়েছে তখন আমরা আবিষ্কার করছি চিত্তপ্রসাদ আমাদের মুক্তির আলোরেখা। বিজন চৌধুরীর নামও আমাদের বলতে হবে। বিজনবাবুর মৌলালি যুবকেন্দ্রের কাজগুলির কথাও বলতে হবে, যে অনবদ্য কাজগুলি পরে ভেঙে দেওয়া হয়।…কলকাতায় সত্তরের দেওয়াল লেখায় মুষ্টবদ্ধ হাত দেখে একদল দক্ষিণপন্থীরা তাকে সাংস্কৃতিক পাঠক্রমের বাইরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁরা বলতে শুরু করেছিলেন, শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে।’ (উল্লেখ : তদেব)
কলকাতার দেয়াললিপিমালার ক্ষেত্রে ১৯৭০-এর দশককে একটি মাইলফলক বলে মনে করা যেতে পারে। শুধু একদা এই দশককে মুক্তির দশক বলে শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল বলেই নয়, সমস্ত ধরনের অতিরেক সত্ত্বেও রাজনীতি-সমাজনীতি-সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই দশকের দৈনন্দিনতায় মানুষকে, অগ্নিসংস্কারের দুস্তর কান্তার মরু, যন্ত্রণার, ভয়ের, সাহসের, অনিশ্চয়তার ও ধৈর্যের পথ পেরোতে হয়েছিল বলেও।

এই সময়েই (১৯৭৫-১৯৭৬ সাল নাগাদ) কলকাতাসহ অন্যান্য স্থানে ‘চলমান (বা গতিশীল) শিল্প আন্দোলন’ দেখা দেয়। এই আন্দোলনে অগ্রণী শিল্পীরা ছাড়াও কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-সমাজকর্মীদের অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। চলমান শিল্প আন্দোলন সম্ভবত ১৯৪০-১৯৫০-এর দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পথে নেমে আসা, মাঠ-ঘাটের নাট্যপ্রদর্শন (অধিকাংশ আলোচনায় এই অভিষঙ্গটি অনুক্ত থেকে যায়) এবং সত্তরের দশকে নাট্যকার-পরিচালক বাদল সরকারের শতাব্দী নাট্যদলের মুক্তাঙ্গন নাট্যপ্রয়াস (অসিত পালের প্রতিবেদন অনুযায়ী : এই সময়েই নিয়ম মতো ভাড়া দিতে না পারায় বাদল সরকারের ‘শতাব্দী’ নাট্যদল একাডেমির মহড়া কক্ষ থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছিল। বাদল সরকার এই উচ্ছেদের প্রতিবাদ করেননি, সম্ভবত বাদল সরকারের দিক থেকে ‘এটি ছিল প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ।’ এবং সম্ভবত এর পরবর্তীকালেই কার্জন পার্কে শতাব্দী প্রায় নিয়মিত তার নাট্যাভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে। এখানে আরও কয়েকটি সংগঠন অনুষ্ঠান করত, তারাও শতাব্দী নাট্যদলের দ্বারা প্রাণিত হয়েছিল। ‘শিল্পকলায় স্বাধীনতার স্বাদ’ পেতে এবং আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে জনসাধারণের ভীতি ও অনীহা দূর করার লক্ষ্যে এই আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। আন্দোলনের লক্ষ্য সম্বন্ধে চলমান শিল্পকলা বা উন্মুক্ত গ্যালারি আন্দোলনের অঘোষিত নেতা শিল্পী অসিত পালের ইশতেহারপ্রতিম বয়ান : ‘আমি বাড়ির মালিকদের কাছে অনুরোধ করছি, তোমাদের ঘরগুলিকে চিত্রাঙ্কিত হতে দাও; আমি গাড়ির মালিকদের কাছে অনুরোধ করছি, তোমাদের গাড়ির উপরিভাগে রঙ করো যাতে তা আকর্ষণীয় হয়। ছবি সর্বত্র আঁকা যায় ―এমনকি আবর্জনার ভ্যানেও। বন্ধ দরজার আড়াল থেকে ছবিগুলো খোলা জায়গায় নিয়ে এসো; ছবিগুলো আমাদের মতো অক্সিজেন চায়। তারা আর গ্যালারির চার দেয়ালের মধ্যে আটকা থাকবে না। সাহিত্য বইয়ের ভেতরে বন্দী থাকবে না; এটি মানুষের মাঝে দেখা যাবে ; সর্বত্র ট্রাম এবং বাসে ছবি আঁকা হবে; ছবি তোমার সাথে চলবে, এটি গতিশীল শিল্প হবে; আমি সর্বত্র রঙিনদের এগিয়ে যেতে বলি, আসুন কলকাতাকে আলোকিত করি!’
চলমান শিল্প আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রথমে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের গেটের পাশের প্রশস্ত অংশের বহির্ভাগের দেয়ালে সারারাত ধরে বিরাট ছবির অলংকরণ করা হয়। এই কাজে অসিত পাল ও তাঁর সহযোগীরা কবি-সাহিত্যিকসহ বহু মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন। হাসপাতালের দেয়াল ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষের লিখিত সম্মতি থেকে শুরু করে কলকাতার সুপ্রাচীন দুই রঙের কারবারি অবিনাশ দত্ত কোম্পানি ও জি সি লাহার থেকে প্রচুর রঙ পর্যন্ত পেয়েছিলেন।
এক জানুযারির কুয়াশাভরা শীতের রাতে এই দেয়াল চিত্র, দেয়াল-পদ্য, দেয়াল-গল্প অঙ্কিত হলো। পথচলতি নগর মাতালেরা অঙ্কনরত শিল্পীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন রঙ এবং ‘শিল্প ক্যান্সার নিরাময় করতে পারে কিনা!’ সেই রাতেই রাস্তায় বিচরণরত একটি ভবঘুরে গরুর গায়েও তুলির আঁচড়ে রঙের প্রলেপ লাগানো হয়।
এই উদ্যোগ সংবাদমাধ্যমের ব্যাপক সমর্থন ও প্রচার লাভ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে শুরু করে টাইমস অব ইণ্ডিয়া পর্যন্ত এ-নিয়ে খরব ও ‘স্টোরি’ প্রকাশ করে। আনন্দবাজার পত্রিকায় একে ‘খোলা হাওয়ার শিল্প’ আখ্যা দেওয়া হয়। আন্দোলনের শরিক সুনীল গঙ্গোপাধায় সেই অঙ্কনকে প্রশংসা করেন, বিশেষভাবে ছবিতে থাকা ‘সাপ এবং পদ্ম সম্পর্ক।’ সংবাদমাধ্যমে নন্দিত হওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগটির অভিনবত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবস্থানগত সুবিধা। আন্দোলনের মুখ্য উদ্যোক্তা অসিত পাল নিজে ছিলেন আনন্দবাজারের কর্মী এবং সমর্থকদের অনেকেই ছিলেন সংবাদমাধ্যমের পদাধিকারী, লেখক-কবি-সাংবাদিক। ক্রমেই গ্যালারির বাইরে শিল্পকে প্রদর্শন ও প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন দ্রুত কলকাতাময় ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তার মাঝখানে মুক্ত-গ্যালারি স্থাপন করা হয়। শিল্পের উন্মুক্ত প্রদর্শনও শুরু হয়। সংগীতে, গল্পে, কবিতায়, গানে স্ট্রীট আর্ট আন্দোলন বেশ শক্তি ও সমর্থন অর্জন করে।
আন্দোলনকারীদের ঘোষিত অভীপ্সা ছিল, এই আন্দোলন এমন একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যা : ‘আগামী বছরগুলিতে বাস্তবে পরিণত হবে, এমন একটি পথ যা আরও পথ খুলে দেবে। মানুষের শরীরে, যানবাহনে, পোশাকে শিল্প থাকবে ; সর্বত্র, রাস্তায়, চলমান শিল্প থাকবে, পবিত্র সুতো ছাড়াই শিল্প। শিল্প মানুষের সাথে সাথে চলবে। শিল্প গতিশীল হবে। কলকাতা হবে একটি দুর্দান্ত ক্যানভাস।’
এই লক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে, পরে হাজরা মোড়ের বসুশ্রী কফি হাউজের ভেতরে, যানবাহনের গায়ে, নারী ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রে প্রচুর ছবি আঁকা হতে থাকে। চৌরঙ্গীর মনোহর দাস তরাগ বা জলাশয়ের কাছে ট্রাম লাইনের পাশে পরিত্যক্ত গম্বুজ (বিশ্রামাগার?)-এ সাধারণের জন্য মুক্ত গ্যালারি (গ্যালারি এ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেই গ্যালারি ঘিরে প্রতিদিন কবিতা পাঠে, সংগীতে, বাউল গানের সুরে, নৃত্যের ছন্দে, সাঁওতালি নৃত্যের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় থাকত জমজমাট আয়োজন। চলমান শিল্প আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে ‘চলমান ক খ গ’ ‘ডাইন এ বি সি’ নামে দ্বিভাষিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়। শিল্পী রামকিঙ্কর বেজ, পরিতোষ সেন, শানু লাহিড়ী, পূর্ণেন্দু পত্রী, রথীন মৈত্র, সুনীলমাধব সেন, সমীর ঘোষ, প্রকাশ কর্মকার, সমীর গুহ, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, কবি সমরেন্দ্র দাস, গল্পকার কল্লোল মজুমদার, কবি ধূর্জটি চন্দ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়, কবি ও সংগীত শিল্পী সুতনুকা বাগচী, তপন ভট্টাচার্য, মৈনাকশঙ্কর রায়, তপশ্রী গোস্বামী, পর্বতারোহী রমা দাশগুপ্ত, সংগীত শিল্পী অজিত পাণ্ডে, রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক শঙ্কর, কবি শুক্লা ঘোয, যোগব্রত চক্রবর্তী, নৃত্যশিল্পী তনুশ্রীশঙ্কর, আনন্দশঙ্কর, দীপঙ্কর সাহা, তপন ঘোষ, কবিতা সিংহ, শরৎ মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর বল, সংগীতশিল্পী স্বপন সোম, বাংলা কবিতার সুরকার ঋষিন মিত্র, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, সুতপন চট্টোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর বল, দেবাশিস দাস, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সমর মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ দাশ, দিব্যেন্দু পালিত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, কৃষ্ণ ধর, নিখিল সরকার, উৎপল বসু, অমিতাভ চৌধুরী, প্রফুল্ল রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, প্রণব মুখোপাধ্যায়, অহিভূষণ মালিক, সুব্রত সেনগুপ্ত, নাসের হোসেন, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শেখর বসু, শুদ্ধশীল বসু প্রমুখ। অসিত পাল তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে, প্রায় চারশো পঞ্চাশ জন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক বিভিন্ন সময়ে এই উন্মুক্ত গ্যালারি পরিদর্শন করেছিলেন, এঁদের মধ্যে ছিলেন একরাম আলী, মৃদুল দাশগুপ্ত, জয় গোস্বামী, দাউদ হায়দার, সৌনক লাহিড়ী, রণজিৎ দাশ প্রমুখও। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরে গ্যালারি এ বন্ধ করে দেওয়া এবং দেয়াল থেকে অসিত পাল অঙ্কিত ছবিগুলি মুছে ফেলার সরকারি নির্দেশনার বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

এই সময়েই দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। সেসময় খুব খোলাখুলিভাবে বা আরামের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করা সম্ভব ছিল না। সরাসরি কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসরণ, রূপারোপ বা পরিচয় না থাকলেও এই আন্দোলনও প্রশাসনিক সন্দেহের ঊর্ধে ছিল না। এই সময়েই শহরের দেয়াল থেকে চলমান মুক্ততার শিল্পকলাকে মুছে ফেলার কাজ শুরু হয়, মেট্রোরেলের গ্রাসে বন্ধ হয়ে যায় গ্যালারি এ। ফলে চলমান শিল্প আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। তবু ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন টিকে ছিল, তার পরেও এই আন্দোলনের বার্ষিকী পালনের সংবাদ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে উত্তপ্ত সেই দিনগুলিতে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যভাগের পশ্চিমবঙ্গের সেই দিনগুলিতে এই শিল্প আন্দোলন বিশেষভাবে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ লালিত না-হওয়া সত্ত্বেও এর ফলে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিতার বলয়ে মুক্তিতার স্বাদ এনেছিল।
চলমান শিল্প আন্দোলন বা ডায়নামিক আর্ট মুভমেন্ট সম্পর্কে বলার কথা এটাই যে, দেয়াল-ছবির ও উন্মুক্ত শিল্প-প্রদর্শনের (ছবি, গান, নৃত্য, আবৃত্তি―সবই ছিল এর অন্তর্গত) এই কার্যক্রম, বিশেষভাবে অঙ্কিত ছবিগুলি স্ট্রীট আর্ট হলেও প্রকৃত অর্থে গ্রাফিতি হয়ে উঠতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। গ্রাফিতি নিছক দেয়াল লিখন বা দেয়াল-ছবির অলংকরণ নয়। সে ছিল এমন এক সময়, যখন প্রতিটি রাতই ছিল দুঃস্বপ্নের রাত, প্রতিটি প্রভাতই ছিল অনিশ্চয়তার, নিরাপত্তাহীনতার, সর্বপ্রকার বিরুদ্ধপক্ষের রাজনীতি ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের পশ্চিমবঙ্গের অস্থির পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে চলমান শিল্প আন্দোলন প্রথম থেকেই রাজনীতিমুক্ত এক ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিল। এই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক অসিত পাল জানাচ্ছেন যে, অসিত পাল চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের দেয়ালে ছবি আঁকার পর এই আন্দোলনের অন্যতম অভিভাবক স্থানীয় কবি ও শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী পালকে বলেছিলেন : ‘তোমরা ঐতিহাসিক কিছু করেছ! মানুষ এখন েদয়াল রাজনৈতিক গ্রাফিতির কথা ভুলে যাবে। এবং পরিবর্তে ছবি, কবিতা এবং গল্পের দিকে তাকাবে।’ এই আন্দোলন যে বঙ্গের এবং সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে ‘মিডিয়া হাইপ’ লাভ করেছিল, তার একটা কারণ―এই আন্দোলনের অরাজনৈতিক (!) চরিত্র-লক্ষণ। যদিও পাল তাঁর প্রতিবেদনের একটি অংশের উপ-শিরোনাম দিয়েছেন : ‘বিপ্লবের অনুভূতি মানুষের মনে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল।’ কিন্তু ‘বিপ্লব’ শব্দটি এক্ষেত্রে সম্ভবত শিল্প আন্দোলনের অভিনবত্ব, গতিশীলতা, পরিবর্তনের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। গ্যালারি এ-তে এসে সংগীত শিল্পী অজিত পাণ্ডে গেয়েছিলেন তাঁর চাসনালা খনি-দুর্ঘটনা (১৯৭৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তদানীন্তন বিহারের ধানবাদের কাছে চাসনালা খনিতে বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনায় বন্যা দেখা দেওয়ায় প্রায় চারশো খনি শ্রমিকের মৃত্যু হয়) নিয়ে নিজের লেখা ও সুরে গ্রথিত অসামান্য গান― ‘রাতকে বিত্যায়লাম হো / দিনকে বিত্যায়লাম হো / তেবেও আমার মনের মানুষ আইলো না / এই চাসনালা খনিতে মরদ আমার ডুব্যা গেল গো / এই পাঞ্চেতের পাহাড়ে / মেঘ জম্যাছে আহা রে / এমন দিনে হায় হায় / মরদ আমার ঘরে নাই / গ্যাঁন্দা ফুলেও রঙ নাই / এই চাসনালা খনিতে মরদ আমার হারাইং গেল গো…গেয়েছিলেন। তাঁর উচ্চ উদাত্ত কন্ঠ ট্রামের যান্ত্রিক শব্দকে ডুবিয়ে দেয়। এটাই ছিল চলমান শিল্প আন্দোলনের প্রাণশক্তির একটা সাধারণ দিক।
সাময়িক পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও ১৯৭০-এর দশকের পরেও কলকাতার দেয়ালগুলি পুরোপুরি নীরব হয়ে যায়নি।
কলকাতার রাস্তার শিল্প তথা গ্রাফিতি-সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলিতে (মধুপর্ণা দে, ব্র্যাড ফরস্টার, ভাইস ম্যাগাজিন, রিথিংকিং দি ফিউচার, দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যতপা আদক, ছন্দক গুহ. অনির্বাণ সাহা, প্রীতম দত্ত, শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী অধিকারী, ইন্ডিয়ান আর্ট কটেজ, সায়ন্তিকা মিত্র, আলিসা আলিম আনসারি, কলকাতা স্ট্রীট আর্ট ফাউন্ডেশন, খুশি মুল্লা, অর্ক আকুলি, প্রণয় চট্টোপাধ্যায়, দেবরূপ চৌধুরী প্রমুখের) কলকাতা গ্রাফিতির সংখ্যাগত সমৃদ্ধির একটা চেহারা বোঝা যায়।
প্রায়শই ১৯৮০-র ও ১৯৯০-এর দশককে কলকাতা তথা বাংলার রাস্তার শিল্পের অন্যতম সমৃদ্ধির কাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।
(ক্রমশ)
(রচনার সঙ্গের ডিজাইনগুলি শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত বা পুনরঙ্কিত, আন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত ও সম্পাদিত এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গৃহীত। রচনার শেষে একটি বিস্তারিত সূত্র পরিচয়ে তা উল্লেখিত হবে)